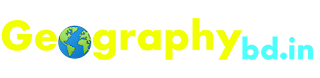একাদশ শ্রেণী বাংলা দ্বিতীয় সেমিস্টার, প্রথম অধ্যায় ছুটি - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রশ্ন উত্তর | Class 11, 1st semester Bengali, First Chapter । WBCHSE । Chuti - Robindranath Tagore
শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা আলোচনা করবো একাদশ শ্রেণীর বাংলা বিষয়ের প্রথম অধ্যায় ছুটি - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিয়ে। আশাকরি তোমরা একাদশ শ্রেণীর দ্বিতীয় সেমিস্টারের এই ছুটি - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যায়টি থেকে যেসব প্রশ্ন দেওয়া আছে তা কমন পেয়ে যাবে। আমরা এখানে একাদশ শ্রেণীর, দ্বিতীয় সেমিস্টারের বাংলা বিষয়ের প্রথম অধ্যায় ছুটি - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর SAQ, শূন্যস্থান পূরণ, এক কথায় উত্তর দাও, Descriptive, ব্যাখ্যা মুলক প্রশ্নোত্তর , সংক্ষিপ্ত নোট এগুলি দিয়েছি। এর পরেও তোমাদের এই ছুটি - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যায়টি থেকে কোন অসুবিধা থাকলে, তোমরা আমাদের টেলিগ্রাম, হোয়াটসাপ , ও ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারো ।
ছুটি - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর - নিচের প্রশ্ন গুলির উত্তর দাও (প্রতিটি প্রশ্নের মান ৫)
প্রশ্ন ১
"খেলা ভাঙিয়া গেল”- কোন্ খেলা, কেন ভেঙে গেল? ৫
উত্তরঃ-
খেলাটির বর্ণনা:
প্রশ্নে উদ্ধৃত অংশটি নেওয়া হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছুটি' গল্প থেকে। আলোচ্য গল্পে নদীতীরে পড়ে থাকা প্রকান্ড শাল কাঠের গুঁড়িটিকে সকলে মিলে ঠেলে গড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার যে খেলাটি পরিকল্পনা করা হয়েছিল, সেই খেলাটি ভেঙে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে।
খেলা ভাঙার কারণ:
'ছুটি' গল্পের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, নদীতীরে পড়ে থাকা একটি শাল কাঠের বিশালাকৃতির গুঁড়িকে সকলে মিলে ঠেলে গড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করে গল্পের নায়ক ফটিক
চক্রবর্তী। কিশোর ফটিকই বালকদের দলের অধিনায়ক তথা সর্দার। সুতরাং তার পরিকল্পিত খেলায় অংশগ্রহণ করতে উপস্থিত সকলে সানন্দে সম্মত হয়। বাধ সাধে ফটিকের ছোটোভাই মাখন। সে গম্ভীরভাবে সেই গুঁড়িটির উপর গিয়ে চড়ে বসে। ফলে অন্যান্য বালকেরাও হতোদ্যম হয়ে পড়ে। মাখনকে গুঁড়ির উপর থেকে নামাতে দু-একজন চেষ্টা করে। ফটিক এসে বলে 'দেখ, মার খাবি। এইবেলা ওঠ।' কিন্তু মাখন কোনোভাবেই সেখান থেকে নামতে সম্মত হয় না। সর্বোপরি, সে কারও কথাতেই কর্ণপাত করে না। ফটিক প্রথমে ভীষণ রেগে গিয়ে ভাইকে শাস্তি দেওয়ার কথা ভাবে। কিন্তু তাতে বাড়ি ফিরে অশান্তি হতে পারে ভেবে নিজেকে সংযত করে নেয়। পরক্ষণেই নতুন একটি পরিকল্পনার কথা তার মাথায় আসে।
ফটিকের পরিকল্পনা অনুযায়ী, মাখনের বসে থাকা অবস্থাতেই গুঁড়িটিকে সকলে মিলে ঠেলতে শুরু করে। স্বাভাবিকভাবেই মাখন মাটিতে পড়ে যায়। মাখনের এই পরিণতিতে অন্য ছেলেরা আনন্দ পেলেও ফটিক শশব্যস্ত হয়ে ছুটে আসে ভাইয়ের কাছে। ঘটনার আকস্মিকতায় খানিক হতভম্ব হলেও পরক্ষণেই মাখন ফটিকের উপর আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। ফটিককে সে অন্ধভাবে মারতে থাকে এবং তার নাকে-মুখে আঁচড়ে দিয়ে মাখন বাড়ি চলে যায়। আনন্দের আয়োজন করতে গিয়ে হঠাৎই এমন বেদনাদায়ক পরিস্থিতি তৈরি হলে খেলাটি বন্ধ হয়ে যায়।
প্রশ্ন ২
"ফটিক নিষ্ফল আক্রোশে হাত পা ছুঁড়িতে লাগিল।"- ফটিকের এরূপ অবস্থার কারণ কী, ব্যাখ্যা করো।
উত্তরঃ-
নিষ্ফল আক্রোশে হাত-পা ছোড়ার কারণ:-
প্রশ্নোদৃত অংশটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'ছুটি' শীর্ষক রচনার অন্তর্গত। ফটিক গ্রাম্য তথা প্রকৃতিপ্রেমিক কিশোর চরিত্র। পড়াশোনা তার অত্যন্ত অপ্রিয়। সারাদিন খেলাধুলা করেই দিন কাটাতে চায় সে। একদিন নদীর ধারে প্রকাণ্ড একটা গাছের গুঁড়িকে গড়িয়ে গড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টায় রত হলে, সেখানে তার ছোটো ভাই মাখন প্রবেশ করে এবং গাছের গুঁড়িটিতে একাধিপত্য স্থাপনের প্রচেষ্টা করলে, ফটিক ও তার বন্ধুরা তাকে সুদ্ধই সজোরে গুঁড়িটিকে ঠেলতে শুরু করে এবং স্বাভাবিক নিয়মেই মাখন পড়ে যায়।
মাখনের পড়ে যাওয়ার ঘটনায় ফটিক অপেক্ষা তার অন্যান্য সঙ্গীরা অনেক বেশি আনন্দিত হয়। ফটিক কিন্তু তৎক্ষণাৎ মাখনকে সাহায্য করতেই এগিয়ে যায় কিন্তু গৌরব অর্জনের ব্যর্থ চেষ্টায় লজ্জা পেয়ে মাখন ফটিককে মারধোর শুরু করে। এই অব্যবস্থা সৃষ্টি হওয়ায় যথারীতি খেলা ভেঙে যায়। ব্যথা ও লজ্জায় মাখন বাড়ির পথে পা বাড়ায় এবং মাকে গিয়ে ফটিকের নামে নালিশ জানায়। ফটিকের কৃতকর্মে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি বাঘা বাগদিকে বলেন, ফটিককে যে-কোনো প্রকারে বাড়িতে নিয়ে আসার জন্য। এতেই বিপত্তি বাড়ে। ফটিক বাড়ি যেতে অস্বীকার করলে, বাঘা বাগদি তাকে বলপূর্বক আড়কোলা করে তুলে নিয়ে যেতে চাইলে ফটিক নিষ্ফল আক্রোশে হাত-পা ছুড়তে থাকে এবং বলাই বাহুল্য যে, তাতে কোনো লাভ হয় না।
প্রশ্ন ৩
'ছুটি' গল্পে প্রকৃতির প্রভাব আলোচনা করো। অথবা, 'ছুটি' গল্পের মর্মান্তিক পরিণতির পিছনে প্রকৃতির প্রভাব কতখানি, তা আলোচনা করো। ৫
উত্তর:-
ভূমিকা:
রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'-তে লিখেছেন-"আমার শিশুকালেই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমার খুব একটা সহজ ও নিবিড় যোগ ছিল।" হ্যাঁ, শিশুকাল থেকেই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে ছিল তাঁর নিবিড় সংযোগ। প্রকৃতিকে তিনি যেমন ভালোবেসেছিলেন, প্রকৃতিও তাঁকে আপন করে নিয়েছিল শিশুকালেই। রবীন্দ্রমানসের কল্পনারসে জারিত হয়ে বিশ্বপ্রকৃতি স্থান করে নিয়েছে সর্বত্র-'ছুটি' গল্পটিও যার ব্যতিক্রম নয়।
প্রকৃতির প্রভাব:
নাগরিক জীবনের গন্ডি পেরিয়ে রবীন্দ্রনাথকে জমিদারি দেখাশোনার কাজে পৌঁছে যেতে হয়েছিল পদ্মাতীরবর্তী পল্লিবাংলার বিস্তীর্ণ সমভূমি শিলাইদহে। প্রকৃতির অসীম রহস্যময় সৌন্দর্য এবং প্রকৃতিলগ্ন মানুষের সহজসরল জীবনযাপন তাঁকে আপ্লুত করেছিল। এই শিলাইদহ পর্বে লেখা 'ছুটি' গল্পটিতে তাই প্রকৃতির প্রত্যক্ষ উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এ গল্পের নায়ক কিশোর ফটিক বড়ো হয়ে উঠেছে পল্লিবাংলার উদার-উন্মুক্ত পরিবেশে। খোলা আকাশ, নীচে দিগন্তজোড়া মাঠ, সীমাহীন নদীতীর আর একদল দামাল ছেলের নামহীন সাম্রাজ্যের রাজা সে। মায়ের ভর্ৎসনায় অভিমানী হয়ে, বয়ঃসন্ধির সময়ে নিজেকে বোঝা-না-বোঝার দ্বন্দ্বজটিলতায় মামার প্রস্তাবে রাজি হয়ে অসীম কৌতূহল নিয়ে সে পাড়ি দেয় কলকাতায়। সেখানে চারদেয়ালের মধ্যে বন্দি হয়ে গিয়ে মামির স্নেহশূন্য সংসারে সে হারিয়ে ফ্যালে জীবনের সহজ চাপল্য। এই বন্দিদশার আগল ভেঙে মুক্তমনের অবাধ বিচরণক্ষেত্রে ফিরে যেতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় তার অন্তর আদিগন্ত প্রকৃতির কাছে ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে।
উপসংহার:
আলোচ্য গল্পে আমরা দেখি খাঁচায় বন্দি বনের পাখির মতো অসহ্য যন্ত্রণা ফটিককে মুক্তির জন্য ব্যাকুল করে তুলেছে। সে বাড়ি ফিরতে চেয়েছে, ফিরে যেতে চেয়েছে প্রকৃতিলগ্ন জীবনের কাছে। ঘুড়ি ওড়ানোর বিস্তৃত মাঠ, সাঁতার কাটার সংকীর্ণ স্রোতস্বিনী, অকর্মণ্যভাবে ঘুরে বেড়ানোর সীমাহীন নদীতীরটির প্রতি সে আশ্চর্য আকর্ষণ অনুভব করেছে। অবাধ-অগাধ স্বাধীনজীবনে ফেরার জন্য তার ব্যাকুলতা প্রকাশিত হয়েছে। মায়ের স্নেহাঞ্চল এবং প্রকৃতির শ্যামলাঞ্চল-বঞ্চিত কিশোর ফটিক মায়া- মমতা-স্নেহ-ভালোবাসাহীন শহুরে পরিবেশ থেকে শেষে ছুটি নিয়েছে। মৃত্যুপথযাত্রী ফটিক মাকে বলেছে-"মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।" ফটিকের এই ব্যঞ্জনাবাহী উক্তিতে রবীন্দ্রনাথ পরিষ্কার করেছেন, প্রকৃতির সঙ্গে যে সত্তা অভিন্ন, প্রকৃতির থেকে বিচ্ছেদে তার মৃত্যু অনিবার্য-সে মৃত্যু কায়িক অথবা মানসিক। 'ছুটি' গল্পের এই মর্মান্তিক পরিণতির পিছনে তাই প্রকৃতির প্রভাবকে অস্বীকার করার উপায় থাকে না।
প্রশ্ন ৪
রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' গল্পের ফটিক চরিত্রটি বিশ্লেষণ করো। ৫
উত্তর:-
ভূমিকা:-
রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র হল- ফটিক। গল্পকার রবীন্দ্রনাথ ছোটোগল্পের ক্ষুদ্র পরিসরে, প্রকৃতির রং তুলি দিয়ে এক কিশোরের মানসিক যন্ত্রণাকে প্রতিবিম্বিত করেছেন। প্রকৃতির সন্তান: প্রকৃতির কোলে লালিত সন্তান ফটিক কলকাতায় মামা ও
মামির আশ্রয়ে এসে প্রথম উপলব্ধি করে, নাগরিক জীবনে সে কতটা অবাঞ্ছিত। ফটিকের গ্রামে ফিরে যাওয়ার ব্যাকুলতা শুধু মায়ের জন্য নয়, তার অন্তরাত্মার সঙ্গে প্রকৃতির এক নিবিড় একাত্মতার কারণে। শিশুর শিক্ষালাভে যান্ত্রিক পরিবেশ যে প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ, সেই মনোভাবই আশ্চর্য সহানুভূতির সঙ্গে গল্পকার এখানে উন্মোচিত করেছেন।
দলের নেতা:
'ছুটি' গল্পের নায়ক ফটিক তার দলবল নিয়ে উন্মুক্ত প্রকৃতির ছিল স্বচ্ছন্দবিহারী এক কিশোর। ঘুড়ি ওড়ানো, নদীতে সাঁতার কাটা, 'তাইরে নাইরে নাইরে না' বলে ঘুরে বেড়ানোর মধ্য দিয়ে তার মন আনন্দরসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠত।
সত্যের পূজারি:
সত্যের পূজারি ফটিক তার ভাই মাখনলালের গালে চড় মেরে ভাইয়ের মিথ্যাচারিতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। কিন্তু অপরদিকে ভ্রাতৃস্নেহে আর্দ্র ফটিক কলকাতা যাত্রার পূর্বে খেলার ঘুড়ি, লাটাই, ছিপ ভাইকে সমর্পণ করে তা সম্পূর্ণ ভোগের অধিকার দিয়ে যায়।
অভিমানী:
ফটিক ভীষণ অভিমানী। খেলতে খেলতে পড়ে গিয়ে মাখন যখন তাকে মেরে বাড়ি চলে গিয়েছে, তখন অভিমানে সে আনমনে বসে থেকেছে। মাখনের মিথ্যে অভিযোগে মা যখন তাকে প্রহার করেছে, সেই } মুহূর্তে মৃদু প্রতিবাদ করলেও মায়ের উপর তার অভিমান হয়েছে। আপাত মাতৃস্নেহবিহীন গৃহ পরিবেশে উপেক্ষিত ফটিক তাই মামার প্রস্তাবে সহজেই কলকাতা যেতে রাজি হয়ে গিয়েছে। আবার কলকাতা গিয়ে মামির হৃদয়হীন আচরণে অভিমান করে সে বাড়ি ছেড়েছে। এই অভিমান থেকেই ক্রমে প্রাণোচ্ছল ফটিক নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে এবং শেষপর্যন্ত মর্মান্তিক পরিণতির শিকার হয়েছে।
স্নেহকাতর:
ফটিক স্নেহের কাঙাল। গল্পে দেখা যায়, পিতৃহীন ফটিক তার মায়ের স্নেহ-মমতা-ভালোবাসা থেকে অনেকটাই বঞ্চিত। সে বোঝে তার মায়ের হৃদয়ের অধিকাংশটাই জুড়ে রয়েছে ভাই মাখন। তাই মামা বিশ্বভরবাবুর সদেহ প্রস্তাবে রাজি হয়ে সে কলকাতা চলে যায়। কিন্তু সেখানে গিয়ে মামির স্নেহহীন সান্নিধ্য তাকে পীড়িত করে। তাই স্নেহবুভুক্ষু ফটিক শেষপর্যন্ত মামারবাড়ি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেয়।
বয়ঃসন্ধিকালীন সমস্যায় জর্জরিত। বয়ঃসন্ধিকালীন অবস্থায় নানা ব্যর্থতা কিশোর-কিশোরীদের অন্তরকে পীড়িত করে। 'ছুটি' গল্পে ফটিকের প্রতি মামির বৃঢ় আচরণ, শিক্ষকের প্রহার, বই হারিয়ে ফেলা, বন্ধুত্বহীন নিঃসঙ্গ জীবন ইত্যাদি ঘটনার ফলে মানসিক দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত ফটিকের অন্তরায়া। বয়ঃসন্ধিতে দাঁড়িয়ে নিজেকে বুঝতে না পারার অক্ষমতাই তাকে অবসাদগ্রস্ত করে তুলেছে।
উপসংহার:
আসলে রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য গল্পে ফটিকের জীবনে আলো ফেলে কিশোর মনের সমস্যার সংকটটিকে যেমন আলোকিত করতে চেয়েছেন, তেমনই দেখিয়েছেন প্রকৃতির সঙ্গে যার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক: প্রকৃতির সঙ্গে বিচ্ছেদে তার বৌখিক মৃত্যু অনিবার্য। তবে, অনুভূতিশীল ফটিক মুমূর্ষু অবস্থাতেও উপলব্ধি করেছে তার ছুটি হয়েছে। রবীন্দ্রসাহিত্যে 'ছুটি'-র ফটিক তাই একটি অনন্য চরিত্র হয়ে আজও জীবন্ত হয়ে আছে।
প্রশ্ন ৫
রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' গল্পের মামির চরিত্রটি আলোচনা করো। ৫
উত্তর:-
ভূমিকা:
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছুটি' গল্পে বিশ্বস্তরবাবুর স্ত্রী অর্থাৎ ফটিকের মামি চরিত্রটি কাহিনির করুণ পরিণতির জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। গল্পে তাঁর উপস্থিতি খুব বেশি নয়। ফটিক যখন তার অবাধ-অগাধ স্বাধীনতা ছেড়ে মামার সঙ্গে কলকাতা এসেছে, তখনই পাঠক প্রথম পরিচিত হয়েছে এই হৃদয়হীন মামির সঙ্গে। ফটিকের বয়ঃসন্ধিকালীন মর্মব্যথাকে আরও দুঃসহ করে তোলার ক্ষেত্রে এই মামির ভূমিকা অপরিসীম।
বিরূপ মনোভাবাপন্ন:
প্রথমেই দেখা গিয়েছে স্বামীর সিদ্ধান্তকে তিনি ভালো মনে গ্রহণ করেননি। বিশ্বম্ভরবাবু ফটিককে নিজদায়িত্বে কলকাতায় নিয়ে
এলে ফটিকের মামি তাতে অসন্তুষ্ট হয়েছেন। ফটিকের সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, ফটিকের আগমনে তিনি খুশি নন। ফটিককে সাদর সম্ভাষণ জানানো তো দূরের কথা, সামান্য প্রীতি বা সৌহার্দ্য বিনিময় করতেও দেখা যায়নি তাঁকে।
হৃদয়হীন-নিষ্ঠুর আচরণ:
গল্পে জানা যায়, তাঁর মামি তিন সন্তানকে নিয়ে নিজের নিয়মে সংসার পরিচালনা করেন। তাই একটি তেরো-চোদ্দো বছর বয়সি অপরিণত, অশিক্ষিত গ্রামের ছেলেকে তাঁর গ্রহণ করতে অসুবিধা হয়েছে। বিশ্বস্তরবাবুর সিদ্ধান্তকে বাধ্য হয়ে মেনে নিলেও কখনোই ফটিকের সঙ্গে তিনি স্নেহপূর্ণ আচরণ করেননি। বরং তাঁর হৃদয়হীন সান্নিধ্যই ফটিককে ঠেলে দিয়েছে গভীর অবসাদে। মামির কাছে নিজেকে দুগ্রহ মনে হয়েছে ফটিকের। শরীর খারাপ হলে মামির সংসারে নিজেকে উপদ্রব বলে মনে করেছে সে। তাই বাড়ি ছেড়েছে ফটিক। ফটিকের বাড়ি ছাড়ার পিছনে মামির এই হৃদয়হীনতা অনেকখানি দায়ী।
মমতাহীন মাতৃত্ব:
মামির তিনটি সন্তান থাকলেও ফটিকের প্রতি তাঁর মমত্ব বা মাতৃত্ববোধের লেশমাত্র প্রকট হতে দেখা যায়নি। ফটিক মামির কাছে মাতৃস্নেহে প্রতিপালিত হতে পারত কিন্তু মামির কাছে তার প্রাপ্তি ছিল চরম অপমান।
প্রকৃতির সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠা এই অসংস্কৃত বালক ফটিকের স্নেহপ্রত্যাশী মনকে মামি অবদমিত করেছেন, তার উৎসাহকেও প্রতিমুহূর্তে দমিয়ে রেখেছেন তিনি। এমনকি, ফটিক অসুস্থ হয়ে পড়লেও মামির মধ্যে কোনও তৎপরতা লক্ষ করা যায় না। গল্পে ফটিকের মর্মান্তিক পরিণতিতে মামির বড়ো ভূমিকার কথা অনুভূতিশীল পাঠকমাত্রই অনুভব করতে পারেন।
বয়ঃসন্ধিকালীন সমস্যায় অনুঘটক:
ফটিকের বয়ঃসন্ধিকালীন সমস্যায় অনুঘটকের কাজ করেছেন মামি। ফটিক তাঁর ননদের ছেলে, সন্তানতুল্য। কিন্তু মামির কাছ থেকে পাওয়া অপমান, উপেক্ষা ও স্নেহবঞ্চনা ফটিকের অন্তরকে পীড়িত করেছে। ফটিকের অসুস্থতায় মামির প্রতিক্রিয়া- "পরের ছেলেকে নিয়ে কেন এ কর্মভোগ।” এই ঘটনাগুলি ফটিকের মনের মধ্যে অপরাধবোধের মাত্রাকে তীব্রতর করেছে। এর পরেই এই মুক্তিপিপাসু বালক বিশ্বপ্রকৃতির অনন্ত রহস্যের মধ্যে বিলীন হয়ে গিয়েছে।
উপসংহার:
রবীন্দ্রনাথ এমনই এক স্বার্থান্বেষী মামির চরিত্রকে গড়ে তুলেছেন যা ফটিককে তার মর্মান্তিক পরিণতির দিকে এগিয়ে দিয়েছে।
প্রশ্ন ৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছুটি' গল্পটির নামকরণের সার্থকতা বিচার করো। ৫
অথবা,
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছুটি' গল্পটি 'নামকরণ' অংশ অনুসরণে লেখো।
অথবা,
'ছুটি' গল্পটির ভাববস্তু ব্যাখ্যা করো।
অথবা,
'বিষয়বস্তু' অংশ অনুসরণে লেখো।
অথবা,
ছোটোগল্প হিসেবে 'ছুটি' গল্পটি কতটা সার্থক হয়ে উঠেছে, তা আলোচনা করো। ৫
উত্তরঃ-
ভূমিকা:
বাংলা ছোটোগল্পের সার্থক স্রষ্টা হলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনিই প্রথম 'ছোটোগল্প' শব্দটি ব্যবহার করেন। ছোটোগল্প কেবল ভাবাশ্রয়ী- কল্পনামুখ্য নয়, বরং জীবননির্ভর এবং এতে রয়েছে খণ্ড কাহিনির ব্যবহার।
ছোটোগল্পকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'বর্ষা যাপন' কবিতায় বলেছিলেন, "নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা, নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে শেষ হয়ে হইল না শেষ।”
ব্যাখ্যা:-
'ছুটি' গল্পটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে প্রাকৃতিক বর্ণনা ব্যতীত কোনো ঘটনা বর্ণনার আতিশয্য এতে নেই। প্লট-এর বাহুল্য নেই, গ্রাম ও শহরের মধ্যেই গল্পটি ঘোরাফেরা করে। ফটিকের বেড়ে ওঠার গ্রাম্য প্রকৃতি থেকে উৎখাত হয়ে নাগরিক যান্ত্রিকতার মধ্যে এসে পড়ার চরম পরিবর্তন ছাড়া আর তেমন কোনো পরিবর্তন এই গল্পে নেই, শেষেও ফটিকের কী হল তার সুস্পষ্ট ধারণা আমরা পাই না-অতৃপ্তি নিয়েই গল্পটি শেষ হয়। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে ছোটোগল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি পুনরায় লক্ষ করা প্রয়োজন।
ছোটোগল্পের বৈশিষ্ট্য:-
পূর্বোক্ত 'বর্ষা যাপন' কবিতায় কবিগুরু ছোটোগল্পের আরও একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন-
"ছোটো প্রাণ ছোটো ব্যথা ছোটো ছোটো দুঃখ কথা" জীবনের চলমান স্রোত থেকে খন্ড খন্ড প্রতীতি আহরণ করবেন গল্পকার। এখানে বিন্দুতে হবে সিধু দর্শন।
* তত্ত্বকথা বা উপদেশ থাকবে না।
* একমুখিতা হবে এই গল্পের বৈশিষ্ট্য।
* বৃহত্তর সত্য, স্বল্পতম ব্যাপ্তির মধ্যে প্রতিফলিত হবে।
* "অন্তরে অতৃপ্তি রবে/সাঙ্গ করি মনে হবে/শেষ হয়ে হইল না শেষ"
* একটি মাত্র মহামুহূর্ত থাকবে এবং সমগ্র গল্পের উৎকণ্ঠা এর উপর নিবদ্ধ থাকবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'ছুটি' গল্পটি বিবেচ্য।
ছোটোগল্পরূপে সার্থকতা:-
গল্পকার আলোচ্য গল্পে ফটিকের সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় বন্ধন ও পরে বিচ্ছেদ-এই মূলভাব ও প্রতীতিকে নিয়ে গল্পের কাঠামো গড়ে তুলেছেন। ফলে ছোটোগল্পের একমুখিতার আদর্শ এখানে রক্ষিত হয়েছে। তবে পার্শ্ব উপকরণ হিসেবে গল্পে চিত্রিত হয়েছে ফটিকের কলকাতায় থাকাকালীন জীবনযাপনের কিছু খন্ড চিত্র। মামির উদাসীনতা ও নিষ্ঠুরতা, স্কুলে মাস্টারমশাইয়ের প্রহার, বই হারিয়ে ফেলা, মামাতো ভাইদের উপেক্ষা ইত্যাদি ফটিকের বেদনাকে আরও ঘনীভূত করে তুলেছে। সমগ্র গল্পে উৎকণ্ঠা দানা বেঁধেছে এই বিশেষ মুহূর্তটিতে- "যে অকূল সমুদ্রে যাত্রা করিতেছে, বালক রশি ফেলিয়া কোথাও তাহার তল পাইতেছে না।” ফটিকের এই মৃত্যুবর্ণনা গল্পকারের সংযত ভাষানৈপুণ্যের পরিচায়ক। এ ছাড়া দুর্যোগপূর্ণ বর্ষণমুখরিত সেই রাত্রির অশান্ত পরিবেশে ফটিকের মানসিক বিপর্যয়কে গল্পকার ও আবেদনস্পর্শী করে তুলেছেন।
উপসংহার:
'ছুটি' গল্পের মহৎ সত্য হল প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত মানবসত্তা প্রকৃতি থেকে বিচ্যুত হলে, সেই সভার অপমৃত্যু ঘটে। তাই গল্পের শেষে কোনো চমক নেই, আছে শাশ্বত জীবনসত্যের ধীর বিশ্বাস। ফলে 'ছুটি' গল্পটি যে একটি আদর্শ ছোটোগল্প হিসেবে বিবেচিত হবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।
প্রশ্ন ৭
রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' গল্প অবলম্বনে বিশ্বম্ভরবাবুর চরিত্রটির পরিচয় দাও। ৫
উত্তরঃ-
ভূমিকা:
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছুটি' গল্পের প্রধান চরিত্র তথা নায়ক ফটিক চক্রবর্তীর মামা বিশ্বম্ভরবাবু। গল্পের শুরুতেই একটি মজাদার ৪ খেলা আবিষ্কার করেও যখন মাখনের দুষ্ট জেদের কারণে খেলা ভঙ্গ হয়ে যায়, তখন ফটিক উদাস হয়ে নদীঘাটে একটি অর্ধনিমগ্ন নৌকার গলুইয়ের উপর বসে থাকে। সেইসময় একটি বিদেশি নৌকায় এক অপরিচিত ব্যক্তির আগমন ঘটে। পরে জানা যায় তিনিই বিশ্বম্ভরবাবু। গল্পকার প্রথমেই জানিয়ে দেন বিশ্বম্ভরবাবু মাঝবয়সি। তাঁর চুলগুলি পাকা হলেও গোঁফ কাঁচা। তিনি নদীঘাটে ফটিকের কাছে চক্রবর্তীদের বাড়ির ঠিকানা জানতে চান এবং ফটিকের ইশারায় সঠিক দিশা না পেয়ে চলে যান। বাড়িতে যখন ফটিক- মাখন-মায়ের বিবাদ তুঙ্গে, ঠিক তখনই সেই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে বিশ্বজরবাবু প্রবেশ করেন এবং বলেন, 'কী হচ্ছে তোমাদের।' বিবাদ সেই সময়ের জন্য থামে। জানা যায়, বিশ্বম্ভরবাবু পশ্চিমে কাজ করতে গিয়েছিলেন অনেকদিন। দেশে ফিরে বোনের খবর নিতে এসেছেন।
স্নেহশীল:
বিশ্বম্ভরবাবু বোনের প্রতি যেমন ছিলেন স্নেহপরায়ণ তেমনই তিনি সংবেদনশীল এক মানবিক চরিত্র। তিনি পশ্চিমে কর্মে লিপ্ত ছিলেন বলে বোনের পতি বিয়োগের সময় আসতে পারেননি। কিন্তু পরবর্তীকালে স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই স্নেহের আকর্ষণে বোনকে দেখতে আসেন।
কর্তব্যপরায়ণ:
বিশ্বম্ভরবাবুর এই আগমনে তাঁর দায়িত্ববোধ তথা কর্তব্যপরায়ণতার দিকটি খেয়াল করা যায়। তিনি বোনের সঙ্গে কথা বলে ভাগনেদের পড়াশোনা এবং মানসিক উন্নতির কথা জানতে চান। ফটিকের উচ্ছৃঙ্খলতা ও পড়াশোনায় অমনোযোগের কথা শুনে এবং বিধবা বোনের অসহায়তা বুঝে ফটিককে কলকাতায় নিজের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেন।
অবিবেচক:
ফটিক কলকাতার নাগরিক পরিবেশে থাকাকালীন যে দুঃসহ ব্যথা অন্তরে বহন করেছিল, তার শরিক হতে পারেননি বিশ্বম্ভরবাবু। স্নেহ, মায়া, মমতা ও সহানুভূতির বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ফটিকের জন্য তিনি তার সহৃদয়তারও কোনো পরিচয় দেননি। এমনকি ফটিকের মামির নিষ্ঠুর আচরণের প্রতিবাদ না করে তিনি নীরব দর্শক হয়েই থেকেছেন।
বাস্তবজ্ঞানহীন:
বিশ্বম্ভরবাবু ছিলেন এক বাস্তববোধহীন মানুষ। কারণ তাঁর নিজের তিনটি সন্তান থাকা সত্ত্বেও ভাগনে ফটিকের শিক্ষাদীক্ষার দায়িত্ব নিয়ে তিনি সংসারে এক মহাসংকট ডেকে আনেন। বিশ্বম্ভরবাবুর বাস্তবজ্ঞানহীনতার জন্যই কার্যত সহজসরল, মুক্ত প্রকৃতির লালিত সন্তান ফটিককে জীবনাহুতি দিতে হয়েছে।
মানবদরদি:
গল্পের শেষে বিশ্বম্ভরবাবুকে আবার মানবিক হতে দেখা যায়। ফটিক বাড়ি থেকে পলায়ন করলে তিনি পুলিশকে খবর দেন। অসুস্থ অবস্থায় পুলিশ ফটিককে ধরে আনলে তিনি তাকে কোলে করে অন্তঃপুরে নিয়ে যান। ফটিকের জ্বর বাড়লে তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে ডাক্তার ডাকেন এবং ফটিকের মাকে আনতে পাঠান। গল্পে তিনি যেটুকু উপস্থিত থেকেছেন, তাতে তাঁর কর্তব্যপরায়ণতা, স্নেহশীলতা যেমন প্রকাশিত হয়েছে তেমনই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর মানবিক হৃদয়বৃত্তিগুলিও।
উপসংহার:
সবশেষে বলা যায় যে, ফটিকের মামা বিশ্বম্ভরবাবুর চরিত্রটি যাবতীয় মানবিক গুণসম্পন্ন হয়েও ফটিকের জীবনকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রে এক ব্যর্থ কারিগররূপেই চিত্রিত হয়েছে।
প্রশ্ন ৮
'ছুটি' গল্পে গ্রাম ও শহরের দ্বন্দ্ব কীভাবে ফুটে উঠেছে, তা আলোচনা করো। ৫
উত্তরঃ-
ভূমিকা:
ব্যক্তিজীবনে চোখে দেখা একটি সামান্য ঘটনাকে কল্পনার রসে জারিত করে অভিজ্ঞতা আর অনুভবের যথাযথ মেলবন্ধনে রবীন্দ্রনাথ নির্মাণ করেছেন 'ছুটি' গল্পটি। ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ নগর কলকাতায় জন্মগ্রহণ করার সুবাদে প্রত্যক্ষ করেছেন নাগরিক মনের সংকীর্ণতা। অন্যদিকে, জমিদারি দেখাশোনার কাজে পল্লিবাংলার প্রকৃতিলগ্ন পরিবেশে অগণিত সহজসরল মানুষের সান্নিধ্য তাঁর মধ্যে গড়ে তুলেছিল অন্য অনুভবের জগৎ। 'ছুটি' গল্পের কাহিনিবৃত্তটিকে রবীন্দ্রনাথ স্থাপন করেছেন গ্রাম-শহরের সেই দ্বান্দ্বিক পটভূমিতে। গ্রামে থাকাকালীন গ্রামীণ মুক্তি ফটিক আলাদা করে উপলব্ধি করতে পারেনি। প্রকৃতি সান্নিধ্যের মর্ম বুঝে ওঠার আগেই মায়ের ভর্ৎসনায়, বয়ঃসন্ধির দ্বন্দ্বে কাতর ফটিক স্বেচ্ছায় শহরে চলে আসতে চায়। তবে শহরে তার সর্বসুখপ্রাপ্তির স্বপ্নভঙ্গ হয় নিমেষেই। মামাবাড়িতে এসেই সে বুঝতে পারে মামির সংসারে তার উপস্থিতি উপদ্রব ছাড়া আর কিছু না। গ্রামের মুক্তাঙ্গনে বিচরণকারী ফটিক এক লহমায় শহরের চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দি হয়ে নিজের স্বতঃস্ফূর্ততা, সহজ চাপল্য হারিয়ে ফেলে। ক্ষতবিক্ষত অন্তর নিয়ে সে বুঁদ হয়ে থাকে গ্রামের কল্পনায়।
গ্রাম ও শহরের দ্বন্দ্ব:
'ছুটি' নায়ক কিশোর ফটিক বড়ো উঠেছে পল্লিবাংলার উদার-উন্মুক্ত পরিবেশে। শহরের বন্দিজীবন থেকে ফটিক ঘুড়ি ওড়ানোর বিস্তৃত মাঠ, সাঁতার কাটার সংকীর্ণ স্রোতস্বিনী, অকর্মণ্যভাবে ঘুরে বেড়ানোর সীমাহীন নদীতীরটির প্রতি আশ্চর্য আকর্ষণ অনুভব করেছে। সে গ্রামে নিজের বাড়িতে ফেরার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। যদিও দুর্ভাগ্যবশত তার আর গ্রামে ফেরা হয়নি, তবু মৃত্যুপথযাত্রী ফটিক হৃদয়হীন শহর থেকে ছুটি নিতে চেয়েছে চিরতরে। গ্রাম ও শহরের এই দ্বান্দ্বিক পটভূমিতেই ফটিকের মর্মান্তিক পরিণতি একটি চিরকালীন সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।
প্রশ্ন ১০
"এ প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিল।"- কোন্ প্রস্তাব, কে অনুমোদন করল? উদ্ধৃত্তাংশটির তাৎপর্য নিরূপণ করো। ৩+২
উত্তরঃ-
প্রস্তাব:
প্রশ্নোদ্ভূত অংশটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'ছুটি' গল্প থেকে গৃহীত। এখানে নদীর ধারে খেলায় রত বালকদের কথা বলা হয়েছে। ছেলেদের দলের সর্দার ফটিক চক্রবর্তী খেলতে খেলতে প্রস্তাব করে যে, নদীর ধারে একটা শাল গাছের গুঁড়ি, যা মাণ্ডুলে পরিণত হওয়ার জন্য অপেক্ষারত ছিল; সেটিকে তারা গড়িয়ে গড়িয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবে। অনুমোদনকারী: এরকমটা করা হলে, এটি যে ব্যক্তির প্রয়োজনের কাঠ তিনি কাঠটিকে স্বস্থানে দেখতে না পেয়ে যে ভীষণ বিব্রত হবেন; তা কল্পনা করেই বালকদল, ফটিকের প্রস্তাবকে সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন করেছিল।
তাৎপর্য:
ফটিক পিতৃহারা সন্তান। তাই যথোচিত শাসনের বালাই তার প্রতি ছিল না। মায়ের অনাদর ও উপেক্ষা উভয়ই তার মনে দাগ কেটেছিল। কিশোরবয়সী এই ছেলেটি অন্যান্য ছেলেদের মতো বা তাদের চেয়েও দুষ্টুমিতে পারদর্শী। খেলতে গিয়ে বড়ো গাছের গুঁড়িটাকে অন্যত্র সরিয়ে দিলে প্রয়োজনে মালিক বিব্রত বোধ করবে, সেটা খুঁজে বেড়াবে-এই আনন্দেই সে মশগুল ছিল। তার এইরূপ ভাবধারায় ভাবিত ছিল, খেলার সকল সঙ্গীরাও। নিজেদের খেলার মাধ্যমে একজন বড়ো মানুষকে বিরক্ত করতে পারার অসীম আনন্দের কথাই বর্ণিত হয়েছে গল্পের এই অংশে।
প্রশ্ন ১১
"এইরূপ উদার ঔদাসীন্য দেখিয়া কিছু বিমর্ষ হইয়া গেল”- কে বিমর্ষ হয়ে গেল এবং কার ঔদাসীন্যের কথাই বা বলা হয়েছে? উদ্ধৃতাংশের নিরিখে বিষয়টি পরিস্ফুট করো। ২+৩
উত্তর:-
যে বিমর্ষ হয়ে গেল:
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গল্পগুচ্ছ' গ্রন্থের প্রথম খন্ডের অন্তর্গত আমাদের পাঠ্য 'ছুটি' গল্পটি থেকে উদ্ধৃতাংশটি গৃহীত হয়েছে। উক্ত অংশে ক্রীড়ায় মত্ত ছেলের দলের বিমর্ষ হওয়ার কথা বলা হয়েছে।
উদাসীন যে:
আলোচ্য অংশে ফটিকের ছোটোভাই মাখনলালের ঔদাসীন্যের কথা বলা হয়েছে।
প্রতিপাদ্য বিষয়:
ফটিকের অভিনব দুষ্টুমি:
নদীর ধারে ছেলের দলের সর্দার ফটিক ও তার সঙ্গীরা খেলায় মত্ত ছিল। এমতাবস্থায় শুকনো বড়ো শাল গাছের গুঁড়ি তাদের নজরে পড়ামাত্র ফটিকের মনে নতুন ভাবনার উদয় হয়। তারপর তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, সেটিকে সকলে মিলে গড়িয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবে।
মাখনলালের প্রবেশ ও খেলাভঙ্গ:
শাল কাঠটিকে গড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার আনন্দ অপেক্ষা সেই কাঠের মালিককে বিব্রত করার আনন্দই তাদের কাছে বেশি। যে মুহূর্তে তারা; তাদের সেই চিন্তাকে বাস্তবায়িত করার পথে অগ্রসর হয়, ঠিক সেইসময় ফটিকের কনিষ্ঠ মাখনলাল সেই গুঁড়ির উপর গিয়ে বসে পড়ে। তার এই কান্ড দেখে ছেলের দল প্রাথমিকভাবে কিছুটা বিমর্ষ হয়ে পড়ে কারণ তারা মাখনলালের আসার অনেক আগে থেকেই সেখানে খেলাধুলা করছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনুমতি ছাড়াই মাখনলাল তাদের খেলায় ব্যাঘাত ঘটাল, সেই ভেবেই বালকদল কিছুটা বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল।
প্রশ্ন ১২
"সেই অকাল-তত্ত্বজ্ঞানী মানব সকল প্রকার ক্রীড়ার অসারতা চিন্তা করিতে লাগিল"-এখানে কাকে 'অকাল-তত্ত্বজ্ঞানী মানব' বলা হয়েছে তা সমগ্র বিষয় অবলম্বনে নিজের ভাষায় ব্যক্ত করো। ৫
উত্তর:-
উদ্দিষ্ট ব্যক্তি:
রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' গল্পে ফটিকের ভাই মাখনকেই 'অকাল-তত্ত্বজ্ঞানী মানব' বলা হয়েছে।
ব্যাখ্যা:
প্রশ্নোদ্ভূত অংশটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'ছুটি' শীর্ষক রচনাংশ থেকে গৃহীত হয়েছে। নদীর ধারে ফটিক এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গরা মিলে একটি কাঠের গুঁড়িকে অন্যত্র সরানোর চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল। তা গড়িয়ে গড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার আনন্দ এবং তার সঙ্গে মালিকের আসন্ন বিরক্তি-এসব মিলিয়ে তারা যখন ব্যস্ত, এমন সময় ফটিকের ছোটোভাই মাখনলাল সেখানে প্রবেশ করে এবং নির্দ্বিধায় সেই গাছের গুঁড়িটি দখল করে বসে পড়ে। এতে ছেলের দল প্রাথমিকভাবে মুষড়ে পড়লেও নতুন খেলার ভাবনায় তারা সকলে খুব উজ্জ্বল ও উচ্ছল হয়ে ওঠে। মাখনকে সরানোর জন্য একটু ঠেলেও দেয়। কিন্তু হিতে বিপরীত হয়। মাখন সেখান থেকে না নেমে আরও চেপে বসে। শিশুসুলভ কোনো আচরণ তার মধ্যে থাকে না, খেলার নির্মল আনন্দও সে উপভোগ করে না। এমনকি এক মুহূর্তের জন্যও মাখনের এটা মনে হয় না যে, যদি এরপর সেই গুঁড়িটা সজোরে ঠেলে দেওয়া হয় তবে সে আহতও হতে পারে। মাখনের মনোজগতের এই নির্বিকার হৃদয়ভাবনা প্রসঙ্গে লেখক এই প্রশ্নোদ্ভূত উক্তিটি করেছেন।
প্রশ্ন ১৩
"তাহাতে আর একটু বেশি মজা আছে।"-প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা করে 'বেশি মজা'-টি কীরূপ, তার পরিচয় দাও। ৫
উত্তরঃ-
ব্যাখ্যা:
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'ছুটি' শীর্ষক রচনাংশে ফটিক এবং তার খেলার সঙ্গীরা একটা শাল গাছের গুঁড়িকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার অভিপ্রায়ে অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়। শুধু তাই নয়, এই কাজে ওই গুঁড়ির মালিককে বিব্রত করার বাসনায় তারা মজা পেল। সেই অনুযায়ী তাদের খেলার প্রক্রিয়া চালু হয়। ইতিমধ্যেই কোনোরকম সংশয় প্রকাশ না করে ফটিকের ভাই মাখন সেই গুঁড়িটা দখল করে। তাকে একটু-আধটু ঠেলে দিয়ে সেই ছেলের দল, গুঁড়ি থেকে নামানোর চেষ্টা করে মাখনকে। কিন্তু সে তো নামেই না, বরং নড়েচড়ে আরও চেপে বসে।
'বেশি মজা'-টির পরিচয়:
মাখনের এহেন কীর্তিকলাপে অত্যন্ত রাগান্বিত হওয়া সত্ত্বেও ভাইকে মারতে পারে না ফটিক। বরং ভাইকে জব্দ করার জন্য সে অন্য কৌশল অবলম্বন করে। আশু বিপদের কোনো সম্ভাবনার কথা বিবেচনা না করেই সে বলে ওঠে-মাখনকে সুদ্ধ ওই কাঠ গড়ানো আরম্ভ করা যেতে পারে। যেহেতু একটু-আধটু ঠেলা খেয়েও মাখন সেই
গুঁড়ি থেকে নেমে যায়নি, তাই কিছুটা ক্রোধান্বিত হয়েই ফটিক এই সিদ্ধান্ত { নেয়। তার মনে হয় এই বিষয়টা তাদের আরও বেশি আনন্দ দেবে। সেই প্রসঙ্গেই উক্তিটি করেছেন কথক।
প্রশ্ন ১৪
খেলার আরম্ভেই এইরূপ আশাতীত ফল লাভ করিয়া অন্যান্য বালকেরা বিশেষ দৃষ্ট হইয়া উঠিল," কোন্ খেলার কথা বলা হয়েছে? বিশেষ দৃষ্ট হওয়ার কারণটি কী তা পাঠ্যাংশ অনুসরণে ব্যক্ত করো। ২+৩
উত্তরঃ-
যে খেলা:
রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' গল্পে নদীর ধারে পড়ে থাকা প্রকান্ড একটা শাল কাঠকে, স্বস্থান থেকে গড়িয়ে নিয়ে গিয়ে গুঁড়িটির মালিককে বিব্রত করার যে খেলাটি ফটিকের মাথায় এসেছিল, সেই খেলার কথা বলা হয়েছে।
আশাতীত ফল ও সৃষ্ট হওয়ার কারণ:
বালকদিগের খেলায় ভঙ্গ দিতে ফটিকের কনিষ্ঠ মাখন, শালের গুঁড়িটির উপর এসে বসে পড়ে। তাকে একটু-আধটু ঠেলা হলেও সে না উঠলে ফটিকের মাথায় আরও মজার একটি খেলার চিন্তা আসে। মাখনকে সুদ্ধই সে গুঁড়িটি গড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়। ফটিক সর্দারের কথামতোই সকলে মিলে গুঁড়িটি ঠেলতে শুরু করলে মাখন মাটিতে পড়ে যায়, এটিই ছিল আশাতীত ফল।
সকলে মাখনকে শায়েস্তা করার জন্যই গুঁড়িটি ঠেলা শুরু করে। এর ফলে যে মাখনের গাম্ভীর্য চূর্ণ হয়ে সে এরূপ জব্দ হবে, তা কেউ আশা করেনি। তথাপি মাখনের এই দুরবস্থা দেখে ফটিক ব্যতীত আর সকল বালকই মনে মনে হৃষ্ট হয়েছিল।
প্রশ্ন ১৫
'ছুটি' গল্পে মামাবাড়িতে গিয়ে ফটিকের যে দুরবস্থা হয়েছিল তা নিজের ভাষায় লেখো। [HS Model Question 24] ৫
অথবা,
"দেয়ালের মধ্যে আটকা পড়িয়া কেবলই তাহার সেই গ্রামের কথা মনে পড়িত।"-কার, কী কারণে গ্রামের কথা মনে পড়ত? ৫
উত্তরঃ-
যার মনে পড়ত:
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'ছুটি' গল্প থেকে - নেওয়া উদ্ধৃত অংশে গ্রামের কথা পড়েছে গল্পের প্রধান চরিত্র তথা নায়ক ফটিকের।
কারণ:
আলোচ্য গল্পে আমরা দেখি কিশোর ফটিক গ্রামের প্রকৃতিলগ্ন উদার-উন্মুক্ত পরিবেশে স্বাধীনভাবে বড়ো হয়ে উঠেছে। কিন্তু পরিবারে সে • মায়ের স্নেহ-মমতা-ভালোবাসা থেকে আপাতভাবে বঞ্চিত থেকেছে। মায়ের তিরস্কার, ভর্ৎসনা আর বয়ঃসন্ধিকালে নিজের প্রকৃতিকে উপলব্ধি করতে - না পারার কারণে সে তার মামার সঙ্গে কলকাতা যাওয়ার প্রস্তাবে রাজি হয়ে গিয়েছে। কলকাতায় মামার বাড়িতে এসে মামির হৃদয়হীন আচরণে, * মামাতো ভাইদের অবজ্ঞায়, শহরের চারদেয়ালের বন্দিজীবনে অল্পদিনেই সে হাঁফিয়ে উঠেছে। একদিকে কিশোর মনের স্নেহবুভুক্ষা, অন্যদিকে মামাবাড়ির অপরিচিত পরিমণ্ডলে সীমাহীন অনাদর ফটিককে মর্মাহত করেছে। গ্রামজীবনের সেই উদার-উন্মুক্ত প্রকৃতিলগ্ন জীবনের প্রতি ফটিক অমোঘ আকর্ষণ অনুভব করেছে। শহরজীবনের অপরিসীম অবজ্ঞা আর নির্মমতা থেকে সেই মুহূর্তে তার ফিরে যেতে ইচ্ছে হয়েছে নিজের সাম্রাজ্যে- যেখানে রয়েছে ঘুড়ি ওড়ানোর উন্মুক্ত আকাশ, সাঁতার কাটার সংকীর্ণ স্রোতস্বিনী, অকর্মণ্যভাবে ঘুরে বেড়ানোর সেই আদিগন্ত মাঠ, সীমাহীন নদীতীর। এমনকি 'অত্যাচারিণী', 'অবিচারিণী' মায়ের স্মৃতিও সেই ক্ষণে তার বন্দিজীবনে একটুখানি বাতাস বয়ে এনেছে। রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য গল্পে দেখিয়েছেন, প্রকৃতির সঙ্গে যার গভীর সংযোগ; প্রকৃতি যার সত্তার গঠনে বড়ো ভূমিকা পালন করেছে-তাকে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করলে পরিণতি মর্মান্তিক হতে পারে। মামাবাড়িতে এসে তাই ফটিকের অবস্থা হয়েছিল মাতৃহীন এক দুগ্রহ বৎসের মতো।
প্রশ্ন ১৬
"আনুষঙ্গিক যে বিপদের সম্ভাবনাও আছে, তাহা তাহার কিংবা আর-কাহারও মনে উদয় হয় নাই।"-কোন্ বিপদের কথা বলা হয়েছে? উদ্ধৃতিটির পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি পরিস্ফুট করো। ২+৩
উত্তর:-
আসন্ন বিপদ:
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছুটি' গল্পে দেখা যায়- মাখন যথাসময়ে নদীর ধারে গাছের গুঁড়ি দখল করে নেওয়ায় রাগান্বিত হয়ে নিজের ভাইকে সেখান থেকে সরানোর জন্য ফাঁদ তৈরি করে ফটিক। কিন্তু তার ফলস্বরূপ সে যে আঘাত পেতে পারে, সে-কথা কারও মাথায় আসেনি। মাখনের আঘাত পাওয়াকেই এখানে বিপদ বলা হয়েছে।
প্রতিপাদ্য বিষয়:
মাখনের একগুঁয়েমি স্বভাব:
গাছের গুঁড়িটি যখন মাখন নিজের কুক্ষিগত করে নেয়, সেইসময় তাকে ভয় পাওয়ানোর জন্য একজন কিশোর আস্তে করে গাছের গুঁড়িটিকে ঠেলে দেয়। সকলে ভেবেছিল হয়তো মাখন ভয় পেয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যাবে কিন্তু একদমই তা হয়না, বরং সে- "আরো একটু নড়িয়া চড়িয়া আসনটি বেশ স্থায়ীরূপে দখল করিয়া লইল" ।
আনুষঙ্গিক বিপদের কথা না ভেবে বালকদের নির্বুদ্ধিতার পরিচয়:
ভাইকে জব্দ করার লক্ষ্যে ফটিক অন্য কৌশল অবলম্বন করে। আসন্ন বিপদের সম্ভাবনার কথা বিবেচনা না করেই সিদ্ধান্ত নেয়, মাখনকে সুদ্ধ ওই কাঠ গড়িয়ে নিয়ে চলবে তারা। শুধুমাত্র খেলার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয় ছেলের দল। আশু বিপদের সম্ভাবনা সম্পর্কে কোনোরূপ স্বচ্ছ ধারণাই তৈরি হয় না ফটিক বা তার সঙ্গীদের। তাদের এইরূপ মানসিক পরিস্থিতি ও নির্বুদ্ধিতার বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক উদ্ধৃত মন্তব্যটি উল্লেখ করেছেন।
প্রশ্ন ১৭
"সেও সর্বদা মনে মনে বুঝিতে পারে, পৃথিবীর কোথাও সে ঠিক খাপ খাইতেছে না।"-বয়ঃসন্ধিতত্ত্ব 'ছুটি' গল্পটিকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে, তা উদ্ধৃতিটির আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৫
উত্তরঃ-
সূচনা:
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জগৎ ও জীবনকে দেখার স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি, মানুষের প্রতি অগাধ সহানুভূতি রবীন্দ্রসাহিত্যে উপস্থিত করেছে রকমারি চরিত্রকে। রবীন্দ্রনাথের হাত ধরেই বাংলা সাহিত্য পৌঁছে গিয়েছিল মানুষের মনের কারখানায়। জাত-ধর্ম, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রায় সববয়সের চরিত্রের অন্তরে আলো ফেলে অসাধারণ দক্ষতায় রবীন্দ্রনাথ তাদের নির্মাণ করেছেন নিজের সৃষ্টিতে। যেমন 'ছুটি' গল্পে কিশোর ফটিকের মধ্যে ফুটে উঠেছে বয়ঃসন্ধির বৈশিষ্ট্য।
বয়ঃসন্ধির দোরগোড়ায় ফটিক:
আলোচ্য গল্পের নায়ক ফটিকের বয়স তেরো-চোদ্দো বছর। প্রকৃতির অপার আনন্দে দিব্যি চলছিল তার দিনযাপন। কিশোর মন মূলত সর্বদাই স্নেহ-মমতা-ভালোবাসার কাঙাল হয়। প্রকৃতির শ্যামলাঞ্চলে অগাধ স্বাধীনতায় যতখানি আনন্দে ছিল ফটিক, বাড়িতে মায়ের স্নেহাঞ্চল থেকে সে যেন ততখানিই বঞ্চিত ছিল। ভাই মাখনের প্রতি মায়ের অতিরিক্ত ভালোবাসা এবং তার প্রতি মায়ের উপেক্ষা-অত্যাচার- উদাসীনতা ফটিকের মনে জন্ম দিয়েছিল অভিমানের। আর এই অভিমান থেকেই যেন সে মামার সঙ্গে কলকাতা যেতে রাজি হয়েছিল। অবশ্য এর সঙ্গে ছিল বয়ঃসন্ধিজনিত কারণে নিজেকে বুঝতে না পারার দ্বন্দ্ব। আবার কলকাতার হৃদয়হীন বাতাসে এবং মামির স্নেহশূন্য সান্নিধ্যে ফটিক অল্পদিনেই বুঝে যায়, শহুরে জীবনের জটিলতায় সে বড্ড বেমানান।
বয়ঃসন্ধিতত্ত্ব ও 'ছুটি' গল্পের মর্মান্তিক পরিণতি:
রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য গল্পে লিখেছেন- "বিশেষত, তেরো-চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মতো পৃথিবীতে বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোনো কাজেও লাগে না। স্নেহও উদ্রেক করে না, তাহার সঙ্গসুখও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধো-আধো কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথামাত্রই প্রগল্ভতা।” এ গল্পে বয়ঃসন্ধির এই যে সংকটের কথা লেখক তুলে ধরেন, বোঝা যায় এই সংকটই গল্পের পরিণতিকে মর্মান্তিক করে তোলে। বয়ঃসন্ধির কারণেই ফটিক নিজেকে বুঝতে পারে না। শহর জীবনের বন্দিদশা থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় তার অন্তর ক্ষতবিক্ষত হয়। মামির সংসারে তার অবাঞ্ছিত উপস্থিতিতে সে নিজেই লজ্জিত। ক্রমে সে নিজেকে গুটিয়ে নিতে থাকে নানা দ্বিধায়। ফটিকের এই বয়ঃসন্ধিজনিত মানসিক দ্বন্দ্ব, গল্পটিকে মর্মান্তিক গন্তব্যে পৌঁছে দেয়। ফটিকের আচরণের মধ্য দিয়ে বয়ঃসন্বিতত্বের প্রভাব 'ছুটি' গল্পে অসামান্য দক্ষতায় ফুটিয়ে তোলেন রবীন্দ্রনাথ।
প্রশ্ন ১৮
"নিজের হীনতা এবং দৈন্য তাহাকে মাটির সহিত মিশাইয়া ফেলিল"- উল্লিখিত চরিত্রের 'হীনতা' ও 'দৈন্য'-এর পরিচয় দাও। ৫
উত্তর:-
হীনতা ও দৈন্যের পরিচয়:
রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি' গল্পে ফটিকের পরিস্থিতি ব্যক্ত করতে উদ্ধৃত মন্তব্যটি করেছেন গল্পকার।
নতুন পরিবেশের তিক্ত অভিজ্ঞতা:
সুশিক্ষা ও যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠার অভিপ্রায়ে ফটিকের মামা ফটিককে গ্রাম থেকে শহরে নিয়ে আসেন। তাকে যথাযথ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য যে স্কুলে তার সন্তানেরা শিক্ষা নিচ্ছিল, সেখানেই নির্বিবাদে ভরতি করে দেন ফটিককেও। কিন্তু প্রতিমুহূর্তে মামির উপেক্ষা ও বকুনি ফটিককে বিদ্ধ করে। একে তো নতুন পরিবেশ, তার উপর বহুদিন মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হওয়ায় মন ভেঙে যেতে লাগল তার। অবশেষে অনেক সাহস জুগিয়ে মামার কাছে গ্রামে যাওয়ার অভিপ্রায় জানালে মামা স্পষ্টতই জানিয়ে দেন, কেবল পুজোর সময় সে বাড়ি যেতে পারবে- এতে যেন আরও মর্মাহত হল ফটিক।
মামির তিরস্কার:
ইতিমধ্যেই ফটিক বই হারিয়ে ফেলায় স্কুলে শাস্তি ও হেনস্থায় বাধ্য হয়ে মামিকে বইয়ের কথা জানিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে মামির চরম তিরস্কার তাকে নিজের চোখেই অপরাধী করে তোলে।
ব্যথিত হৃদয়ের হীনতা ও 'দৈন্য:
এইসকল বিচ্ছিন্ন ঘটনায় ফটিকের অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে ওঠে এই ভেবে যে, সে অন্যের পয়সা অনর্থক নষ্ট করছে। তাই মায়ের উপর অত্যন্ত অভিমান হয়-কেন তাকে মামার বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছেন মা। এইরূপ নানা চিন্তাভাবনায় জর্জরিত ফটিকের ব্যথিত বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক 'হীনতা' ও 'দৈন্য' শব্দ দুটির ব্যবহার করেছেন।
প্রশ্ন ১৯
"রোগের সময় এই অকর্মণ্য অদ্ভুত নির্বোধ বালক পৃথিবীতে নিজের মা ছাড়া আর-কাহারও কাছে সেবা পাইতে পারে, এরূপ প্রত্যাশা করিতে তাহার লজ্জা বোধ হইতে লাগিল"- নির্বোধ বালক কাকে বলা হয়েছে এবং সেই বালকের এরূপ ভাবনার কারণ কী? ৫
উত্তর:-
উত্তর নির্বোধ বালক:
গল্পকার রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছুটি' গল্পে বালকদের সর্দার ফটিক চক্রবর্তীকেই এখানে নির্বোধ বালক বলে অভিহিত করেছেন।
ভাবনার কারণ:
সন্তানের প্রতি মায়ের স্নেহ-বাৎসল্য ও মমত্ববোধ বিশ্বব্যাপী অভিনন্দিত হয়। ফটিকের বিরুদ্ধে তার মায়ের অভিযোগ ছিল যে, পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে এই সন্তানটি অতিষ্ঠ করে তুলেছে। কিন্তু মায়ের গভীর স্নেহ-বাৎসল্যের ফল্গুধারাটি তার অন্তরে সতত প্রবাহিত ছিল। তা ছাড়া প্রকৃতিপ্রেমিক ফটিক উপলব্ধি করেছে, মায়ের স্নেহ- প্রীতিহীন বিচ্ছিন্ন জীবন তার কাছে দুর্বিষহ। স্কুলে শিক্ষকের প্রহার, বই হারানোর ফলে মামির অপমান, মামাতো ভাইদের উপেক্ষা ইত্যাদি বিষয় তার অন্তরের পীড়াকে আরও ত্বরান্বিত করেছে। ফলে জ্বরে আক্রান্ত ফটিক একদিন মামার বাড়ি থেকে পলায়ন করে। কারণ স্নেহহীন মামার বাড়ি ছিল তার নরকযন্ত্রণার শামিল। মায়ের উন্ন স্পর্শ পেতে সে উদ্গ্রীব হয়ে ওঠে, মায়ের যত্নই তার মহৌষধ হতে পারে এমনটাই বোধ করে ফটিক। তার মান-অভিমান, অপমান, হীনম্মন্যতাবোধ, লজ্জা- এসব কিছুই বিস্মৃত হয়ে মায়ের সান্নিধ্যে মন অফুরন্ত স্নেহধারায় ভরে উঠবে। রোগজ্বালায় কাতর ফটিকের এমনটাই মনে হয়েছিল।
রবীন্দ্রনাথ কৈশোরের মানসিক উদ্দীপনা বা চঞ্চলতাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য স্নেহবিচ্যুত আত্মার এই নির্বোধ ক্রন্দনধ্বনি ফটিক চরিত্রে রূপায়িত করেছেন।