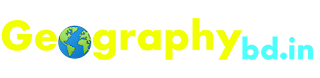একাদশ শ্রেণী ইতিহাস দ্বিতীয় সেমিস্টার, পঞ্চম অধ্যায় পরিবর্তনশীল ঐতিহ্য (Changing Traditions) প্রশ্ন উত্তর | Class 11, 1st semester History, Fifth Chapter । WBCHSE । Oitijher Poriborton
শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা আলোচনা করবো একাদশ শ্রেণীর ইতিহাস বিষয়ের পঞ্চম অধ্যায় ঐতিহ্যের পরিবর্তন নিয়ে। আশাকরি তোমরা একাদশ শ্রেণীর দ্বিতীয় সেমিস্টারের এই ঐতিহ্যের পরিবর্তন অধ্যায়টি থেকে যেসব প্রশ্ন দেওয়া আছে তা কমন পেয়ে যাবে। আমরা এখানে একাদশ শ্রেণীর, দ্বিতীয় সেমিস্টারের ইতিহাস বিষয়ের পঞ্চম অধ্যায় ঐতিহ্যের পরিবর্তন এর SAQ, শূন্যস্থান পূরণ, এক কথায় উত্তর দাও, Descriptive, ব্যাখ্যা মুলক প্রশ্নোত্তর , সংক্ষিপ্ত নোট এগুলি দিয়েছি। এর পরেও তোমাদের এই ঐতিহ্যের পরিবর্তন অধ্যায়টি থেকে কোন অসুবিধা থাকলে, তোমরা আমাদের টেলিগ্রাম, হোয়াটসাপ , ও ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারো ।
অধ্যায় ৫ - পরিবর্তনশীল ঐতিহ্য (Changing Traditions) অধ্যায়ের সকল প্রশ্ন ও উত্তর
1. ক্রুসেড কী?
অথবা,
ক্রুসেড বলতে কী বোঝো?
উত্তর:-
▶ 'ক্রুসেড' কথার অর্থ 'ধর্মযুদ্ধ'। 'ক্রুসেড' (Crusade) কথাটি এসেছে লাতিন Crux শব্দ থেকে।
★ সংজ্ঞা:
বিধর্মী মুসলমানদের অধিকার থেকে পবিত্র তীর্থভূমি জেরুজালেম তথা প্যালেস্টাইন উদ্ধারের জন্য পোপ ও রোমান সম্রাটদের নেতৃত্বে প্রায় 200 বছর ধরে যে সামরিক অভিযান চলে, তাকেই বলা হয় 'ক্রুসেড' বা 'ধর্মযুদ্ধ'।
অন্যভাবে বলা যায় যে, জেরুজালেমের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে ইউরোপের খ্রিস্টান জগৎ ও প্রাচ্যের মুসলমানদের মধ্যে একাদশ শতক থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত যে লড়াই চলেছিল, তাকেই বলা হয় ক্রুসেড। উল্লেখ্য যে, এরূপ মোট ৪টি ক্রুসেড হয়েছিল।
2. ক্রুসেডের মূল তিনটি উদ্দেশ্য কী ছিল?
উত্তর:-
▶খ্রিস্টানদের ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের মূল তিনটি উদ্দেশ্য ছিল -
① পবিত্র তীর্থভূমি জেরুজালেমকে বিধর্মী মুসলমানদের হাত থেকে উদ্ধার করা।
② ক্রুসেডের সাফল্যলাভের মধ্য দিয়ে সমকালীন পোপরা চেয়েছিলেন পূর্বাঞ্চলীয় রোমান চার্চগুলির ওপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে।
③ ক্রুসেডে দলে দলে বহু সাধারণ মানুষ যোগদান করেছিল। তাদের উদ্দেশ্য। ছিল ধর্মযুদ্ধে যোগদান করে পুণ্যলাভ করা, তথা মৃত্যুর পর স্বর্গলাভ করা।
3. তৃতীয় ক্রুসেডকে কেন 'রাজাদের যুদ্ধ' বলা হয়?
উত্তর:-
▶ তৃতীয় ক্রুসেডকে 'রাজাদের যুদ্ধ' বলার কারণ-এই ক্রুসেডে
পবিত্র রোমান সম্রাট প্রথম ফ্রেডারিক বা ফ্রেডারিক বারবারোসা-সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশের রাজারা যোগদান করেছিলেন। সেই তালিকায় ছিলেন ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগাস্টাস এবং ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম রিচার্ড, তিনি 'Rechard the lion heart' বা 'সিংহ হৃদয় রিচার্ড' নামে পরিচিত ছিলেন।
4. সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে ক্রুসেডের কী প্রভাব পড়েছিল বলে তোমার মনে হয়?
উত্তর:-
▶ ক্রুসেডারদের বীরত্ব, ত্যাগস্বীকার ও বিচিত্র অভিজ্ঞতার বিবরণ ইউরোপের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। মুসলমানদের চিকিৎসার ব্যাপারে অসাধারণ দক্ষতা খ্রিস্টানদের মুগ্ধ করে। তারা মুসলমানদের কাছ থেকে শেখে '০'-র ব্যবহার, বীজগণিত ও প্রাচ্যের দর্শন। ক্রুসেডের সময় পশ্চিম ইউরোপের খ্রিস্টানরা মুসলমানদের উন্নত সভ্যতা ও বিলাসবহুল জীবনযাত্রার সংস্পর্শে আসে। তারা মুসলমান এবং পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের বিত্তবান শ্রেণির সংস্পর্শে এসে বহু নতুন ধরনের খাদ্য, ফলমূল, মশলা, কাগজ, চিনি, কাচের জিনিসপত্র, মসলিন, ওষুধপত্র, রং, পোশাক, বিলাসদ্রব্য, আসবাবপত্র, শিল্প ও স্থাপত্যরীতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে। প্রাচ্য দ্রব্যে বিত্তবান খ্রিস্টানদের ঘর ভরে যায়। বহু বিদেশি শব্দ গ্রহণ করায় পশ্চিম ইউরোপের ভাষাগুলিও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।
5. রেনেসাঁ কী? অথবা, রেনেসাঁ বলতে কী বোঝো?
উত্তর:-
►রেনেসাঁ (Renaissance) কথাটি এসেছে ফরাসি Renaistre শব্দ থেকে, যার অর্থ 'নবজাগরণ'।
★ সংজ্ঞা: পঞ্চদশ শতকের ইউরোপে গ্রিক-লাতিন ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে সাহিত্য, ললিতকলা, জ্ঞানবিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি ক্ষেত্রে এক নবচেতনার স্ফুরণ ঘটে। ইউরোপীয় ভাবজগতের এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনকেই বলা হয় রেনেসাঁ। অন্যভাবে বলা যায়, এই সময় গ্রিক ও লাতিন সংস্কৃতির প্রভাবে ইউরোপীয় মননে এক উদার, ধর্মনিরপেক্ষ ও যুক্তিবাদী নতুন ভাবধারার অনুপ্রবেশ ঘটে। এই ঐতিহাসিক ঘটনাই রেনেসাঁ বা নবজাগরণ বা নবজাগৃতি নামে খ্যাত।
6. ক্যারোলিঞ্জিয়ান রেনেসাঁর স্বরূপ আলোচনা করো।
উত্তর:-
▶ পন্ডিতদের মতে পবিত্র রোমান সম্রাট শার্লেম্যানের রাজত্বকালে, অর্থাৎ নবম শতকের প্রথম দিকে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক জগতে এক স্ফুরণ ঘটেছিল। এই স্ফুরণকেই বলা হয় ক্যারোলিঞ্জিয়ান রেনেসাঁ।
* ক্যারোলিঞ্জিয়ান রেনেসাঁর স্বরূপ:
① শার্লেম্যানের রাজত্বকালে মঠ পরিচালিত বিদ্যালয়গুলি ছিল শিক্ষাদানের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। প্রতিটি মঠেই থাকত সুবিশাল পাঠাগার। সেখানে সংরক্ষিত হত বিভিন্ন পুথি, পাণ্ডুলিপি। পরবর্তীকালে (দ্বাদশ শতকে) এসব দলিল পণ্ডিতদের জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে প্রভূত সাহায্য করেছিল। এখান থেকেই পাওয়া গেছে একটি নতুন লিপি, যা 'ক্যারোলিঞ্জিয়ান মিনাসকিউল' নামে খ্যাত।
② শার্লেম্যানের রাজসভা অলংকৃত হত প্রচুর জ্ঞানীগুণী দ্বারা। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন-আলকুইন, পিটার (Piter of Pisa), থিয়োডল্ফ, পল দ্য ডেকন প্রমুখ।
③ তাঁর আমলে ইতিহাসচর্চা, ব্যাকরণচর্চা, সাহিত্যচর্চা ও শিল্পচর্চার ব্যাপক স্ফুরণ ঘটে। এ যুগের বিখ্যাত কবি ছিলেন থিয়োডল্ফ ও ওয়ালফ্রেড স্ট্যাবো। জন দ্য স্কট ছিলেন সে-সময়ের খ্যাতনামা মৌলিক দার্শনিক তথা চিন্তাবিদ। এই সময় Ecclesiastical লাতিন ভাষাচর্চা শুরু হয়, যা ছিল লাতিন চার্চের উপাসনামূলক বা ধর্মীয় ভাষা।
(4)শিল্পকলা ও স্থাপত্যশিল্পের ক্ষেত্রেও ক্যারোলিঞ্জিয়ান যুগ পিছিয়ে ছিল না। শিল্পীরা মুসলিম ও বাইজানটাইন ঐতিহ্য দ্বারা প্রভাবিত হয়। আইলা-শ্যাপেলের প্রাসাদ ও ক্যাথেড্রাল ছিল সে-যুগের শিল্পকলার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।
7. কনস্ট্যান্টিনোপলের পতনের সঙ্গে ইউরোপীয় রেনেসাঁ বা নবজাগরণের সম্পর্ক কী ছিল?
উত্তর:-
▶ রেনেসাঁ বা নবজাগরণ আকস্মিকভাবে ঘটেনি। বহু বছর ধরে ধাপে ধাপে এর উত্তরণ ঘটে। তথাপি 1453 খ্রিস্টাব্দকে ইউরোপীয় নবজাগরণের সূচনাবর্ষ ও ইউরোপের আধুনিক যুগের সূচনাকাল ধরা হয়। 1453 খ্রিস্টাব্দে তুর্কিদের হাতে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য বা বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের পতন হলে সেখানকার জ্ঞানীগুণী মানুষরা পুথিপত্র নিয়ে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যে চলে আসেন। তাঁরা ইটালির রোম, ভেনিস, পিসা, জেনোয়া, ফ্লোরেন্স প্রভৃতি শহরে গ্রিক ও লাতিন সংস্কৃতির চর্চা শুরু করেন। এভাবে এই শহরগুলি এক- একটি শিক্ষার পীঠস্থানে পরিণত হয়। সে-সময় ইটালির ফ্লোরেন্স ছিল সংস্কৃতিচর্চার অন্যতম পীঠস্থান। সে-কারণে এই শহরকে বলা হত 'দ্বিতীয় এথেন্স' ও 'সাংস্কৃতিক রাজধানী'। ফলে সেখানে যুক্তিনির্ভর গ্রিক ঐতিহ্য আবার ফিরে আসে। তার ফলে মানুষ যুক্তির কষ্টিপাথরে সবকিছু যাচাই করে নিতে শেখে। যা যুক্তিগ্রাহ্য নয়, তা মানুষ প্রত্যাখ্যান করে। তখন থেকে মানুষ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ঝড়-বন্যা-ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনাবলির রহস্য উদ্ঘাটন করতে থাকে। সুশীল সমাজ ও আনন্দময় জীবনের স্বার্থে তারা নতুন করে সাহিত্য, শিল্প, ললিতকলা প্রভৃতি সৃজনশীল কাজে মেতে ওঠে।
এইভাবে ইটালিকে কেন্দ্র করে ইউরোপে নবজাগরণের সূচনা হয় এবং কালক্রমে তা ইউরোপের অন্যান্য দেশে বিস্তার লাভ করে।
৪. রেনেসাঁ সম্পর্কিত মানবতাবাদ বলতে কী বোঝো?
উত্তর:-
▶ ইউরোপীয় নবজাগরণের একটি ইতিবাচক দিক ছিল মানবতাবাদ। এই মানবতাবাদ হল সমকালীন ইউরোপের জীবনমুখী দর্শনের একটি অঙ্গ। যেখানে ধর্ম ও ধর্মীয় বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করে ইউরোপের একদল মনীষী মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখ, হাসিকান্না প্রভৃতি বিষয়কে মূলধন করে তাঁদের সৃষ্টিকর্মে মেতে উঠেছিলেন। মানবকল্যাণের এই ব্রতকেই বলা হয় মানবতাবাদ। এর ব্যাপ্তি ঘটেছিল সাহিত্য, শিল্প, ললিতকলার মতো সৃজনশীল বিষয়ে।
উল্লেখ্য যে, 'হিউম্যানিজম' বা 'মানবতাবাদ' দ্বারা পার্থিব জগতের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করা হয় মানুষকে। মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও গুণাবলি বিকাশের ওপর জোর দেওয়া হয়। মানুষকে দেওয়া হয় তার প্রাপ্য মর্যাদা। মানুষই হল সমস্ত শক্তির উৎস; ঈশ্বর নন। ঈশ্বর মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন না। উপরন্তু এই মতবাদে মানুষে মানুষে ঐক্য গড়ে তোলার কথা বলা হয়।
9. রেনেসাঁর পিছনে ফ্লোরেন্সের মেদেচি পরিবারের অবদান কী ছিল?
উত্তর:-
▶ ইটালির ফ্লোরেন্স নগর ছিল রেনেসাঁস আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র। এখানে মেদিচি পরিবারের নেতৃত্বে এক বিশিষ্ট জীবনধারা গড়ে উঠেছিল। কাল্পনিক স্বর্গসুখলাভের পরিবর্তে বর্তমান জীবনকেই সুখে-আনন্দে গড়ে তুলতে তাঁরা ব্যগ্র হয়ে ওঠেন। মেদিচি পরিবারের কসিমো এবং লরেঞ্জো দ্য মেদিচির পৃষ্ঠপোষকতায় জ্ঞান ও শিল্প সাহিত্যচর্চায় ফ্লোরেন্স নগর অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। স্বাভাবিকভাবেই ফ্লোরেন্স শহরে নবজাগরণের প্রথম প্রকাশ দেখা যায়। ফ্লোরেন্স বাদে ইটালিতে আরও কয়েকটি সমৃদ্ধ শহর ছিল। সেখানকার বিত্তবান বণিকরা সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জনের আশায় শিল্প-সাহিত্য প্রসারে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মেতে উঠতেন। ফলে, নতুন সংস্কৃতির ধারা ফ্লোরেন্স থেকে মিলান, রোম, ভেনিস, জেনোয়া প্রভৃতি শহরে প্রবাহিত হয়। এই স্রোত কিন্তু ইটালিতেই আবদ্ধ থাকল না। আল্পস পর্বত অতিক্রম করে নবজাগরণ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল জার্মানি, ফ্ল্যান্ডার্স, নেদারল্যান্ডস, পোর্তুগাল, স্পেন, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশগুলিতে।
10. রেনেসাঁ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী লিয়োনার্দো-দ্য- ভিঞ্চিকে কেন 'Universal man' বলা হয়?
উত্তর:-
▶ ইটালির ফ্লোরেন্সনিবাসী লিয়োনার্দো-দ্য-ভিক্তি ছিলেন একাধারে চিত্রকর, ভাস্কর, স্থপতি, কবি, সংগীতজ্ঞ, গণিতজ্ঞ, বিজ্ঞানী ও দার্শনিক। তিনি বর্তমানকালেও পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা বলে পরিগণিত হন। 1452 খ্রিস্টাব্দে ফ্লোরেন্সের নিকটবর্তী ভিঞ্চি গ্রামে তাঁর জন্ম হয়।
তাঁর অঙ্কিত চিত্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মগুলির মধ্যে বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছে।
① তাঁর চিত্রগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল দ্য লাস্ট সাপার ও মোনালিসা। তাঁর ছবিগুলিতে অপূর্ব মায়াবী আলোছায়া ও রঙের সমাবেশ ঘটেছে।
② 31 বছর বয়সে তিনি ভার্জিন অব দ্য রকস এঁকেছিলেন। এই চিত্রটি এখনও লন্ডনের আর্ট গ্যালারিতে শোভা পাচ্ছে। চিত্রটির আর-একটি সংস্করণ প্যারিসের লুভ্যর জাদুঘরে রয়েছে।
③ ভূতত্ত্ব, জীববিদ্যা, গণিত, স্থাপত্য, সংগীত ও দর্শনশাস্ত্রেও তাঁর ব্যুৎপত্তি ঘটেছিল।
④ আবার যন্ত্রশিল্পী হিসেবেও তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল।
⑤ পাখির ওড়াকে বিষয় করে তিনি উড়োজাহাজের নকশা এঁকে গিয়েছেন।
⑥ স্কুর প্যাঁচ-কাটার যন্ত্র, মেশিনগান, সাবমেরিন, প্যারাসুট, ট্যাংকের নকশাও তিনি অঙ্কন করেছিলেন।
এই কারণেই তাঁকে Universal Man বলে অভিহিত করা হয়।
10. মার্টিন লুথারের প্রতিবাদী আন্দোলনের ফল কী হয়েছিল?
উত্তর:-
▶ জার্মানি নিবাসী মার্টিন লুথার ছিলেন ষোড়শ শতকের একজন প্রতিবাদী ধর্মসংস্কারক। তিনি ক্যাথোলিক চার্চের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। এর ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। যেমন-
① লুথারের প্রতিবাদী আন্দোলনের ফলে খ্রিস্টান ধর্ম ও সমাজ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যথা-রোমান ক্যাথোলিক ধর্ম ও প্রোটেস্টান্ট ধর্ম।
② লুথারের প্রতিবাদী আন্দোলনের প্রভাবে 1520-এর দশকে ইউরোপে অ্যানা ব্যাপটিস্ট আন্দোলনের সূচনা হয়। এই আন্দোলন ছিল মূলত পোপ ও ক্যাথোলিক চার্চ বিরোধী।
③ লুথারের প্রতিবাদী আন্দোলন শুধু জার্মানিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তা প্রসারিত হয়েছিল ইংল্যান্ড, ফ্রান্স-সহ ইউরোপের অন্যান্য দেশে।
11. কত খ্রিস্টাব্দে ধর্মসংক্রান্ত অগসবার্গের সন্ধি হয়? এই সন্ধির গুরুত্ব আলোচনা করো।
উত্তর:-
1555 খ্রিস্টাব্দে সুইডেনের অগসবার্গে পবিত্র রোমান সম্রাট পঞ্চম চার্লস ও প্রোটেস্টান্টদের মধ্যে অগসবার্গের সন্ধি হয়।
* সন্ধির গুরুত্ব: এই সন্ধির ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী, যেমন-
① প্রোটেস্টান্ট চার্চ আইনত বৈধতা লাভ করে।
② রাজার ধর্মই প্রজার ধর্ম-এটি স্বীকৃত হয়।
③ বলা হয়, প্রোটেস্টান্ট চার্চের বিশপ ও অ্যাবট এবং প্রোটেস্টান্ট প্রজাদের ওপর কোনো অত্যাচার করা হবে না। যেসব প্রজা রাজার ধর্মকে নিজের ধর্ম বলে মেনে নেবে না তাদের দেশত্যাগ করার সুযোগ দিতে হবে।
④ যে-কোনো ধর্মীয় বিরোধ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মেটাতে হবে। এইভাবে জার্মানিতে প্রোটেস্টান্ট ধর্ম তার জায়গা করে নেয়।
12. প্রতিসংস্কার আন্দোলন বলতে কী বোঝো ? এর উদ্দেশ্য কী ছিল?
উত্তর:-
▶ প্রোটেস্টান্ট মতবাদকে দমন করে ক্যাথোলিক ধর্মমতকে আ বাঁচিয়ে রাখার জন্য চার্চের অভ্যন্তরে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। ফলে ইটালি, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স ও স্পেনে ক্যাথোলিক চার্চের সংস্কারসাধনের জন্য জোরালো দাবি ওঠে। একে বলা হয় Counter Reformation বা প্রতিসংস্কার আন্দোলন, যা প্রথম শুরু হয় স্পেনে।
এই প্রতিসংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে-ক্যাথোলিক চার্চগুলির অভ্যন্তরীণ সংস্কারের কাজ শুরু হয়, যেমন-
① যাজকরা যাতে চরিত্রবান হয় এবং নৈতিকতার পথে পরিচালিত হয় সেদিকে নজর দেওয়া হয়।
② প্রচারকে হাতিয়ার করে ও বলপূর্বক প্রোটেস্টান্টদের ক্যাথোলিক মতবাদে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এককথায় এই আন্দোলন ছিল ক্যাথোলিক ধর্মের শুদ্ধিকরণের আন্দোলন। যার দ্বারা চার্চগুলিকে দুর্নীতিমুক্ত করা যায় এবং সেই সঙ্গে চার্চ ও ক্যাথোলিক ধর্মের প্রতি সাধারণ মানুষের বিশ্বাস অর্জন করা যায়।
13. 'গোল্ডেন কাউন্সেল' কী?
অথবা,
প্রতিসংস্কার আন্দোলনের প্রেক্ষিতে চার্চের যে সংস্কার- সাধন করা হয়েছিল তা উল্লেখ করো।
অথবা,
চার্চের সংস্কার সাধন প্রশ্নে পোপদের কী ভূমিকা ছিল?
উত্তর:-
▶ ষোড়শ শতকের শেষদিকে ইউরোপে প্রতিসংস্কার আন্দোলনের সূচনা হয়। এই সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে চার্চের জন্য বেশ কিছু সংস্কার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল।
* পোপদের অবদান/গোল্ডেন কাউন্সেল:
এই উদ্যোগের দিশারিরা ছিলেন রোমের পোপগণ। পোপ ষষ্ঠ অ্যাড্রিয়ান সর্বপ্রথম কান্ডারির ভূমিকা পালন করেন। তিনিই প্রথম চার্চের সংস্কারসাধনের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। তারপর পোপ দশম লিয়ো এ প্রসঙ্গে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তী পোপ তৃতীয় পল যাজকদের উন্নত নৈতিক জীবনাদর্শ তথা তাঁদের শুদ্ধ জীবনযাপনের পক্ষে সওয়াল করেন। এজন্য তিনি চার্চের সংস্কারের জন্য কয়েকটি প্রস্তাব দেন, যা 'গোল্ডেন কাউন্সিল' নামে খ্যাত। তাতে বলা হয়
① ধর্মযাজক, সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীগণ শুদ্ধাচার ও নৈতিক জীবনযাপন করবেন।
② কেউই চার্চের একটির বেশি পদ অলংকৃত করতে পারবেন না।
③ তাঁরা তাঁদের পাপাচারের জন্য প্রভুর কাছে অনুশোচনা বা অনুতাপ করবেন এবং
④ মঠবাসী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীগণ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবেন না।
পরবর্তী পোপ চতুর্থ লিয়ো এই নিয়মাবলি কঠোরভাবে প্রয়োগ করেন।
14. বাসবন্না কে ছিলেন? তাঁর মতবাদগুলি উল্লেখ করো।
উত্তর:-
▶ বাসবন্না ছিলেন দ্বাদশ শতকের দক্ষিণ ভারতীয় এক শৈব সাধক।
* বাসবন্নার মতবাদ:
① বাসবন্না শিবের প্রেমময় ভক্তির ওপর জোর দিয়েছিলেন।
② তিনি তাঁর অনুগামীদের গলায় ইষ্টলিঙ্গ (ছোট্ট শিবলিঙ্গ) ধারণের নির্দেশ দেন।
③ তিনি মূর্তিপূজা, সামাজিক বৈষম্য, কুসংস্কার, লিঙ্গ- বৈষম্য, কঠোর ধর্মীয় আচার-বিচার প্রভৃতির ঘোর বিরোধী ছিলেন।
④ তিনি প্রচার করেন মন্দির প্রতিষ্ঠার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ একজন ভক্তের শরীর ও আত্মাই হল তার মন্দির। এসব কারণে এইচ কে শাস্ত্রী তাঁকে 'দক্ষিণ ভারতের মার্টিন লুথার' বলে অভিহিত করেছেন। তারপর এই আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র চান্না বাসবন্না।
15. বীর শৈব ঐতিহ্য সম্পর্কে কী জানো?
উত্তর:-
দক্ষিণ ভারতে বীর শৈব বা লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বাসবন্না।
★ বীর শৈব ঐতিহ্য:
① লিঙ্গায়তরা বিশ্বাস করতেন যে মৃত্যুর পর ভক্তবৃন্দ ভগবান শিবের সঙ্গে একাত্ম হবে এবং এই পৃথিবীতে আর ফিরে আসবে না। অর্থাৎ, তারা পুনর্জন্মে বিশ্বাসী ছিলেন না।
② এই সম্প্রদায়ের ভক্তরা শবদেহকে কখনোই দাহ করতেন না, পরিবর্তে তাঁদের মৃত পরিজনের দেহ আনুষ্ঠানিকভাবে সমাধিস্থ করতেন।
③ লিঙ্গায়তরা বর্ণ- ব্যবস্থার বিরোধী ছিলেন এবং তারা কিছু নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে অস্পৃশ্য বা দূষিত হিসেবে গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। সমাজে যেসব সম্প্রদায়ের স্থান গৌণ ছিল, তারা লিঙ্গায়তদের অনুগামী হতে শুরু করেন।
④ ধর্মশাস্ত্রে যেসব সামাজিক প্রথা অস্বীকৃত ছিল, যেমন-প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর বিবাহ, বিধবাদের পুনর্বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক রীতিনীতিগুলি লিঙ্গায়তরা স্বীকৃতি দিয়েছিল।
16. নাথ শৈব সম্প্রদায় সম্পর্কে কী জানো?
উত্তর:-
▶ খ্রিস্টীয় একাদশ শতকে উত্তর ভারতে নাথ শৈবসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মতসেন্দ্রনাথের শিষ্য 'কানফাটা' যোগী ওরফে গোরক্ষনাথ। অনেকের মতে দত্তাত্রেয় ছিলেন নাথ সম্প্রদায়ের আদিগুরু, যিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছিলেন। তাঁকে বলা হয় যোগের দেবতা (God of yoga) ।
★ আচার:
নাথ সম্প্রদায় শিবকে তাদের আদি দেবতা বা প্রথম প্রভু বলে মনে করে। তারা বর্ণপ্রথার ঘোরবিরোধী। শিব সাধনায় তারা হঠযোগ অনুসরণ করে। এই যোগের অঙ্গ হল নানা ধরনের ক্রিয়া, মুদ্রা, আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতি শুদ্ধিকরণের কৌশল। তারা নামমাত্র একটি কোটি বসন পরিধান করে। সারা শরীরে ছাইভস্ম মেখে থাকে। গাঁজা সেবন করে।
17. ভারতে সুফিবাদ প্রসারের তিনটি কারণ উল্লেখ করো।
উত্তর:-
▶ মধ্যযুগীয় ভারতে সুফি মতবাদ তথা সুফি আন্দোলনের প্রসার ও বিকাশ এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। এই প্রসার বা সাফল্যের পিছনে ছিল নানাবিধ কারণ, যেমন-
① সরকারি অনুগ্রহ:
সুফিসন্তরা সমকালীন সুলতান ও মোগল শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। দিল্লির শাসকরা ইসলামের আদর্শ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করলেও সুফিসন্তদের মতবাদ ও আদর্শের বিরোধিতা করেননি। উপরন্তু তাঁরা সুফি দরগাগুলির উন্নতিকল্পে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন।
② ধর্মীয় উদারতা:
সুফিসন্তরা ছিলেন ধর্ম বিষয়ে উদার। তাঁরা হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মের বিরোধিতা করেননি, ফলে বহু হিন্দু সুফিবাদের অনুরাগী হয়। সুফিসন্তরা কাউকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিতকরণ করেননি বা বে-শরিয়াপন্থীদের বা-শরিয়া মতবাদ অনুসরণ করতে বলেননি। বরং তাঁরা সৌভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলার ওপর জোর দিয়েছিলেন।
③ বর্ণভেদের বিরোধিতা:
তাঁরা জাতপাত ও বর্ণভেদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। যে কারণে অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া নিম্নবর্ণের অনেক হিন্দু এই ভাবধারায় শামিল হয়।
18. দরগাহ কী?
অথবা,
দরগাহগুলির কার্যকলাপ আলোচনা করো।
উত্তর:-
দরগাহ বা দরগা হল একজন সুফিসন্ত, পির ও দরবেশের সমাধিস্থল বা মাজার।
(1) প্রত্যেক সুফি ঘরানায় এক বা একাধিক দরগাহ ছিল। এগুলি ছিল পির বা মুরশিদ বা শেখদের (শিক্ষাগুরু) কর্মক্ষেত্র। তাঁদের শিষ্যদের বলা হত মুরিদ।
(2) দরগাগুলিতে পির ও তাঁর মুরিদ বা শিষ্য তথা অনুগামীরা একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় আচার-আচরণ পালন করতেন। এখানে গুরু তাঁর উপদেশ দিতেন এবং কোরান পাঠ করতেন। শিষ্যদের নিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করতে হত এবং মস্তক মুণ্ডন করে তাপ্পি লাগানো বস্ত্র পরিধান করতে হত।
(3) দরগাগুলি এক-একটি উপাসনাস্থল ও শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হত। পির তথা শেখের মৃত্যুর পর তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে দরগায় উদ্যাপিত অনুষ্ঠানরীতিকে 'উরস' বলা হত।
(4) দরগাগুলিতে থাকে নানা ধরনের সুযোগসুবিধা, যেমন-লঙ্গরখানা, খানকাহ বা ধর্মশালা, মসজিদ, সভাঘর প্রভৃতি।
19. আইন বিষয়ে কনফুসীয় মতবাদ কী ছিল?
উত্তর:-
▶ কনফুসিয়াস ছিলেন প্রাচীন চিনের এক দার্শনিক। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি তাঁর সুচিন্তিত মতবাদগুলি প্রচার করেছিলেন।
কনফুসিয়াস আইন সম্পর্কে বলেছেন যে-
① রাষ্ট্র পরিচালনার সময় রাজা ইচ্ছামতো আইন রচনা করতে পারেন না। তাঁকে রাষ্ট্র এবং জনগণের প্রয়োজনে ও কল্যাণে আইন প্রণয়ন করতে হবে। সেখানে জনগণ- সহ রাষ্ট্রের জ্ঞানী-গুণী মানুষদের মতামত থাকা উচিত। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন যে, রাষ্ট্রের সাধারণ আইনের পাশাপাশি আঞ্চলিক আইনেরও প্রয়োজন আছে।
② প্রশাসন সম্পর্কে তিনি বলেছেন, রাষ্ট্র পরিচালিত হবে একজন কর্মঠ, দক্ষ ও শক্তিশালী শাসক দ্বারা। উভয় ক্ষেত্রেই তিনি নৈতিকতার ওপর জোর দিয়েছিলেন।
③ তবে আইন ও শাসন বিষয়ে প্রশাসনকে সতর্ক করেছেন এই বলে যে, আইনের শাসন দ্বারা মানুষকে কখনোই শৃঙ্খলাপরায়ণ করে তোলা যাবে না। তাঁর মতে, মানুষের আত্মার যখন উন্নতি ঘটবে তখনই মানুষ ভালোমন্দ বুঝতে শিখবে, তাতে মানুষের আইন ভাঙার মনোভাব তথা অপরাধমূলক কাজ করার প্রবণতা দূর হবে।
20. শিন্টো ধর্মের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো।
উত্তর:-
▶ শিন্টো ধর্ম হল জাপানের একটি বহুল প্রচলিত ধর্ম। শিন্টো ধর্মের বৈশিষ্ট্যগুলি হল-
① এই ধর্মে কোনো কঠোর নিয়ম ও পালনীয় আচার-আচরণ নেই।
② অনেকের মত যে, শিন্টো ধর্ম আসলে একটি সরল জীবন পদ্ধতি, যাতে শেখানো হয় নৈতিকতা ও মূল্যবোধের শিক্ষা। এই ধর্ম শেখায় কীভাবে মানুষ 'মাকোতা-নো-কো-কোরা' অর্থাৎ, কলুষতা ও অরাজকতা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন ও সুন্দর জীবনের অধিকারী হয়ে উঠতে পারে।
(3) এই ধর্ম একটি কামি (দেবতা) কেন্দ্রিক ধর্ম। শিন্টো ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস যে, ইজানাগি (স্বর্গ) ও ইজানামি (পৃথিবী) থেকেই কামি বা দেবতাদের জন্ম। এই কামিদের মধ্যে কিছু কামিকে তারা অশুভ শক্তির প্রতীক হিসেবে দেখে। ফলে এদের বিশুদ্ধ করার জন্য তারা বেশ কিছু আচার পালন করে।
| একাদশ শ্রেণীর ইতিহাস এর দ্বিতীয় সেমিস্টারের সকল অধ্যায় ও প্রশ্নোত্তর |
|---|
| অধ্যায় ৪ - রাষ্ট্রের প্রকৃতি, রাষ্ট্রচিন্তা ও প্রতিষ্ঠান (Nature of the State and Its Apparatus) |
| অধ্যায় ৫ - পরিবর্তনশীল ঐতিহ্য (Changing Traditions) |
| অধ্যায় ৬ - বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিস্তৃত দিগন্ত (Expanding Horizons of Science and Technology) |
| একাদশ শ্রেণীর ইতিহাস এর দ্বিতীয় সেমিস্টারের সিলেবাস |
| Mock Test |
| Coming Soon |
| Coming Soon |