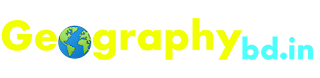একাদশ শ্রেণী ইতিহাস দ্বিতীয় সেমিস্টার, চতুর্থ অধ্যায় রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও রাষ্ট্রযন্ত্র / রাষ্ট্রের প্রকৃতি, রাষ্ট্রচিন্তা ও প্রতিষ্ঠান প্রশ্ন উত্তর | Class 11, 1st semester History, Fourth Chapter । WBCHSE । Rastrer Prokriti o Rastro jontro
শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা আলোচনা করবো একাদশ শ্রেণীর ইতিহাস বিষয়ের চতুর্থ অধ্যায় রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও রাষ্ট্রযন্ত্র / রাষ্ট্রের প্রকৃতি, রাষ্ট্রচিন্তা ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে। আশাকরি তোমরা একাদশ শ্রেণীর দ্বিতীয় সেমিস্টারের এই রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও রাষ্ট্রযন্ত্র / রাষ্ট্রের প্রকৃতি, রাষ্ট্রচিন্তা ও প্রতিষ্ঠান অধ্যায়টি থেকে যেসব প্রশ্ন দেওয়া আছে তা কমন পেয়ে যাবে। আমরা এখানে একাদশ শ্রেণীর, দ্বিতীয় সেমিস্টারের ইতিহাস বিষয়ের চতুর্থ অধ্যায় রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও রাষ্ট্রযন্ত্র / রাষ্ট্রের প্রকৃতি, রাষ্ট্রচিন্তা ও প্রতিষ্ঠান এর SAQ, শূন্যস্থান পূরণ, এক কথায় উত্তর দাও, Descriptive, ব্যাখ্যা মুলক প্রশ্নোত্তর , সংক্ষিপ্ত নোট এগুলি দিয়েছি। এর পরেও তোমাদের এই রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও রাষ্ট্রযন্ত্র / রাষ্ট্রের প্রকৃতি, রাষ্ট্রচিন্তা ও প্রতিষ্ঠান অধ্যায়টি থেকে কোন অসুবিধা থাকলে, তোমরা আমাদের টেলিগ্রাম, হোয়াটসাপ , ও ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারো ।
অধ্যায় ৪ - রাষ্ট্রের প্রকৃতি, রাষ্ট্রচিন্তা ও প্রতিষ্ঠান (Nature of the State and Its Apparatus) অধ্যায়ের সকল প্রশ্ন ও উত্তর
1. কৌটিল্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
অথবা,কৌটিল্য কে ছিলেন?
উত্তর:-
▶ কৌটিল্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়-
a) কৌটিল্য ছিলেন তক্ষশিলা নিবাসী একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধি কূটনীতিবিদ ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
b) তিনি ছিলেন খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের মানুষ।
c) তাঁকে চাণক্য বা বিন্নুগুপ্তের সঙ্গে অভিন্ন মনে করা হয়। বলা হয়ে থাকে চাণক্যের ছদ্মনাম ছিল কৌটিল্য।
d) তিনি ছিলেন মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রধানমন্ত্রী।
e) ইটালির বিখ্যাত রাষ্ট্রচিন্তাবিদ ম্যাকিয়াভেলির মতো কৌটিল্যও রাজা, ধর্ম ও রাজ্যের স্বার্থে নীতির পথ বর্জন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাই কেউ কেউ তাঁকে 'ভারত ইতিহাসের ম্যাকিয়াভেলি' বলে অভিহিত করে থাকেন। তবে এ নিয়ে বিতর্ক আছে।
f) তাঁর রচিত প্রধান গ্রন্থ হল অর্থশাস্ত্র, যার মূল বিষয়বস্তু হল 'রাষ্ট্রনীতি'। এ ছাড়াও গ্রন্থটি থেকে মৌর্যযুগের শাসনব্যবস্থা, সমাজ, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে বিস্তৃত ও নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায়। তবে সমগ্র অর্থশাস্ত্রের মূল লক্ষ্য রাজার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি পরিচালন বিষয়ে উপদেশ দান করা।
g) তিনি ছিলেন প্রাচীন ভারতের প্রথম বরেণ্য রাষ্ট্রচিন্তাবিদ।
2. অর্থশাস্ত্র বলতে কৌটিল্য কী বুঝিয়েছেন?
উত্তর:-
▶ কৌটিল্য তাঁর রাষ্ট্রবিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থের নামকরণ করেছেন অর্থশাস্ত্র। প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়েছে। যেমন-রাজধর্ম, রাজ্যশাস্ত্র, দণ্ডনীতি, নীতিশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ইত্যাদি। অর্থাৎ, অর্থশাস্ত্র রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আর এক নাম। আপাতদৃষ্টিতে অর্থশাস্ত্রের দ্বারা বোঝায় অর্থনীতিবিজ্ঞান। কিন্তু কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্র গ্রন্থের পঞ্চদশ অধিকরণে অর্থশাস্ত্র কথাটির ব্যাখ্যা করেছেন।
✅ কৌটিল্যের ব্যাখ্যা:
কৌটিল্য বলেছেন, মানুষের বৃত্তি বা জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায় হল অর্থ “মনুষ্যনাং বৃত্তিরর্থঃ)। মনুষ্যদের বসতি যে ভূমিতে বা পৃথিবীতে, তাকেও বলে অর্থ ('মনুষ্যবর্তী ভূমিরিত্যথঃ)। যে শাস্ত্র এই পৃথিবীকে লাভ করা বা প্রাপ্তি ও পালনের উপায় শেখায়, তা হল অর্থশাস্ত্র ("তস্যাঃ পৃথিব্যা লাভ পালনোপায়ঃ শাস্ত্রমর্থ শাস্ত্রমিতি”)। কৌটিল্যের মতে, অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তু হল, মানুষ বসবাস করে যে ভূমি বা ভূখণ্ডে, তার লাভ বা প্রাপ্তি ও পালনের উপায়।
✅ মন্তব্য:
কৌটিল্যীয় যুগের প্রধান অর্থনীতি ছিল ভূমির ওপর নির্ভরশীল কৃষি। যে রাজার যতবেশি ভূমি থাকবে, তিনি ততবেশি শক্তিশালী হবেন। সে-কারণে ভূমিভিত্তিক রাজ্যজয়, রাজ্যপ্রশাসন ও রাজ্যরক্ষা বিষয়ক শাস্ত্রকে অর্থশাস্ত্র হিসেবে আখ্যা দেওয়া যথার্থ হয়েছে।
3. কৌটিল্য কীজন্য বিখ্যাত?
উত্তর:-
▶ কৌটিল্য ছিলেন খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের ভারতের তক্ষশিলার অধিবাসী একজন কূটনীতিবিদ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ। তাঁর আসল নাম চাণক্য বা বিছুগুপ্ত। কৌটিল্য প্রধানত দুটি কারণে ভারত ইতিহাসে সর্বাধিক বিখ্যাত-
a) মৌর্ঘসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এবং
b) অর্থশাস্ত্র-এর রচয়িতা হিসেবে।
এ ছাড়াও আমরা কৌটিল্য কে আরো কিছু রূপে দেখে থাকি যেমন :-
i) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের অভিভাবক, উপদেষ্টা ও প্রধানমন্ত্রী- কৌটিল্য:
একদা কৌটিল্য মগধের নন্দবংশের রাজা ধননন্দের দ্বারা অপমানিত হয়ে নন্দবংশের উচ্ছেদের প্রতিজ্ঞা করেন। তিনি তাঁর প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করার জন্য দিন গুণছিলেন। এ সময় তিনি পাটলিপুত্রের রাখাল বালকদের মধ্যে বালক চন্দ্রগুপ্তের চরিত্রে রাজোচিত লক্ষণ দেখে ত্যাকে তক্ষশিলায় নিয়ে যান। এরপর কৌটিল্য বালক চন্দ্রগুপ্তকে শাস্ত্র ও শস্ত্রে শিক্ষিত করেন। পরবর্তী কালে তিনি দুঃসাহসী যুবক চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সাহাযে। নন্দবংশের উচ্ছেদ ঘটিয়ে মগধে মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠা (324 খ্রিস্টপূর্ব) করতে সাহায্য করেন। কৌটিল্যই যুবক চন্দ্রগুপ্তের অভিভাবক ও উপদেষ্টা ছিলেন। সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ছিলেন ব্রাহ্মণ কৌটিল্যের স্নেহধন্য। তাই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সিংহাসনে বসে কৌটিল্যকে তাঁর প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন।
ii) অর্থশাস্ত্র-এর রচয়িতা কৌটিল্য:
কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র হল সংস্কৃত ভাষায় লেখা ভারতের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনীতি-বিষয়ক গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে আদর্শ রাষ্ট্রনীতি, মৌর্যযুগের প্রশাসন- ব্যবস্থা, সমাজ, অর্থনীতি বিষয়ে বিস্তৃত ও নির্ভরযোগ্য বিবরণ রয়েছে। ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে কৌটিল্যের অবদান। অপরিসীম। অর্থশাস্ত্রে সর্বপ্রথম ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তার একটি সংহত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপ দেখতে পাওয়া যায়।
4. অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তু কী?
উত্তর:-
▶কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে রাষ্ট্রনীতি ও প্রশাসনযন্ত্রের আদর্শ বা মডেল উপস্থাপিত করেছেন। কৌটিল্য রাজতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের আলোচনা করেছেন। অর্থশাস্ত্রে দুটি বিষয়ের ওপর 'গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে-
i) তন্ত্র ও ii) আবাপ।
i) 'তন্ত্র' অংশে আলোচিত বিষয়সমূহ:
'তন্ত্র' হল রাজার কর্তব্য বিষয়ক, প্রজাকল্যাণ, অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা স্থাপন ইত্যাদি। এই অংশে আলোচিত হয়েছে রাজার শিক্ষা ও বিনয়, মন্ত্রীদের গুণাগুণ, বিভিন্ন প্রকার গুপ্তচর, রাজার দৈনন্দিন কর্তব্য, বিভিন্ন প্রশাসন বিভাগের অধ্যক্ষ সমুদয়, বিচারব্যবস্থা, রাজ্য পরিচালনার পদ্ধতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়।
ii) 'আবাপ' অংশের আলোচ্য বিষয়:
'আবাপ' হল প্রতিবেশী রাষ্ট্রের গতিবিধির ওপর লক্ষ রাখা এবং যুদ্ধ ঘোষণা করা।
এই অংশে আলোচিত হয়েছে আন্তঃরাজ্য সম্পর্ক, কূটনীতি বিষয়ক ছ-টি কৌশল, যুদ্ধজয় ও বিজিত দেশে জনপ্রিয়তা। অর্জন পদ্ধতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়। কৌটিল্যের দৃষ্টিতে প্রত্যেক স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্রের রাজা তার প্রতিবেশী রাজ্য জয়ে ইচ্ছুক হন। তাই তিনি বিজিগীষু (বিজয়লাভে ইচ্ছুক) রাজা। বিজিগীষু রাজার কর্তব্যও এই অংশে আলোচিত হয়েছে।
5. রাজার ক্ষমতা সম্পর্কে অর্থশাস্ত্রে কী বলা হয়েছে?
▶ কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে রাষ্ট্রনীতি বর্ণনা করেছেন। অর্থশাস্ত্রে রাজার ক্ষমতা ও গুণাবলির উল্লেখ করা হয়েছে।
i) চূড়ান্ত ক্ষমতা:
অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হলেন রাজা। 'তিনি রাষ্ট্রের প্রধান অলঙ্গ এবং রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা। এককথায় তিনি পার্থিব জগতে চূড়ান্ত সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী। তাঁর কর্তৃত্বকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা কারও নেই। রাজাকে কেন্দ্র করেই শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠবে। তিনিই হবেন প্রধান আইনপ্রণেতা, প্রধান বিচারক ও প্রধান সেনাপতি। অর্থাৎ, সামরিক, বেসামরিক ও বিচারব্যনএস্থা সর্বত্রই রাজার একাধিপত্য। কৌটিল্য বলেছেন, "রাজাই হলেন রাজ্য, সব প্রকৃতি বা অঙ্গের সংক্ষিপ্ত রূপ” (অর্থশাস্ত্র, অষ্টম অধিকরণ)। তাঁর দৃষ্টিতে রাজা ও ররাষ্ট্র সমার্থক, তাই রাজাকে সর্বগুণসম্পন্ন ও শক্তিশালী হতে হবে।
ii) ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ:
অর্থশাস্ত্রে রাজার ক্ষমতার ওপর কিছু নিয়ন্ত্রণ আরোপের কথা বলা হয়েছে। রাজা সর্বশক্তিমান হলেও রাষ্ট্রপরিচালনায় মন্ত্রীপরিষদ, অমাত্য প্রমুখদের সাহায্য তার প্রয়োজন হয়। অবশ্য রাজা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেও ওই পরামর্শ গ্রহণ করা বা না-করা রাজার ইচ্ছাধীন ছিল। তবে কৌটিল্য কখনোই রাজতন্ত্রকে একনায়কতন্ত্রে পরিণত করেননি। তাঁর দৃষ্টিতে রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হবে 'সচিবায়ত্ত-রাজ্য'।
6. রাজার গুণাবলি সম্পর্কে অর্থশাস্ত্রে কী বলা হয়েছে?
উত্তর:-
▶ কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে রাজার বিভিন্ন গুণাবলির ওপর বিশেষ আলোকপাত করেছেন। কৌটিল্যের মতে, রাজার চারটি আবশ্যিক গুণাবলি থাকা দরকার। এগুলি হল
i) উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে রাজা সর্বদা সব কাজে 'আত্মনিয়োগ করবেন। রাজার এই গুণকে বলা হয় উত্থান গুণ।
ii)রাজা হবেন ধর্মপরায়ণ। তিনি হবেন নম্র ও বিচক্ষণ। শত্রু দমনেও তিনি হবেন দক্ষ। রাজার এই গুণাবলিগুলিকে একত্রে অভিগামিক গুণ বলা হয়।
iii) রাজা হবেন তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন, বাকপটু, বিপদকালে সংযমী ও স্থির- মতিসম্পন্ন। রাজার এই গুণগুলিকে বলা হয় ব্যক্তিগত গুণ।
iv) এ ছাড়া রাজা হবেন প্রখর স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম ও যে-কোনো সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ। রাজার এই গুণাবলিকে বলা হয় প্রজ্ঞা গুণ।
এ ছাড়াও রাজাকে ইন্দ্রিয় সংযমী ও সত্যবাদী হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।।
7. কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাজার কর্তব্য সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?
উত্তর:-
▶ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাজার কর্তব্য আলোচিত হয়েছে। সেগুলি হল-
i) কৌটিল্য রাজাকে কঠোর পরিশ্রম করার উপদেশ দিয়েছেন।
ii) কৌটিল্য বলেছেন রাজার চূড়ান্ত সার্বভৌম ক্ষমতা থাকলেও তিনি কখনোই স্বেচ্ছাচারী হবেন না। কৌটিল্য ছিলেন অবাধ রাজতন্ত্র ও স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে।
iii) রাজার অন্যতম কর্তব্য হল রাজ্যকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা।
iv) রাজা রাষ্ট্রে সুশাসন প্রবর্তন করবেন, অরাজকতা দূর করবেন, জনগণের নিরাপত্তা বিধান করবেন এবং ধনী-দরিদ্র সকলকে শোষণের হাত থেকে রক্ষা করবেন। কৌটিল্য প্রজাবর্গের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা আর সামরিক শৃঙ্খলা ও সংহতিকে রাজ্যের প্রধান উদ্দেশ্য বলে অভিহিত করেছেন।
v) রাজা প্রজাদরদি হবেন। কৌটিল্য বলেছেন- "প্রজাসুখে সুখং রাজ্ঞঃ প্রজানাং চ হিতে হিতম্। নাত্মপ্রিয়ং হিতং রাজ্ঞঃ প্রজানাং তু প্রিয়ং হিতম্।।”
অর্থাৎ, প্রজার সুখেই রাজা সুখী, প্রজার মঙ্গলেই রাজার মঙ্গল। রাষ্ট্রচিন্তাবিদ কৌটিল্য সেই রাজাকে আদর্শ রাজা মনে করতেন, যাঁর জীবন প্রজার সেবায় ও কল্যাণের জন্য উৎসর্গিত।
৪. জিয়াউদ্দিন বরনি কে ছিলেন? তিনি কীজন্য বিখ্যাত?
উত্তর:-
▶ জিয়াউদ্দিন বরনি (1285-1358 খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন ভারতে সুলতানি যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক।
* বিখ্যাত হওয়ার কারণ-
i) তিনি সুলতান মোহম্মদ- বিন-তুঘলক ও ফিরোজ শাহ তুঘলকের শাসনকালে উচ্চ সরকারি পদে আসীন ছিলেন। তিনি নিজে সতেরো বছর মোহম্মদ-বিন-তুঘলকের সভাসদ ও 'নাদিম' ছিলেন। এটি ছিল একজন পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবীর পদ। সুলতান প্রায়ই তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতেন। সভাপণ্ডিত ও প্রাজ্ঞ মানুষ হিসেবে সুলতান তাঁর প্রশংসাও করতেন।
ii) ইতিহাসের বিষয়বস্তু ও ইতিহাস-দর্শন সম্পর্কে বরনির স্পষ্ট ধারণা ছিল। মধ্যযুগের তিনিই একমাত্র ঐতিহাসিক যিনি অর্থনৈতিক জীবনের ওপর প্রচুর তথ্য সরবরাহ করেছেন। তাঁর লেখা তারিখ-ই-ফিরোজশাহি থেকে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের রাজত্বের আরম্ভ থেকে সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলকের রাজত্বের গোড়ার দিকের ঘটনার কথা জানা যায়। তাঁর ফতোয়া-ই-জাহান্দারি গ্রন্থে সুলতানি যুগের শাসননীতি এবং নরপতিদের আদর্শ সম্পর্কে তাঁর ধারণার বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়। বরনির তারিখ-ই-ফিরোজশাহি সমকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক গ্রন্থ।
9. ফতোয়া-ই-জাহান্দারি গ্রন্থের গুরুত্ব কী?
উত্তর:-
▶ জিয়াউদ্দিন বরনি 1352 খ্রিস্টাব্দ থেকে 1357 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে লিখেছিলেন ফতোয়া-ই-জাহান্দারি। এই গ্রন্থটির গুরুত্ব হল-
i) ইসলামি রাষ্ট্র কেমন হওয়া উচিত এ গ্রন্থে তার বিবরণ আছে। তাঁর মতে, দেশে ইসলামীয় ঐতিহ্য। ও রীতিনীতি সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সুলতানের হাতে সর্বাত্মক ক্ষমতা থাকা উচিত।
ii) ভারতে সুলতানি যুগে রাষ্ট্রশাসনের জন্য তিনি এই গ্রন্থে 24টি উপদেশ দিয়েছেন। রাজতন্ত্রের সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত, সুলতানদের শাসননীতি কোন্ পথে পরিচালিত হওয়া উচিত, এসব বিষয় তিনি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে সুলতানকে নিরপেক্ষতা বজায় রেখে ন্যায়পরায়ণ হতে হবে। তিনি লিখেছেন যে, রাষ্ট্রশাসনে একমাত্র উচ্চ-বংশজাত মুসলমানদেরই নিয়োগ করতে হবে।
iii) বরনি সুলতানকে রাষ্ট্র শাসনের প্রয়োজনীয় বিধি 'জাওয়াবিত' প্রণয়ন করার পরামর্শ দিয়েছেন। রাষ্ট্রশাসন (সিয়াসৎ) এবং ধর্মীয় অনুশাসন (শরিয়ৎ)-এর মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হলে তিনি প্রথমটিকেই গুরুত্ব দিতে বলেছিলেন।
iv) এই গ্রন্থটি সুলতানি আমলের রাষ্ট্রনীতি ও রাষ্ট্রের চরিত্র অনুধাবন করতে বহুলাংশে সাহায্য করে।
10. ফতোয়া-ই-জাহান্দারি গ্রন্থে উল্লেখিত রাষ্ট্রনীতি প্রসঙ্গে জিয়াউদ্দিন বরনি রাষ্ট্রীয় আইন সম্পর্কে কী আলোচনা করেছেন?
উত্তর:-
▶ সুলতানি যুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বরনি তাঁর ফতোয়া-ই জাহান্দারি গ্রন্থে রাষ্ট্রনীতি আলোচনায় রাষ্ট্রীয় আইন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন।
* রাষ্ট্রীয় আইন:
বরনি মনে করেন যে, একজন আদর্শ সুলতানের প্রধান উদ্দেশ্যই হল কোরান ও ইসলামি আইন বা শরিয়তের বিধান মেনে রাষ্ট্রকে পরিচালনা করা। কিন্তু গোঁড়া মুসলিম বরনিও স্বীকার করেছেন যে, ভারতের মতো রাষ্ট্রব্যবস্থায় শরিয়তি আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। কারণ শরিয়তের বিধান ও ভারতের বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। এই অবস্থায় সুলতানের প্রধান কর্তব্য হল রাষ্ট্রকে রক্ষা করা, সেহেতু পুরোপুরি শরিয়তি শাসনব্যবস্থা প্রয়োগ না-করে তাঁকে বাস্তববোধের পরিচয় দিতে হবে। বরনি তাই সুলতানকে রাষ্ট্রশাসনের প্রয়োজনীয় বিধি যাকে বলা হয় জাওয়াবিত, তা প্রণয়নের অধিকার দিয়েছেন। জাওয়াবিত হল সুলতানের নিজস্ব অনুশাসন। তবে জাওয়াবিত জারি করে সুলতানরা বহুক্ষেত্রে ইসলামের বিধিকে ভঙ্গ করেছিলেন। তাই রাষ্ট্রশাসন (সিয়াসৎ) ও ধর্মীয় অনুশাসন (শরিয়ৎ)-এর মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হলে প্রথমটিকেই গুরুত্ব দিতে বলেছেন। তা ছাড়া যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শরিয়তের বিধানকেও যুগোপযোগী করার পরামর্শও তিনি দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, রাষ্ট্রনীতিবিদদের চিন্তা ও বৈষয়িক জ্ঞানের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপরিচালনার নীতিকে বলা হয় জাহান্দারি।
11. রাজতন্ত্র সম্পর্কে বরনির মতামত কী ছিল?
উত্তর:-
▶ সুলতানি যুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রনীতিবিদ জিয়াউদ্দিন বরনি তাঁর রচিত ফতোয়া-ই-জাহান্দারি গ্রন্থে রাজতন্ত্র সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করেছেন।
① চরম রাজতন্ত্রকে সমর্থন:
বরনি চরম রাজতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন। তিনি রাজতন্ত্রকে একটি বংশানুক্রমিক প্রতিষ্ঠান বলে উল্লেখ করেছেন। রাজা বা সুলতান হবেন রাষ্ট্রের সর্বশক্তির আধার এবং নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর মতে, সাম্রাজ্যের শান্তি, শৃঙ্খলা, স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার স্বার্থে সুলতানের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করার প্রয়োজন। তিনি সুলতানকে 'জিলুল্লাহ' বা 'আল্লাহর ছায়া' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি কোরানের নির্দেশ অনুযায়ী দেশ শাসন করবেন।
② পারসিক রাজতন্ত্রের অনুকরণের নির্দেশ:
বরনি পারসিক রাজতন্ত্রের প্রশংসা করেছেন। তিনি মনে করেন যে, পারস্যের সম্রাট ইসলামের আদর্শ ও ভাবধারা রক্ষা করে চলেছেন। পারস্যের রাজতন্ত্রের আদর্শ, রীতিনীতি, আদবকায়দা, জাঁকজমক, আড়ম্বর ও মর্যাদা সমগ্র ইসলামি জগতে শ্রদ্ধা অর্জন করেছে। তাই তিনি ভারতের সুলতানি রাজতন্ত্রকে পারস্যের সাসানীয় রাজতন্ত্রের অনুকরণে গড়ে তোলার পরামর্শ দিয়েছেন। ঐতিহাসিক আশরফ লিখেছেন যে, দিল্লিতে সুলতানরা মূলত পারস্যের সাসানিদ সম্রাটদের অনুকরণে বৈভবপূর্ণ জীবনযাপন করতেন এবং সর্বসমক্ষে তার প্রকাশ ঘটানো হত।
③ কাউন্সিল গঠন:
বরনি মনে করেন প্রশাসনিক কাজে সাহায্যের জন্য সুলতান কাউন্সিল গঠন করবেন। 'মজলিস-ই-খওয়াত' ও 'বার-ই-খাস' নামে দুটি সভা বা পরিষদের পরামর্শ সুলতান গ্রহণ করবেন।
12. জিয়াউদ্দিন বরনি নরপতিত্বের আদর্শ সম্পর্কে কী মতামত প্রকাশ করেছেন?
উত্তর:-
▶ নরপতিত্বের আদর্শ সম্পর্কে প্রধান কয়েকটি বিষয়-
① ইসলামীয় কর্তব্য পালন:
বরনি সুলতানকে রাষ্ট্রশাসনে ইসলামীয় ঐতিহ্য ও শরিয়তের বিধানকে গুরুত্ব দিতে বলেছেন। সুলতানের উচিত ইসলামীয় ঐতিহ্য ও রীতিনীতি অনুসারে রাষ্ট্রক্ষমতা প্রয়োগ করা। বরনি আরও বলেছেন যে, এ বিষয়ে সুলতানের উচিত অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করা। বরনি মনে করেন দেশে ইসলামীয় ঐতিহ্য ও রীতিনীতি সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য সুলতানের হাতে সর্বাত্মক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থাকা উচিত।
② বংশকৌলীন্য:
বরনি বলেছেন, সুলতানের 'উচ্চ বংশকৌলীন্য' থাকতে হবে। তিনি মনে করেন যে, সুলতান যদি উচ্চ ও পরাক্রমশালী রাজবংশের হন, তবে সাধারণ প্রজাদের সঙ্গে সুলতানের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা তৈরি হবে। তখন স্বাভাবিকভাবেই তিনি তাঁর প্রজাদের ভালোবাসা ও আনুগত্য লাভ করবেন।
③ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা:
সুলতান হবেন ন্যায়পরায়ণ ও তিনি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন। ন্যায়বিচার বলতে বরনি সত্য, ন্যায় ও ধর্মের প্রতিষ্ঠাকে বুঝিয়েছেন।
④ শরিয়তের বিধানকে অনুসরণের নির্দেশ:
বরনি মনে করেন, একজন শাসক শরিয়তের বিধান অনুসরণ করে সফলভাবে রাষ্ট্রপরিচালনা করবেন। এ প্রসঙ্গে তিনি। শাসনকার্যে পারস্যের সাসানিদ রাজতন্ত্রকে অনুকরণ করতে বলেছেন। কিন্তু শরিয়তের বিধান ও ভারতের বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে পার্থক্য থাকায় বরনি 'জাওয়াবিত' নামে রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়নের পরামর্শ দিয়েছেন।
13. 'ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্র' বলতে কী বোঝায়? অথবা, ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলি কী?
উত্তর:-
▶ 'ধর্মাশ্রয়ী' বা 'পুরোহিততান্ত্রিক' রাষ্ট্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Theocratic' 'Theocratic' শব্দটি সৃষ্টি হয়েছে Theos (থিয়োস) থেকে। Theo শব্দটির অর্থ 'দেবতা'। এইভাবে অর্থানুসারে 'দেবতাতান্ত্রিক রাষ্ট্র' হল 'ধর্মাশ্রয়ী' বা 'পুরোহিততান্ত্রিক রাষ্ট্র'।
* ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য:
i) ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্রে ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে গভীর সম্পর্ক থাকে এবং রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনীতি, শাসননীতি পরিচালিত হয় যাজক ও পুরোহিত শ্রেণির নির্দেশে ও পরামর্শে।
ii) ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্রে অদৃশ্য ঈশ্বর হলেন সব শক্তির উৎস এবং চূড়ান্ত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।
iii) এই ধরনের রাষ্ট্রে ঈশ্বরের নির্দেশই হল আইন।
iv) সুলতান বা সম্রাট ঈশ্বরের প্রতিনিধি। তিনি ঈশ্বরের নামে রাষ্ট্র পরিচালনা করে থাকেন।
14. জিয়াউদ্দিন বরনি দিল্লি সুলতানি রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে কী মতামত প্রকাশ করেছেন?
উত্তর:-
▶জিয়াউদ্দিন বরনি বলেছেন দিল্লির সুলতানি রাষ্ট্র ছিল ধর্মনিরপেক্ষ। এর কারণ-
① ইসলামের আদর্শ থেকে বিচ্যুতি:
বরনির মতে, মধ্যযুগে দিল্লির সুলতানেরা ইসলামীয় আদর্শ বা আইনবিধি (শরিয়ত) উপেক্ষা করেই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। ইসলামীয় বিধি উপেক্ষা করেই ভারতে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইসলামীয় তত্ত্ব অনুসারে খলিফা হলেন সমগ্র মুসলিম জাতির ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় প্রধান। সুলতানরা হলেন 'খলিফার প্রতিনিধি' ও তাঁর অধীনে থেকে রাষ্ট্রশাসন করবেন। দিল্লির সুলতানরা রাজনৈতিক কারণে নিজেদের 'খলিফার প্রতিনিধি' বলে ঘোষণা করলেও বাস্তবে তাঁরা ছিলেন স্বাধীন ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।
② রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতির পৃথিকীকরণ:
বরনি মনে করেন, দিল্লির সুলতানগণ বুঝেছিলেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ধর্মাবলম্বী ভারতে শাসনকালকে দীর্ঘস্থায়ী করতে হলে রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মনীতিকে আলাদা করা উচিত। সুলতানগণ সেই আদর্শই কার্যকারী করায় উদ্যোগী হয়েছিলেন।
15. তোমার মতে সুলতানি রাষ্ট্রের প্রকৃতি কী ছিল?
উত্তর:-
আমার কাছে বিষয়টি বিতর্কিত বলে মনে হয়েছে । অনেকে সুলতানি রাষ্ট্রকে "Theocratic' বা 'ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্র' বলে অভিহিত করেছেন। আবার অনেক আধুনিক ঐতিহাসিক ও গবেষক সুলতানি রাষ্ট্রকে 'ধর্মতন্ত্র' না-বলে, ধর্মনিরপেক্ষ বলার পক্ষপাতী। জিয়াউদ্দিন বরনির ধারণা ছিল সুলতানি রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ।
সুলতানি যুগে ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হত। উলেমা সম্প্রদায় যথেষ্ট প্রভাবশালী হলেও তাঁরা সুলতানকে প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক-এসব ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন না। বাস্তবে সুলতান ছিলেন সর্বেসর্বা, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় শক্তির প্রতীক। মনে রাখতে হবে দিল্লির সুলতানি-শাহি ছিল একটি কেন্দ্রীভূত রাজতন্ত্র। এই রাজতন্ত্রের অর্থাৎ সুলতানের শক্তির মূল ভিত্তি ধর্ম ছিল না, ছিল শক্তিশালী সেনাবাহিনী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের সমর্থন। সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন, আলাউদ্দিন খলজি ও মোহম্মদ-বিন-তুঘলকের হাতে শক্তিশালী সেনাবাহিনী ছিল, এজন্য তাঁরা উলেমাদের বিশেষ আমল দিতেন না। সুলতানদের উলেমাশ্রেণির ওপর নির্ভর করার পরিবর্তে সেনাবাহিনী ও অভিজাতবর্গের সমর্থনের ওপর নির্ভর করার জন্য আমি দিল্লি সুলতানি রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ, সামরিক ও অভিজাততান্ত্রিক বলে অভিহিত করতে পারি।
16. সফিস্টদের পরিচয় দাও। তাঁদের উদ্দেশ্য কী ছিল?
উত্তর:-
▶ প্রাচীন গ্রিসে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সফিস্ট যুক্তিবাদী দার্শনিকদের খোঁজ পাওয়া যায়। তাঁরাই প্রথম গ্রিসে রাষ্ট্রনৈতিক ধারণার বীজ বপন করেছিলেন। সফিস্ট চিন্তানায়করা ছিলেন গ্রিসের যুক্তিবাদের শিক্ষক।
* পরিচয়:
'সফিস্ট' বলতে বোঝায় দক্ষ ও জ্ঞানী মানুষ। সফোস (Sophos) একটি গ্রিক শব্দ, যার অর্থ 'জ্ঞানী'।
'সফিস্ট' দার্শনিকরা ছিলেন পেশাদার ভ্রাম্যমাণ শিক্ষক। এঁরা গ্রিসের নানা নগররাষ্ট্রে ঘুরে আলোচনা ও বিতর্কের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দিতেন। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের এথেন্সের জৌলুস ও সম্পদ এঁদের এথেন্সের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। তাই নানা স্থান ভ্রমণ করে তাঁরা এথেন্সে এসে থিতু হন। প্রোটো- গোরাস, জর্জিয়াস, প্রোডিকাস, হিগ্লিয়াস, থ্রাসিমাকাস, অ্যান্টিফোন-এঁরা ছিলেন সফিস্টদের প্রবীণ সম্প্রদায়। আর নবীন প্রজন্মের সফিস্টদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন লাইকোফ্রোন, অ্যালকিডামাস, পোেলাস, ক্রিটিয়াস প্রমুখ।
* উদ্দেশ্য:
সফিস্টদের উদ্দেশ্য ছিল-
① ইতিহাস, ভূগোল, নৃতত্ত্ব, গণিত, বিজ্ঞান, রাজনীতি ইত্যাদি নানা বিষয়ে শিক্ষিত করে তোলা।
② ধনী পরিবারের তরুণ প্রজন্মকে উপযুক্তরূপে শিক্ষিত করে জনজীবনে সফল করে তোলা। এই প্রসঙ্গে সব সফিস্টরা বলতেন যে, তাঁরা 'উৎকর্ষের' (excellence) চর্চা করেন।
17. সফিস্টদের রাষ্ট্রধারণা সম্পর্কে যা জান লেখো।
উত্তর:-
① রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব:
সফিস্টদের রচনাতেই প্রথম পাওয়া যায়-রাষ্ট্র সামাজিক চুক্তির দ্বারা সৃষ্টি। তাঁদের মতে, রাষ্ট্র কোনো প্রাকৃত বা স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান নয়, রাষ্ট্রের চরিত্রে বিবর্তনবাদের বৈশিষ্ট্য বিরাজমান। রাষ্ট্রকে সফিস্টরা কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান বলে মনে করতেন। সফিস্টরা মনে করতেন, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব শক্তি বা ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল। তাঁদের মতে, অসাম্য ও বাহুবলের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় কাঠামো প্রকৃতপক্ষে শক্তিশালীদেরই স্বার্থরক্ষা করে।
② রাষ্ট্রীয় আইন:
সফিস্টদের মতে রাষ্ট্রীয় আইন মানুষের তৈরি। সুতরাং, তা পরিবর্তনশীল ও আপেক্ষিক। কিন্তু ঈশ্বরের তৈরি প্রাকৃতিক নিয়ম বা আইন চিরন্তন বা শাশ্বত। কৃত্রিমভাবে আরোপিত রাষ্ট্রীয় আইন অমান্য করা গেলেও প্রাকৃতিক আইন অমান্য করা যায় না। সফিস্ট দার্শনিক হিপ্পিয়াস রাষ্ট্রীয় আইনের সঙ্গে প্রাকৃতিক আইনের পার্থক্য দেখিয়েছিলেন এবং রাষ্ট্রীয় আইনকে মানবজাতির ওপর নিপীড়নকারী হিসেবে অভিহিত করেছেন। সফিস্ট দার্শনিক থ্রাসমাকাস মনে করতেন, আইন ও সমাজের ধারা সমাজের শক্তির উৎস এবং এগুলি মানুষের সুবিধার্থে তৈরি। আর এক সফিস্ট দার্শনিক অ্যান্টিফোন বলেছেন, সবথেকে সুবিধাজনক জীবনযাপন হল অন্যান্য প্রতিবেশীদের সামনে রাষ্ট্রীয় আইনকে মেনে চলা, আর একলা অবস্থায় প্রকৃতির আইন মানা।
③ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ:
সফিস্টরা রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী আদর্শকে প্রাধান্য দিতেন। তাঁরা ব্যক্তির হাতেই ন্যায়-অন্যায় নির্ণয় করার অধিকারদানের পক্ষপাতী ছিলেন।
18. সক্রেটিস বিখ্যাত কেন?
উত্তর:-
▶ গ্রিসের চিন্তার জগতের অন্যতম দিকপাল ব্যক্তিত্ব ছিলেন সক্রেটিস (470-399 খ্রিস্টপূর্ব)। তাঁর খ্যাতির কারণ হল-
① আদর্শ শিক্ষক:
সক্রেটিসের মূল লক্ষ্য ছিল দেশের জন্য উপযুক্ত নাগরিক তৈরি করা। তাঁর চিন্তার মূল বিষয় ছিল আদর্শ রাষ্ট্র ও সৎ নাগরিক। তর্ক ও আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে তিনি শিক্ষা দিতেন। তৎকালীন তরুণ সমাজ তাঁর প্রতি দারুণভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। তাঁর শিক্ষার মূল কথা ছিল মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে সবকিছু যাচাই করে নিতে হবে।
② দর্শনশাস্ত্রে সক্রেটিসের অবদান:
(a) সক্রেটিস অনুসন্ধানের পদ্ধতি হিসেবে দ্বান্দ্বিক বিচারের প্রয়োগ করতেন।
(b) নীতিশাস্ত্রের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও তিনি দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণ ব্যবহার করেছিলেন। সক্রেটিস বলেছিলেন, 'সদ্গুণই জ্ঞান' (Virtue is Knowledge) | Virtue (সদগুণ) ছিল তাঁর কাছে সামাজিক গুণাবলি ও নৈতিক গুণাবলি, যা প্রকৃত মানুষ ও নাগরিক হিসেবে পূর্ণতা দেয়।
③ রাষ্ট্রদর্শনে অবদান:
সক্রেটিস রাষ্ট্রকে অপরিহার্য মানবিক সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি বলেছেন, সর্বশ্রেষ্ঠ শাসনতন্ত্র হল অভিজাততন্ত্র। গণতন্ত্র তাঁর কাছে ছিল অর্থহীন প্রক্রিয়া, অশিক্ষিতদের শাসন। রাষ্ট্রীয় আইনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা থাকলেও তিনি সবকিছুকেই যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে বিচার করার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে গুরুত্ব দেন। সক্রেটিস গ্রিক দার্শনিকদের ও রোমান দার্শনিকদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। তিনি হয়ে উঠেছিলেন পাশ্চাত্য রাজনৈতিক দর্শনের পিতামহ, নীতিশাস্ত্রের প্রবর্তক।
19. সক্রেটিসের রাষ্ট্রদর্শন সম্পর্কে কী জানো?
উত্তর:-
▶ সক্রেটিস ছিলেন প্রাচীন গ্রিসের এক খ্যাতনামা দার্শনিক।
রিপাবলিক গ্রন্থে তাঁর রাষ্ট্রদর্শন সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়, যেমন-
i) তিনি বলেছেন, 'সদ্গুণই হল জ্ঞান (Virtue is knowledge)। এই সম্পূণ সম্পন্ন নাগরিকদের দ্বারাই একটি আদর্শ রাষ্ট্র গড়ে তোলা যায়।
ii) তিনি বলেছেন শিক্ষার মধ্য দিয়েই একটি যুক্তিবাদী নাগরিক সমষ্টি গড়ে তোলা যায়। এর দ্বারা রাষ্ট্রের মঙ্গল হয়, কারণ তারা রাষ্ট্রীয় আইন মেনে চলে।
iii) গণতন্ত্র সম্পর্কে তিনি বলেছেন, গণতন্ত্র হল অজ্ঞ ও অশিক্ষিতদের শাসন। সেক্ষেত্রে তিনি বলেছেন জ্ঞানী ব্যক্তিরাই রাষ্ট্র শাসন করবে।
iv) তিনি বলেছেন সকলের উচিত রাষ্ট্রীয় আইন মেনে চলা।
20. রাষ্ট্রীয় আইনের প্রতি সক্রেটিসের শ্রদ্ধাবনতার পরিচয় দাও।
উত্তর:-
▶ গণতন্ত্রের প্রতি গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিসের আস্থা ছিল না।
তবে রাষ্ট্রীয় আইনের প্রতি তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তার পরিচয় পাওয়া যায়, যখন এথেন্সের সরকার তাঁকে কারাবন্দী করে রাখে, তখন সক্রেটিসের প্রিয় অনুগামীগণ তাঁকে কারাগার থেকে পালিয়ে যেতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি সেই অনুরোধে সাড়া দেননি। বরং তিনি বলেছিলেন, কারাগার থেকে পলায়ন করার অর্থ এথেনীয় আইন বা রাষ্ট্রীয় আইনকে অমান্য করা। তিনি আরও বলেন যে, এথেন্সের আইন তিনি অন্যান্য নাগরিকদের মতোই মেনে চলতে বাধ্য।
21. প্লেটো কে ছিলেন? তিনি কীজন্য বিখ্যাত?
উত্তর:-
▶ প্লেটো (427-347 খ্রিস্টপূর্বাব্দ) গ্রিক রাষ্ট্রদর্শনের এক অতি উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি ছিলেন সক্রেটিসের সুযোগ্য শিষ্য এবং 'রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক' অ্যারিস্টটলের শিক্ষক।
* গ্রন্থ:
প্লেটোর লেখাগুলি Dialogue হিসেবে লেখা। এগুলি হল Apology of Socretes, Laches, Protagoras প্রভৃতি। এ ছাড়া প্লেটোর অন্যান্য বিখ্যাত রচনাগুলি হল ফিডো (Phaedo), দ্য সিম্পোসিয়াম (The Sympo- sium), রিপাবলিক (Republic) ও লজ (Laws)। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করেছিল প্লেটোর Republic Laws I
* খ্যাতির কারণ:
ভাববাদী দর্শনের সূত্রপাত: গুরু সক্রেটিসের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে প্লেটো প্রকৃতিবাদী ও বস্তুনির্ভর দর্শনকে প্লেটো অস্বীকার করেন। তিনি ভাববাদী দর্শনের সূত্রপাত ঘটান। তিনি ছিলেন ভাববাদী (Utopian) দর্শনের জনক।
* রাষ্ট্র সম্পর্কিত দর্শনের রূপকার:
প্লেটো ছিলেন রাষ্ট্র সম্পর্কিত দর্শনের সুসামঞ্জস্য রূপকার। তাঁর হাতেই রাষ্ট্রদর্শন সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ ও সার্থকভাবে চিত্রিত হয়। তিনি তাঁর বিখ্যাত Republic গ্রন্থে তাঁর নিজস্ব ধারণাপ্রসূত ন্যায়বিচার ভিত্তিক দার্শনিক রাজা শাসিত 'আদর্শ রাষ্ট্র'-এর কল্পনা করেছিলেন। আর এই 'আদর্শ-রাষ্ট্র'-এর কর্মসূচি হিসেবে শিক্ষা এবং এক ধরনের সাম্যবাদী ব্যবস্থার বর্ণনা করেছিলেন।
22. প্লেটোর 'আদর্শ রাষ্ট্র' ধারণাটি সংক্ষেপে আলোচনা করো।
উত্তর:-
▶ গ্রিক রাষ্ট্রচিন্তাবিদ প্লেটো তাঁর বিখ্যাত Republic গ্রন্থে একটি আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা করেছেন।
① স্বাভাবিক রাষ্ট্র:
প্লেটোর ধারণায় আদর্শ রাষ্ট্র কোনো কল্পরাষ্ট্র নয়; তা হল স্বাভাবিক রাষ্ট্র। এ বিষয়ে তিনি বলেছেন, মানুষের প্রতিদিনের জীবনে অনেক ধরনের মৌলিক চাহিদা থাকে। এই চাহিদাগুলির প্রয়োজন মেটানোর জন্যই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। প্লেটোর মতে, মানুষ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এই কারণে বেঁচে থাকার জন্য তার যেসব বাস্তব জিনিসের প্রয়োজন সেগুলি সে একক উদ্যোগে মেটাতে পারে না। এক্ষেত্রে তাকে নির্ভর করতে হয় অন্যের সাহায্যের ওপর। এইভাবে জীবনধারণের তাগিদে অসংখ্য মানুষ পারস্পরিক আদানপ্রদানের ভিত্তিতে মিলিত হয় এক যৌথ জীবনে। এই যৌথ জীবনের সাংগঠনিক রূপই হল রাষ্ট্র।
② ব্যক্তির বর্ধিত আকার রাষ্ট্র:
প্লেটোর মতে, ব্যক্তি হলেন রাষ্ট্রের অংশ। ব্যক্তির বর্ধিত আকার রাষ্ট্র। ব্যক্তির কল্যাণই হল রাষ্ট্রের কল্যাণ। তাই নাগরিকদের কল্যাণকামী চিন্তাভাবনায় সুশিক্ষিতভাবে গড়ে তোলা রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত।
③ শ্রেণিভিত্তিক রাষ্ট্র:
প্লেটোর মতে, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক প্রয়োজন ও স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় আদর্শ রাষ্ট্রে তিনটি শ্রেণির উদ্ভব হয়,
যথা-
A. পালক বা শাসকশ্রেণি,
B. সামরিক শ্রেণি ও
C. কারিগর শ্রেণি।
রাষ্ট্রে যৌথ জীবনের অন্তর্ভুক্ত মানুষ সকলে একরকম নয়। নিজ নিজ সামর্থ্যের সীমা ও ধরন অনুযায়ী প্রতিটি মানুষ অন্য মানুষ থেকে আলাদা। এইজন্য একজন মানুষের পক্ষে বিভিন্ন ধরনের কাজ করা অসম্ভব এবং তা বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ, শ্রমবিভাজনই হল যৌথ জীবনের ভিত্তি।
④ প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রে শাসনভার থাকবে দার্শনিক রাজাদের ওপর। এদের গুণ হল প্রজ্ঞা।
⑤ প্লেটোর কল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রে কর্মবিশেষীকরণ ও শ্রম বিভক্তির নীতির প্রতিফলন ঘটবে, যোগ্য লোকেরা যোগ্য স্থান পাবে। রাষ্ট্র সংঘাতের হাত থেকে রেহাই পাবে। তাতে রাষ্ট্রে শান্তি ও উন্নতি প্রতিষ্ঠিত হবে।
23. অ্যারিস্টট্ল কে ছিলেন?
উত্তর:-
▶ প্রাচীন গ্রিসের একজন খ্যাতনামা দার্শনিক অ্যারিস্টটলের জন্ম হয় উত্তর-পূর্ব গ্রিসের স্ট্যাগিয়া নামক এক নগররাষ্ট্রে। তাঁর পিতা নিকোমেকাস-এর মৃত্যুর পর সতেরো বছর
বয়সে অ্যারিস্টটল এথেন্সে চলে আসেন এবং প্লেটোর সান্নিধ্য লাভ করেন। এথেন্সই ছিল তাঁর শিক্ষাজীবন ও কর্মজীবনের মূলকেন্দ্র। প্লেটো-প্রবর্তিত অ্যাকাডেমিতে তিনি পাঠগ্রহণ করেন এবং প্লেটোর শ্রেষ্ঠ ছাত্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। 343 খ্রিস্টপূর্বাব্দে ম্যাসিডনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ অ্যারিস্টট্লকে তাঁর পুত্র আলেকজান্ডারের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। পরে তিনি এথেন্সে 'লিসিয়াম' নামে একটি দার্শনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।
★ গ্রন্থ রচনা:
অ্যারিস্টট্ল যুক্তিবিদ্যা, অধিবিদ্যা, নীতিশাস্ত্র, কাব্যশাস্ত্র, অলংকারশাস্ত্র, মনস্তত্ত্ব, উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণীবিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি নানা বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। বিভিন্ন বিষয়ে অ্যারিস্টটলের পরিণত গবেষণাকে একত্রে 'কর্পাস অ্যারিস্টটেলিকাম' (Corpus Aristotelicum) বলা হয়। Politics গ্রন্থে তিনি তাঁর পূর্বতন লেখকদের মতামত তুলে ধরে আদর্শ রাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যাখ্যা করেন।
অ্যারিস্টট্ল এক সুসংহত, পূর্ণাঙ্গ ও পরিণত রাষ্ট্রতত্ত্ব নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটেছে স্বাভাবিকভাবেই বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। যেহেতু মানুষ প্রকৃতিগতভাবে রাজনৈতিক জীব, সে-কারণে রাষ্ট্র একটি স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান। অ্যারিস্টট্লকে 'পশ্চিমি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক' বলা হয়।
24. অ্যারিস্টটলের রাষ্ট্রধারণা সংক্ষেপে আলোচনা করো।
উত্তর:-
▶ প্লেটোর শিষ্য অ্যারিস্টট্ল এক পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রতত্ত্ব নির্মাণ করেছিলেন।
* অ্যারিস্টট্লের রাষ্ট্রধারণা
① রাষ্ট্র একটি স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান:
অ্যারিস্টট্ল মনে করেন, রাষ্ট্র হল একটি স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটেছে স্বাভাবিকভাবেই বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। তাঁর মতে, যেহেতু মানুষ হল একটি রাজনৈতিক জীব, তাই রাষ্ট্র একটি স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান। অ্যারিস্টট্ল বলেছেন, যে মানুষ রাষ্ট্রের মধ্যে বসবাস করে না সে হয় পশু নয়তো দেবতা। মানুষ তাঁর নিজের যুক্তি দিয়ে বুঝতে পারে রাষ্ট্রে বসবাসের কী সুবিধা ও রাষ্ট্রকে কেন তার দরকার। তাই মানুষ তাঁর নিজের জীবনের উন্নতির প্রয়োজনে ও সুরক্ষার তাগিদেই রাষ্ট্রের প্রয়োজনবোধ করে। রাষ্ট্র ছাড়া কোনো ব্যক্তি সম্পূর্ণ হতে পারে না। সমালোচকরা অ্যারিস্টটলের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। তাঁরা বলতে চান-রাষ্ট্রের উৎপত্তি স্বাভাবিক হলেও সেই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ে সম্মতি, ধর্ম, রক্তের সম্পর্ক, এমনকী বলপ্রয়োগ ইত্যাদিরও অবদান আছে। ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। প্রকৃতপক্ষে বহুধর্মী উপাদানের মিলনের ফলেই রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটেছে।
② রাষ্ট্র মানবদেহ স্বরূপ:
অ্যারিস্টট্লের মতে রাষ্ট্র হল মানবদেহের মতো। মানবদেহের যেমন বিভিন্ন অঙ্গ- প্রত্যঙ্গ থাকে এবং তাদের সমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গ দেহ গঠিত হয়, তেমনি রাষ্ট্রের মধ্যেও থাকে ব্যক্তি, সংঘ ইত্যাদি। একটির অনুপস্থিতিতে যেমন দেহ পূর্ণতা লাভ করতে পারে না, ঠিক তেমনই ব্যক্তি বা সংঘ ব্যতীত রাষ্ট্র পূর্ণ হতে পারে না। রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত না থাকলে ব্যক্তি মানুষের জীবনেরও কোনো মূল্য নেই।
③ ত্রিস্তরভিত্তিক:
অ্যারিস্টট্ল ধারণা করেছেন, রাষ্ট্র গড়ে ওঠে তিনটি স্তরের ওপর ভিত্তি করে, যথা-প্রথমে পরিবার, পরে গ্রাম এবং সবশেষে রাষ্ট্র।
④ রাষ্ট্রের স্থান ব্যক্তির আগে:
অ্যারিস্টট্ল মনে করেন, সময়ের বিচারে ব্যক্তির স্থান রাষ্ট্রের আগে হলেও গুরুত্বের বিচারে রাষ্ট্রের স্থান ব্যক্তির আগে। কারণ রাষ্ট্রের একটি অংশ হল ব্যক্তি। অ্যারিস্টটলের মতে, "রাষ্ট্র ব্যক্তি ও সংঘ পূর্ববর্তী।” তাঁর তত্ত্বে গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যতার অভাব পরিলক্ষিত হয়।
25. অ্যারিস্টট্ল সংবিধান বা রাষ্ট্রের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে কী মতামত প্রকাশ করেছেন?
উত্তর:-
▶ গ্রিসের বিখ্যাত রাষ্ট্রচিন্তাবিদ অ্যারিস্টট্ল রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অসামান্য অবদানের জন্য চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে রয়েছেন। অ্যারিস্টট্লকে 'রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক' বলা হয়। অ্যারিস্টট্ল তৎকালীন সময়ের প্রায় 158টি দেশের সংবিধান সংগ্রহ করে সেগুলি পর্যালোচনা করেছিলেন এবং একটি উত্তম সংবিধান বা সরকার ব্যবস্থার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর Politics গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে বিভিন্ন ধরনের সংবিধান, সরকার এবং তাদের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।
* সংবিধান বা রাষ্ট্রের শ্রেণিবিভাগ:
অ্যারিস্টট্ল বলেছেন যে,
① কোনো কোনো সংবিধানে শাসকগোষ্ঠী সকলের অভিন্ন স্বার্থরক্ষাকে প্রাধান্য দেন। এই ধরনের সংবিধানকে বলা হয় যথার্থ বা সঠিক (Real)।
② আবার কোনো ক্ষেত্রে শাসকগোষ্ঠী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীস্বার্থ অর্জনকে প্রাধান্য দেয়। এই ধরনের সংবিধান হল বিকৃত (Perverted) সংবিধান। তা ছাড়া অ্যারিস্টট্ল বলেছেন শাসনক্ষমতা একজনের হাতে থাকতে পারে, অল্প কয়েকজনের হাতে থাকতে পারে এবং বহুজনের হাতে থাকতে পারে। অ্যারিস্টট্ল শাসক গুণ (অভিন্ন স্বার্থ বা সংকীর্ণ স্বার্থ) এবং শাসকের সংখ্যা (একজন, কয়েকজন বা বহুজন)-এই দুটি নীতির ওপর ভিত্তি করে সংবিধান বা রাষ্ট্রের শ্রেণিবিভাগ করেছেন। যথার্থ বা সঠিক সংবিধানে একজন শাসক বা কয়েকজন শাসক বা বহুজন শাসক সমাজের সকলের অভিন্ন স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে শাসন পরিচালনা করেন। অ্যারিস্টট্ল একজনের শাসনকে বলেছেন 'রাজতন্ত্র', অল্প কয়েকজনের শাসনকে তিনি বলেছেন 'অভিজাততন্ত্র' এবং বহুজনের শাসনকে বলেছেন 'পলিটি'।
26. সেনেকার রাষ্ট্রধারণা সম্পর্কে যা জান সংক্ষেপে লেখো।
উত্তর:-
▶ সেনেকা ছিলেন একজন রোমান দার্শনিক। প্রাচীন রোম সম্রাট নিরো-র শিক্ষক ও রাজনৈতিক পরামর্শদাতা ছিলেন সেনেকা (50 খ্রিস্টপূর্বাব্দ-41 খ্রিস্টাব্দ)।
* সেনেকার রাষ্ট্রধারণা:
রাষ্ট্র সম্পর্কে সেনেকার ধারণা গড়ে উঠেছিল অধ্যাত্মবাদ, মানবতাবাদ ও বস্তুবাদের ওপর ভিত্তি করে।
① ন্যায় ও নীতিবোধ:
সেনেকার রাষ্ট্র ধারণার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল ন্যায় ও নীতিবোধ। তিনি মনে করেন রাষ্ট্রে ন্যায়নীতিকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত।
② রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য। তাঁর মতে রাষ্ট্র হল আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিতঃ
জনকল্যাণকর সংস্থা। তাই জনগণ রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে রাষ্ট্রের প্রতি সবসময় আনুগত্য দেখাবে। অপর দিকে রাষ্ট্র সকল মানুষকেই নাগরিকত্ব দেবে। সেনেকা মনে করেন নাগরিকত্ব হল একটি সর্বজনীন বিষয়। নাগরিক রাষ্ট্রকে যেমন আনুগত্য দেবে, এর বিনিময়ে রাষ্ট্র তেমনি তার নাগরিকদের সমস্ত সমস্যা ও অভাব-অভিযোগ দূর করে তার কল্যাণ করবে। আর সেই কারণেই রাষ্ট্র ও নাগরিক উভয়ের দিক থেকেই পারস্পরিক বন্ধন গড়ে ওঠা একান্ত জরুরি।
③ ভালো নেতা, ভালো সরকার:
সেনেকার মতে, শিক্ষিত, সৎ মানুষদের বেশিরভাগেরই শাসন করার মতো সাহস ও গুণ থাকে না। তাঁর মতে, যেসকল ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিত, কম সৎ তাঁরা অনেকেই সাহসী ও তাঁদের শাসন করার গুণ থাকে। তাঁরা সাহসের সঙ্গে রাষ্ট্রশাসন করতে পারেন এবং মানুষের যথেষ্ট মঙ্গল করতে পারেন। সেনেকার রাষ্ট্র ধারণায় এঁরাই হলেন ভালো নেতা এবং এঁদের পরিচালিত সরকার হল ভালো সরকার।
④ দুই কমনওয়েলথ:
সেনেকার মতে, প্রত্যেক মানুষ দুই কমনওয়েলথের সদস্য, যে পৌররাষ্ট্রের (Civil State) প্রজা ও বৃহত্তর রাষ্ট্র (Greater State)-এর সদস্য। বৃহত্তর রাষ্ট্র বলতে সেনেকা তখনকার সমাজকে বুঝিয়েছেন।
27. সেনেকা কে ছিলেন? তিনি বিখ্যাত কেন?
উত্তর:-
▶ সেনেকা ছিলেন রোমান রাষ্ট্রচিন্তাবিদ।
* গ্রন্থ রচনা:
সেনেকা স্টোয়িক দর্শনকে জনপ্রিয় করার জন্য 13টি নীতিমূলক দর্শন গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর সবথেকে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল On Clemency। সেনেকা তাঁর বন্ধু লুশিলিয়াসকে যেসকল চিঠিপত্র লিখেছিলেন সেগুলির মধ্যে 124টি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এগুলি সেনেকার দর্শনের ভান্ডার।
* সেনেকার খ্যাতির কারণ
① রাষ্ট্রধারাণার জন্য:
সেনেকার রাষ্ট্রধারণা গড়ে উঠেছিল অধ্যাত্মবাদ, মানবতাবাদ ও বস্তুবাদের ওপর নির্ভর করে। তিনি ব্যালেছেন, রাষ্ট্র হল আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এক জনকল্যাণকর সংস্থা। রাষ্ট্র প্রত্যেক ব্যক্তিকে নাগরিকত্ব দেবে। নাগরিকও রাষ্ট্রকে আনুগত্য দেখাবে। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য দেখানোর বিনিময়ে রাষ্ট্র তার নাগরিকদের কল্যাণ করবে। আর সেই কারণেই রাষ্ট্র ও নাগরিক উভয়ের দিক থেকেই পারস্পরিক বন্ধন গড়ে ওঠা প্রয়োজন। দুর্নীতি, 'বিশৃঙ্খলা থেকে রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য সেনেকা এমন এক রাষ্ট্রধারণার কথা বলছেন, যেখানে ন্যায়নীতি প্রধান ভূমিকা নেবে। তিনি বলেছেন, রাষ্ট্র শাসনের জন্য উচ্চশিক্ষার দরকার হয় না, দরকার হয় সাহস ও শাসন করার গুণ। তাঁর মতে কম শিক্ষিতরাই সাহসের সঙ্গে দেশশাসন করে মানুষের মঙ্গল করতে পারে।
② খ্রিস্টান ধর্মের ওপর প্রভাবের জন্য:
সেনেকার দর্শন ছিল অনেকটা ধর্মীয় ভাবযুক্ত। তিনি মানুষের পাপকর্ম ও মানবিকতা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন।। তিনি মানুষের রাজনৈতিক গুণাবলিকে দ্বিতীয় স্থানে রেখেছেন। তিনি সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন মানুষের ক্ষমা, দয়া, দান, সহিষ্কৃতা, ভালোবাসা প্রভৃতি গুণাবলিকে। ফলে খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে সেনেকার দর্শন গুরুত্ব লাভ করে। কারণ খ্রিস্টীয় দর্শনেও করুণা ও ক্ষমার মধ্য দিয়ে মানুষকে পাপমুক্ত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এইভাবে সেনেকা রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।
28. পলিবিয়াস প্রাচীন রোমান প্রজাতন্ত্রকে একটি মিশ্র সরকারের আখ্যা দেন কেন?
উত্তর:-
▶ পলিবিয়াস ছিলেন একজন গ্রিক দার্শনিক। তবে তিনি History of Rome লিখে বিশেষ খ্যাতি লাভ। করেছিলেন।
* মিশ্র সরকার ব্যবস্থা:
পলিবিয়াস লিখেছেন যে, রোম প্রজাতন্ত্রের মিশ্র সংবিধানই হল আদর্শ সংবিধান। এখানে-
① কনসালদের মাধ্যমে রাজতন্ত্রোর নীতিমালা,
② সিনেটের মাধ্যমে অভিজাতদের প্রতিনিধিত্ব এবং
③ জনপ্রতিনিধি পরিষদের মাধ্যমে গণতন্ত্রের সংমিশ্রণ ঘটেছে। মিশ্র সংবিধানের জন্যই রোম বিশ্ব সমাজ গঠনে সফল হয়েছে। তাঁর মতে, রোম নামে প্রজাতন্ত্র হলেও আসলে এখানকার শাসনতন্ত্র রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও প্রজাতন্ত্রের মিশ্রিত রূপ।
29. সিসেরিয়ান আইন কী?
উত্তর:-
▶ সিসেরো ছিলেন একজন প্রখ্যাত রোমান আইনজ্ঞ। আইন বিষয়ক তাঁর লেখা দুটি অমূল্য গ্রন্থ হল-টি রিপাবলিকা ও ডি লেজিবাস। এই গ্রন্থ দুটিতে প্রাচীন রোমান আইন, রাষ্ট্র, ন্যায়বিচার, সরকার প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। উক্ত সংকলনমূলক গ্রন্থে তিনি দু-প্র কার আইনের কথা বলেছেন। যথা-প্রাকৃতিক আইন ও রাষ্ট্রীয় আইন।
① প্রাকৃতিক আইন বলতে সিসেরো বুঝিয়েছেন, প্রাকৃতিক জগতে প্রচলিত সাধারণ নিয়মকানুন, যে নিয়মকানুন দ্বারা ঈশ্বর বিশ্বজগৎকে নিয়ন্ত্রণ বা শাসন করে চলেছেন। তিনি বলেছেন, পাথরখণ্ড আকাশের দিকে নিক্ষেপ করলে তা প্রাকৃতিক নিয়মেই মাটিতে নেমে আসে। তাঁর মতে, দৈব নির্দেশেই বিশ্বচরাচর পরিচালিত হচ্ছে। প্রাকৃতিক আইন সর্বত্র বিরাজমান এবং তা শাশ্বত। প্রাকৃতিক আইন হল চিরন্তন ও সর্বজনীন। তাই এই আইনের প্রতি মানুষের চূড়ান্ত আনুগত্য প্রদর্শন করা উচিত।
② সিসেরোর মতে, রাষ্ট্রীয় আইন তৈরি করে মানুষ; ব্যক্তি ও সমাজের হিতার্থে রাষ্ট্রীয় আইন তৈরি করা হয়। সেজন্য প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য রাষ্ট্রীয় আইনের প্রদর্শন করা। রাষ্ট্রীয় আইনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হবে, যার দ্বারা মানুষের জীবন পরিচালিত হবে।
30. সিসেরোর মতে 'ন্যায় ও সাম্যনীতি' কী?
উত্তর:-
▶ সিসেরোর রাষ্ট্রভাবনায় ন্যায় ও সমতার দৃষ্টিভঙ্গি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাঁর মতে, ন্যায়পরায়ণতা ও ন্যায়বিচার হল জাতির মেরুদণ্ড। তা না হলে সুষ্ঠু রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সুসংহত সমাজ গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। সিসেরো নৈতিকতা নির্ভর প্রাকৃতিক আইন, সকল মানুষের সমতা, বিশ্বরাষ্ট্র প্রভৃতি বিষয়ের ওপর বিশেষ জোর দেন। তাঁর মতে, ন্যায়বিচারের অভাবেই সমাজে নানা ধরনের বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তিনি মনে করতেন, যেহেতু বিশ্বের সমস্ত মানুষ একই প্রাকৃতিক আইন মেনে চলে, সেহেতু তারা সকলেই অনুগামী নাগরিক (fellow citizens)। তিনি বিশ্বাস করতেন না, একদল মানুষ সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রভুত্ব করবে, আর একদল মানুষ ক্রীতদাস জীবনযাপন করবে। তিনি একে প্রাকৃতিক আইন লঙ্ঘনের নামান্তর বলে মনে করেন। এই প্রশ্নে তিনি বলেছেন, প্রাকৃতিক আইনের সঙ্গে সংগতি রেখে রাষ্ট্রীয় আইন গড়ে তুলতে হবে। আবার এই রাষ্ট্রীয় আইনের মধ্যে সমতা থাকবে। তিনি মনে করতেন, সমতার নীতি হল মানুষের জীবন ও রাষ্ট্রজীবন পরিচালনার একটি নৈতিক শর্ত।
31. 'পিলগ্রিমেজ অব্ গ্রেস' কী?
উত্তর:-
▶ ইংল্যান্ডরাজ অষ্টম হেনরি তাঁর প্রথমা স্ত্রী ক্যাথারিনকে বিবাহবিচ্ছেদ করে অ্যানি বোলিন নামে এক মহিলাকে বিবাহ করার জন্য পোপের অনুমতি চেয়ে পাঠান। কিন্তু পোপ তা মঞ্জুর করেননি। এই অবস্থায় হেনরি ইংল্যান্ডের চার্চ থেকে পোপের কর্তৃত্বের অবসান ঘটানোর জন্য কতকগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, যেমন- প্রথমেই তিনি 1529 খ্রিস্টাব্দে রিফরমেশন পার্লামেন্টে আহ্বান করেন। ②1535 খ্রিস্টাব্দে টমাস ক্রমওয়েলকে ইংল্যান্ডের 'ধর্মপ্রতিনিধি' হিসেবে ঘোষণা করেন। এই অবস্থায় ক্রমওয়েল মঠ সংক্রান্ত নানান সংস্কারসাধন করেন। এর মধ্যে ছিল বড়ো বড়ো মঠগুলি ধ্বংসসাধন, মঠের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা ইত্যাদি।
এই অবস্থায় মঠব্যবস্থার প্রতি এই আক্রমণের প্রত্যুত্তরে ইংল্যান্ডে যে ধর্মীয় বিদ্রোহ মাথাচাড়া দেয়, তাকেই বলা হয় 'পিলগ্রিমেজ অব্ গ্রেস'।
32. ইউরোপে আধুনিক যুগের সূচনায় কীভাবে জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে ওঠে বলে মনে হয়?
উত্তর:-
▶ সামন্ততন্ত্রের যুগে ইউরোপের রাজশক্তি বেশ দুর্বল ছিল। কারণ সামন্ততান্ত্রিক সমাজের সুযোগ নিয়ে চার্চ ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিল। তাই দুর্বল রাজতন্ত্র চার্চের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেনি। কিন্তু চতুর্দশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধ থেকে পশ্চিম ইউরোপে নানা কারণে সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় শুরু হয়। এই অবস্থায় রাজশক্তি ক্রমশ সবল হয়ে উঠতে থাকে। আবার এই সময়ে এক নতুন বুর্জোয়া শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। এই বুর্জোয়া শ্রেণি তাদের ব্যাবসাবাণিজ্যের স্বার্থে ও নিরাপত্তার কারণে রাজাকে সমর্থন করে। এর ফলে রাজশক্তি আরও বলবান হয়। এসব কিছুর সম্মিলিত প্রভাবে ধীরে ধীরে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে। শেষপর্যন্ত এই জাতীয়তাবাদ বিভিন্ন রাষ্ট্রের ভিত্তিরূপে কাজ করে ইউরোপে শক্তিশালী জাতিরাষ্ট্রের সূচনা করে।
33. আদি-আধুনিক যুগের ইউরোপীয় জাতিরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে লেখো।
উত্তর:-
▶ আদি-আধুনিক যুগের ইউরোপীয় রাজনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব।
* বৈশিষ্ট্য:
① জাতিরাষ্ট্রগুলি ছিল সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।
② জাতিরাষ্ট্রের শীর্ষে ছিলেন কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার প্রতীক- রূপে সবল এক জাতীয় রাজশক্তি। সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্রের শাসক বা রাজা ছিলেন নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী।
③ জাতিরাষ্ট্রে 'নিরঙ্কুশ স্বৈরতন্ত্র' বা 'চূড়ান্তবাদ' প্রচলিত ছিল।
④ পঞ্চদশ শতক শুরু হওয়ার আগেই সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল, তাই সামরিক শক্তির পূর্ণ অধিকার কেন্দ্রীভূত হয়েছিল রাজার হাতে। রাজার নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রে। স্থায়ী অভিজ্ঞ সেনাবাহিনী গড়ে উঠেছিল।
v) সামন্ত- প্রভুদের প্রশাসনিক সব ধরনের ক্ষমতা হ্রাস করে রাজার হাতেই সেসব ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল।
vi) রাজা ছিলেন আইন প্রণয়নের অধিকারী। কিন্তু রাজা নিজে ছিলেন আইনের ঊর্ধ্বে। রাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থার ওপর সার্বভৌম শাসক বা রাজার একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।
34. রাষ্ট্র সম্পর্কে ম্যাকিয়াভেলির অভিমত কী ছিল?
উত্তর:-
▶ ম্যাকিয়াভেলি চার্চ ও ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কহীন একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কথা বলেছেন। তাঁর মতে,
i) মানুষ তার স্বার্থসিদ্ধি ও নিরাপত্তার প্রয়োজনেই রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে স্বীকার করে। নিজেদের উন্নতির জন্যই মানুষ রাষ্ট্রের প্রয়োজন উপলব্ধি করে।
ii) রাষ্ট্রের মূল পরিচয় ব্যক্ত হয় ক্ষমতার মধ্য দিয়ে।
iii) ভালো আইনব্যবস্থা ও উৎকৃষ্ট সমরশক্তি হল রাষ্ট্রের দুই স্তম্ভ। ম্যাকিয়াভেলির মতে যে রাষ্ট্র সমরশক্তিতে সুসজ্জিত সেখানে ভালো আইনব্যবস্থা থাকবেই। বস্তুত উপযুক্ত সমরশক্তি রাষ্ট্রকে স্থায়িত্ব দেয়।
iv) প্রতিটি রাষ্ট্র সর্বদা নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা করে।
v) শক্তিশালী শাসকই রাষ্ট্রের সুশাসনের ভিত্তি।
vi) তাঁর মতে, রাষ্ট্রশাসনের ক্ষেত্রে ন্যায়-অন্যায় বলে কিছু নেই। vii) রাষ্ট্রকে জনপ্রিয় হতে হলে মানুষের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা দিতে হবে। এ কাজগুলি করে নিজের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির দিকে সর্বদা নজর দেওয়াই হবে রাষ্ট্রের সরকারের লক্ষ্য। viii) ম্যাকিয়াভেলির মতে, যে রাষ্ট্রের প্রশাসনে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়, সেই রাষ্ট্রই 'শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র'।
35. রাষ্ট্রের উৎপত্তি কীভাবে হয়েছে এ বিষয়ে জাঁ বদার অভিমত কী ছিল?
উত্তর:-
▶ জাঁ বদাঁ লিখেছেন যে, রাষ্ট্র হল বিষয়সম্পত্তি-সহ বিভিন্ন পরিবারের সমষ্টি। তাঁর মতে, রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তিসমূহের প্রতিষ্ঠান নয়। রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে পরিবার থেকে। মানুষের জীবনধারণের জন্য যে মূল প্রয়োজন ও চাহিদা তা মেটাতেই পরিবারের উৎপত্তি। কাজেই পরিবার হল এক অতি প্রয়োজনীয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। পরিবার ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রথার ওপর নির্ভরশীল। পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সম্পত্তি দখলকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ শুরু হয়। এই সংঘর্ষে যে শ্রেণি বিজয়ী হয় তারা পরাজিত শ্রেণিকে ক্রীতদাসে পরিণত করে নিজেদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এইভাবে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে।
36. জাঁ বদাঁর 'সার্বভৌমত্বের তত্ত্ব' বলতে কী বোঝো?
উত্তর:-
▶ জাঁ বদাঁ বলেছেন, সুসংহত কোনো রাষ্ট্র প্রথমেই জনগণের জন্য ন্যায়বিচার এবং প্রতিরক্ষার বিষয়ে নজর দেবে। এরপর রাষ্ট্র তার জনগণের কল্যাণের জন্য মনোযোগী হবে। বদাঁর মতে, পরিবারে পুরুষের আধিপত্যের অনুগত হয়ে থাকতে হয় বাকি সদস্যদের। একইভাবে রাষ্ট্রের চরম আধিপত্যের অধীনে থাকতে হয় বাকি সকলকে বদাঁ বলেছেন, এই চরম আধিপত্য হল রাষ্ট্রের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। বদাঁ রাষ্ট্রের এই চরম আধিপত্যের নাম দিয়েছেন 'সার্বভৌমত্ব' (Sovereignty)।
37. জাঁ বদাঁর 'সার্বভৌমত্ব তত্ত্বের' বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো।
উত্তর:-
▶ জাঁ বদাঁর সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্যগুলি হল
i) রাষ্ট্রের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ। সামন্ততন্ত্র যেভাবে রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট করে, তা রাষ্ট্রবিরোধী কাজ। সুতরাং রাষ্ট্রীয় ঐক্যের প্রশ্নে রাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রয়োগ একান্ত জরুরি, যার দ্বারা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সব রাজনৈতিক সংস্থাগুলি নিয়ন্ত্রণে থাকে।
ii) তাঁর মতে, সার্বভৌমত্ব সকল আইনের ঊর্ধ্বে। কোনো আইনই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের নিয়ন্ত্রক হতে পারে না।
iii) রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের ক্ষমতা চিরস্থায়ী, কখনোই অস্থায়ী হতে পারে না। বঁদার মতে, রাষ্ট্রের চরম সার্বভৌম ক্ষমতাই অন্যান্য সংগঠন থেকে রাষ্ট্রকে পৃথক করেছে। সার্বভৌমত্ব নিঃসন্দেহে অবিভাজ্য।
38. পারসিক সম্রাটদের সঙ্গে স্যাট্রাপদের কীরূপ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল বলে মনে হয়?
উত্তর:-
▶ পারসিক সম্রাটদের সঙ্গে স্যাট্রাপদের একটি অম্লমধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তা লক্ষ করা যায় উভয়ের কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে। যেমন-
① দায়বদ্ধতা:
স্যাট্রাপরা তাঁদের কাজের জন্যে সম্রাটের কাছে দায়বদ্ধ থাকতেন। স্যাট্রাপরা দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে সম্রাটরা তাঁদের সাবধান করে দিতেন। এতে কোনো কাজ না হলে সম্রাট তাদের পদ থেকে সরিয়ে দিতেন।
② পর্যবেক্ষক:
স্যাট্রাপিতে কেমন কাজ হচ্ছে সম্রাট তা ঘুরে ঘুরে দেখার জন্য পর্যবেক্ষক নিয়োগ করতেন। তারা স্থানীয় প্রশাসন সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহ করে সম্রাটকে জানাতেন।
③ সতর্ক করা:
স্যাট্রাপরা তাঁদের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে এবং বার্ষিক বিবরণ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্রাটকে না-দিলে, সম্রাট কোনো কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার পূর্বে স্যাট্রাপদের সতর্ক করে দিতেন। তারপর একই ভুল করলে তাঁদের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিতেন।
④ স্বাধীনতা:
স্যাট্রাপরা সম্রাটের নামে প্রশাসন পরিচালনা করতেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসন বা সম্রাট দুর্বল হয়ে পড়লে বিভিন্ন স্যাট্রাপির শাসক স্বাধীনতা ভোগ করতেন।
⑤ বিদ্রোহ:
পারস্যের বিভিন্ন স্যাট্রাপদের বিদ্রোহ একটি নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়ে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। শেষপর্যন্ত বিদ্রোহ দমনে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে হয়েছিল। সর্বশেষ বড়ো বিদ্রোহ হয়েছিল তৃতীয় আলেকজান্ডারের আমলে।
39. ম্যান্ডারিন বলতে কী বোঝো?
অথবা,
'ম্যান্ডারিন' শব্দটির উৎপত্তি সম্পর্কে কী জানো?
উত্তর:-
▶ প্রাক-আধুনিক চিনের আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল ম্যান্ডারিন (Mandarin) বা উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী শ্রেণি। মাঞ্জু বা চিং বংশের শাসনাধীন চিনের আঞ্চলিক প্রশাসনব্যবস্থার প্রধান স্তম্ভ ছিল ম্যান্ডারিন শ্রেণি। 'ম্যান্ডারিন' একটি ইংরেজি শব্দ। 'ম্যান্ডারিন' বলতে বোঝায় 'চিনের সরকারি কর্মচারী'। আবার ইংরেজি 'ম্যান্ডারিন' কথাটি এসেছে পোর্তুগিজ ম্যান্ডারিম (Mandarim) শব্দ থেকে। চিনে ব্যাবসাবাণিজ্য করতে আসা পোর্তুগিজ বণিকরা চিনের উচ্চপদস্থ রাজ-কর্মচারীদের 'ম্যান্ডারিম' বলত। অনেকের দাবি যে, সংস্কৃত 'মন্ত্রিণ' শব্দ থেকে 'ম্যান্ডারিন' কথাটি এসেছে।
40. ম্যান্ডারিন পদে যোগ দিতে গেলে একজন চিনা নাগরিকের কোন্ কোন্ গুণ থাকা আবশ্যক ছিল?
উত্তর:-
▶ ম্যান্ডারিন পদে যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ করা হত। যাঁরা কাব্য ও সাহিত্যে পারদর্শী, যাঁরা নিজেদের কনফুসীয় শিক্ষা ও দর্শনচর্চা করেন তাঁদেরকে যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হত। চিনা সংস্কৃতি, কনফুসীয় দর্শন, ধ্রুপদি চিনের ঐতিহ্য সম্পর্কে তাঁদের বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে হত। অবশ্য ম্যান্ডারিন পদ সকলের জন্য খোলা ছিল না। অপরাধী, অভিনেতা, খেটে-খাওয়া মানুষ থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ এই পদের যোগ্য ছিল না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে চিনা সম্রাট স্বয়ং ম্যান্ডারিনদের নিয়োগ করতেন অথবা তাদের বরখাস্ত করতে পারতেন।
41. ম্যান্ডারিনদের কাজ কী ছিল?
উত্তর:-
▶ বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত এবং আঞ্চলিক প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত চিনের ম্যান্ডারিনগণ নানা ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন।
i) তাদের কর্তব্য ছিল সম্রাটের বা সাম্রাজ্যের অনুশাসন, কনফুসীয় জীবনাদর্শ ও চিনা ঐতিহ্য অনুসরণ করা।
ii) তারা সাম্রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতেন, কর আদায় করতেন, বিচার কাজ পরিচালনা করতেন, সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ব্যবস্থা করতেন, বাণিজ্য শুল্ক আদায় করতেন।
iii) তারা সরকারি ডাক-পরিসেবার তত্ত্বাবধান এবং অন্যান্য আঞ্চলিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কাজ পরিচালনা করতেন।
iv) সাধারণ মানুষের কাছে ম্যান্ডারিন শ্রেণি ছিলেন সর্বজ্ঞ অভিভাবক। ম্যান্ডারিনরা সরকারকে সুশাসনে সাহায্য করতেন। সম্রাটকে নানা বিষয়ে পরামর্শ দিতেন।
42. ইক্কা প্রথার গুরুত্ব আলোচনা করো।
উত্তর:-
▶ মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের শাসনব্যবস্থায় ইক্তা প্রথার গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ-
i) এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সুলতানি যুগে দিল্লিকেন্দ্রিক এক সুদৃঢ় শাসনব্যবস্থা গড়ে ওঠে।
ii) এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে চিহ্নিত অঞ্চলে সুলতানি সাম্রাজ্যের ভিত্তি মজবুত হয়।
iii) ইক্তাব্যবস্থার সূত্র ধরেই সম্রাট আকবর মোগল শাসনব্যবস্থায় মনসবদার নামক এক সামরিক পদাধিকারী শ্রেণি গড়ে তোলেন, যা ছিল মোগল সাম্রাজ্যের ঐক্য ও সংহতির প্রতীক।
iv) ইকতা প্রথার মধ্য দিয়ে সেযুগের গ্রাম্য অর্থনীতিতে নবজোয়ার আসে। সংশ্লিষ্ট ইক্কাগুলিতে ইক্কাদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় কুটিরশিল্প ও হস্তশিল্পের প্রসার ঘটে।
v) ইক্তা প্রথার মধ্য দিয়ে সুলতানি সাম্রাজ্যের অর্থনীতি সমৃদ্ধিশালী হয়। কারণ ইস্তাগুলি থেকে দিল্লি বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আদায় করত। তাতে সুলতানি রাজকোশ ভরে উঠত।
vi) ইকতাদারগণ কেন্দ্রকে প্রয়োজনে সৈন্য সরবরাহ করতেন। তাতে সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায়।
vii) গ্রাম থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করে তা ইক্কাদার নিয়ে আসত শহরে, সেখানে সে সাধারণভাবে বসবাস করত। ফলে শহরের বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়।
viii) ইজারাদারদের রাজস্ব হিসেবে গ্রামীণ উৎপাদনের এক মোটা অংশ শহরে যাবার ফলে শহরে জনবসতি বাড়ে। শহরেও হস্তশিল্প গড়ে ওঠে। এ ছাড়া ইকতা ব্যবস্থার মাধ্যমে দিল্লির সুলতানদের কয়েকটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছিল। যেমন-
(A) ইক্কা বিলির মাধ্যমে আমির ও মালিকদের সন্তুষ্ট করা সম্ভব হয়েছিল।
(B) সুলতানি রাজ্য স্ফীত হওয়ায় দূরবর্তী অঞ্চলে যোগাযোগের যে অসুবিধা দেখা দিয়েছিল ইক্কাদার নিয়োগের মাধ্যমে তা দূর হয়েছিল।
(C) ইক্কা ব্যবস্থা নতুন নতুন বিজিত এলাকা থেকে রাজস্ব আদায় সুনিশ্চিত করেছিল।
43. ইকতা প্রথার কোন্ কোন্ ত্রুটি বা দুর্বলতা লক্ষ করা যায় বলে মনে হয়?
উত্তর:-
▶ দিল্লির সুলতানরা কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার লক্ষ্য নিয়েই ইস্তা ব্যবস্থার প্রচলন করেন। যেমন-
① ইক্কাদাররা জমির মালিকানা পেত না।
② ইক্কাদাররা ততদিনই ইক্কার ভোগদখল করত যতদিন সুলতান তাদের প্রতি প্রসন্ন থাকতেন।
③ সবসময়ই ইকতাদারদের কাজকর্মে সরকারি হস্তক্ষেপ ঘটত। ④ তাদের মাঝেমধ্যে বদলিও করা হত। এইসব ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও ইক্কাদাররা ইক্কার ওপর স্বাধীন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চাইত। দুর্বল সুলতানদের আমলে ইক্কাদাররা ইক্কার ওপরে বংশানুক্রমিক অধিকার কায়েম করতে সক্রিয় ছিল এবং সফলও হয়েছিল। অনেক সময় আবার এমনও হত যে ইক্কাদাররা বেশি অর্থের লোভে নিজের নির্দিষ্ট ইক্কা অন্যকে ইজারা দিত। এর ফলে অতিরিক্ত অর্থের বোঝা কৃষকদের বইতে হত। অধ্যাপক ইরফান হাবিব মনে করেন, এই অবস্থায় কৃষকদের অবস্থা Semi-Serf বা আধা-ভূমিদাসদের মতোই হয়েছিল। এই দিক থেকে প্রচলিত ইকতা ব্যবস্থার মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক উপাদান খুঁজে পাওয়া যায়।
44. মনসবদারি প্রথা কী?
উত্তর:-
▶ সম্রাট আকবরের রাজত্বকালের আগে পর্যন্ত সামরিক ও বেসামরিক বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নগদ বেতনের পরিবর্তে জায়গির দেওয়া হত। আর জায়গি- রদাররা প্রয়োজন অনুযায়ী সম্রাটকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতেন। ফলে তাঁদের আর্থিক ও আঞ্চলিক প্রতিপত্তি বেড়ে যেত, অন্যদিকে সাম্রাজ্যের আর্থিক ক্ষতি হত। কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগে জায়গিরদাররাই স্বাধীনতা ঘোষণা করতেন। তাই পারস্যের অনুকরণে সম্রাট আকবর এই প্রথার পরিবর্তে 1577 খ্রিস্টাব্দে মনসবদারি প্রথার প্রবর্তন করেন।
'মনসব' কথার অর্থ হল 'পদমর্যাদা' বা 'Rank'। এই পদমর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিরা মনসবদার বা Holders of Rank নামে পরিচিত। ঐতিহাসিক আরভিন- এর মতে, পদমর্যাদা ও বেতনক্রম অনুসারে সামরিক কর্মচারীদের শ্রেণিবিভক্ত করাকেই বলা হয় মনসবদারি প্রথা।
45. মনসবদারি প্রথার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।
উত্তর:-
▶মনসবদারি প্রথা প্রবর্তনের মাধ্যমে সম্রাট আকবরের আমলে নগদ বেতন বা জায়গির দেওয়া হত। কিন্তু জায়গির প্রথার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ ঘটেনি। তা ছাড়া সে-সময়ের বাজারদর অনুযায়ী মনসবদারের বেতন ছিল বেশি। এই বেতন থেকেই তাদের নিজস্ব খরচ এবং ঘোড়া ও ভারবাহী পশুপালনের খরচ বহন করতে হত। জায়গিরপ্রাপ্ত মনসবদারদের খরচ ওই জায়গিরের আয় থেকে সরবরাহ করতে হত। মনসবদারি পদ বংশানুক্রমিক ছিল না। মনসবদারদের মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হত। মনসবদাররা যাতে নিয়মিত অশ্ব ও অশ্বারোহী মোতায়েন রাখতে বাধ্য হয় তার জন্য আকবর দাগ ও চেহেরা প্রথা চালু করেন। ঘোড়ার গায়ের চামড়ায় নম্বরের ছাপ দেওয়াকে বলা হত দাগ বা Branding প্রথা। চেহেরা প্রথার দ্বারা সৈন্যদের চেহারার বর্ণনা, নাম ও ঠিকানা-সহ দৈনিক কার্যবিবরণীর তালিকা (Descriptive roll) প্রস্তুত করা হত।
46. মনসবদারি প্রথার সুফল ও কুফল কী হয়েছিল বলে মনে হয়?
উত্তর:-
▶মনসবদারি প্রথার সুফল ও কুফলগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল-
★ সুফল:
i) মনসবদারি প্রথার ফলে কেন্দ্রীয় সামরিক শাসন- ব্যবস্থার ব্যাপকতা ছাড়াও সাম্রাজ্যের নানা অংশে সেনাবাহিনী গঠনের সুযোগসুবিধা পাওয়া যায়।
ii) এই পদ বংশানুক্রমিক না-হওয়ার ফলে প্রশাসনে যোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগের সুযোগ ছিল।
iii) মনসবদারি প্রথার ফলে সে-সময় সামন্তপ্রথার উদ্ভব ঘটেনি। iv)এর ফলে মধ্য এশিয়ায় অধিবাসীদের জাতিগত প্রাধান্য বিলুপ্ত হয়।
v) এই প্রথা মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করে।
★ কুফল:
মনসবদারি প্রথার নানা দুর্বলতা ছিল। সম্রাট আকবরের আমলেই এই প্রথার কুফলগুলি দেখা যায়।
i) এই প্রথা ছিল একটি জটিল প্রক্রিয়া, ক্রমে এর মধ্যে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা প্রবেশ করে।
ii)নানা সুযোগ- সুবিধা ভোগ করা সত্ত্বেও মনসবদাররা গোপনে কেন্দ্রীয় শক্তির বিরোধিতা করতেন।
iii) এই প্রথায় নানা দুর্নীতিও যুক্ত হয়।
47. জাট ও সওয়ার কী?
উত্তর:-
▶ প্রত্যেক মনসবদারকে জাট ও সওয়ার বাহিনী রাখতে হত। তবে এ নিয়ে বিতর্ক আছে। সম্ভবত 'জাট' বলতে পদাতিক বাহিনী ও 'সওয়ার' বলতে অশ্বারোহী বাহিনীকে বোঝানো হত। 1597 খ্রিস্টাব্দের পর সম্রাট আকবর মনসবদারি প্রথায় জাট ও সওয়ার ব্যবস্থা চালু করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল যাতে মনসবদারগণ সঠিক অশ্বরোহী ও পদাতিক বাহিনী পালন করেন। তবে কেউ কেউ মনে করেন যে, 'জাট' হল মনসবদারের ব্যক্তিগত পদমর্যাদা এবং 'সওয়ার' হল 'সওয়ার' সংখ্যা অনুযায়ী 'তলব-ই-তকিনান' বা পোষ্যদের জন্য বেতন। আবার সওয়ার পদ তিন ধরনের ছিল। যথা-ইয়াক-আস্থা বা এক অশ্বসওয়ারি, দু-আস্থা বা দুই অশ্বসওয়ারি ও শি-আস্থা বা তিন অশ্বসওয়ারি। মনসবদারগণ তাঁদের ভালো কাজের সুবাদে নানা উপাধিতে ভূষিত হতেন। যেমন-খান-ই-খানান, খান-ই-জাহান ইত্যাদি।
| একাদশ শ্রেণীর ইতিহাস এর দ্বিতীয় সেমিস্টারের সকল অধ্যায় ও প্রশ্নোত্তর |
|---|
| অধ্যায় ৪ - রাষ্ট্রের প্রকৃতি, রাষ্ট্রচিন্তা ও প্রতিষ্ঠান (Nature of the State and Its Apparatus) |
| অধ্যায় ৫ - পরিবর্তনশীল ঐতিহ্য (Changing Traditions) |
| অধ্যায় ৬ - বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিস্তৃত দিগন্ত (Expanding Horizons of Science and Technology) |
| একাদশ শ্রেণীর ইতিহাস এর দ্বিতীয় সেমিস্টারের সিলেবাস |
| Mock Test |
| Coming Soon |
| Coming Soon |