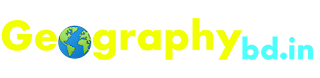একাদশ শ্রেণী ইতিহাস দ্বিতীয় সেমিস্টার, ষষ্ঠ অধ্যায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিস্তৃত দিগন্ত (Expanding Horizons of Science and Technology) প্রশ্ন উত্তর | Class 11, 1st semester History, Sixth Chapter । WBCHSE । Digonter Bistar
শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা আলোচনা করবো একাদশ শ্রেণীর ইতিহাস বিষয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিস্তৃত দিগন্ত নিয়ে। আশাকরি তোমরা একাদশ শ্রেণীর দ্বিতীয় সেমিস্টারের এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিস্তৃত দিগন্ত অধ্যায়টি থেকে যেসব প্রশ্ন দেওয়া আছে তা কমন পেয়ে যাবে। আমরা এখানে একাদশ শ্রেণীর, দ্বিতীয় সেমিস্টারের ইতিহাস বিষয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিস্তৃত দিগন্ত এর SAQ, শূন্যস্থান পূরণ, এক কথায় উত্তর দাও, Descriptive, ব্যাখ্যা মুলক প্রশ্নোত্তর , সংক্ষিপ্ত নোট এগুলি দিয়েছি। এর পরেও তোমাদের এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিস্তৃত দিগন্ত অধ্যায়টি থেকে কোন অসুবিধা থাকলে, তোমরা আমাদের টেলিগ্রাম, হোয়াটসাপ , ও ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারো ।
অধ্যায় ৬ - "বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিস্তৃত দিগন্ত (Expanding Horizons of Science and Technology)/ দিগন্তের বিস্তার" অধ্যায়ের সকল প্রশ্ন ও উত্তর
1. বিজ্ঞান বলতে কী বোঝো?
উত্তর:-
▶ 'Science' বা 'বিজ্ঞান' কথাটি এসেছে লাতিন Scientia শব্দ থেকে। বাংলা ভাষায় এর আক্ষরিক অর্থ হল বিশেষ জ্ঞান। সাধারণভাবে 'বিজ্ঞান' বলতে বোঝায় "কোনো একটি বিষয়ে শৃঙ্খলিত জ্ঞান"। অথবা বলা যায় যে, যুক্তি ও তথ্য দিয়ে প্রমাণ সাপেক্ষে কোনো বিষয়ে জ্ঞানার্জনই হল বিজ্ঞান।
* সংজ্ঞা:
বিজ্ঞানের সংজ্ঞা কী অথবা বিজ্ঞান বলতে কী বোঝায়-তা নিয়ে পণ্ডিতমহলে বিতর্কের শেষ নেই। যেমন- Wikipedia মতে, বিজ্ঞান হল প্রকৃতি সম্পর্কিত জ্ঞান, যা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাকৃতিক ঘটনাকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে। Encyclopedia Britannica-য় উল্লেখ রয়েছে-"বিজ্ঞান হল প্রাকৃতিক ঘটনাবলি ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে শৃঙ্খলাবদ্ধ জ্ঞান"। বর্তমানে আমরা বিজ্ঞান বলতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও তার বিভিন্ন শাখা, যেমন-পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূবিদ্যা, জীববিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, পূর্তবিদ্যা, কৃষিবিদ্যা, মনোবিদ্যা প্রভৃতিকে বুঝি।
2. আধুনিক বিজ্ঞানচর্চায় রজার বেকনের অবদান কী ছিল?
অথবা,
রজার বেকনকে 'আধুনিক বিজ্ঞানের জনক' বলা হয় কেন?
উত্তর:-
▶ ইউরোপীয় রেনেসাঁকালে ইংল্যান্ডের এক স্বনামধন্য বিজ্ঞানী ছিলেন রজার বেকন। তিনিই প্রথম বিজ্ঞানচর্চায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার ওপর জোর দিয়েছিলেন। সে-কারণে তাঁকে 'আধুনিক বিজ্ঞানের জনক' বলা হয়।
* বেকনের বিজ্ঞানচর্চা:
রজার বেকনের লেখা দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ হল-ওপাস মাজুস (Opus Majus) এবং ওপাস মাইনাস (Opus Minus)। পোপ চতুর্থ ক্লিমেন্টের অনুরোধে রজার বেকন ওপাস মাজুস গ্রন্থটি লেখা শুরু করেন। এটি লাতিন ভাষায় লিখিত। এতে স্থান পেয়েছে ব্যাকরণ, যুক্তিবিদ্যা, গণিত, পদার্থবিজ্ঞান ও দর্শন। এটি সাতটি ভাগে বিভক্ত। গ্রন্থটির পঞ্চম খণ্ডে আলোর প্রতিসরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অনেকের মত যে, তিনিই চশমার কাচ আবিষ্কার করেছিলেন, যার ইঙ্গিত পাওয়া যায় তাঁর লেখা অন বার্নিং লেন্সস্ গ্রন্থে। ③ খুব সম্ভবত তিনিই ইউরোপে প্রথম গান পাউডার বা বারুদের ফর্মুলা ব্যবহার করেছিলেন। এর উল্লেখ পাওয়া যায় তাঁর লেখা ওপাস টেরটিয়াম (Opus Tertium) গ্রন্থে। বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর কতকগুলি ভবিষ্যদ্বাণী আশ্চর্যভাবে মিলে গেছে। যেমন-অশ্ববিহীন যান বা মোটরগাড়ি, পালবিহীন জাহাজ বা স্টিমার, হাওয়ায় ভাসা যান বা উড়োজাহাজ, ভারোত্তোলনকারী যন্ত্র বা ক্রেন এবং ঝুলন্ত সেতু।
3. আধুনিক বিজ্ঞানচর্চায় ফ্রান্সিস বেকনের অবদান কী ছিল?
অথবা,
ফ্রান্সিস বেকনকে কেন 'পরীক্ষামূলক দর্শনের জনক' বলা হয়?
উত্তর:-
▶ এলিজাবেথীয় যুগ তথা রেনেসাঁকালের ইংল্যান্ডের এক স্বনামধন্য বিজ্ঞানী ছিলেন ফ্রান্সিস বেকন। তিনি মনে করতেন যে, গভীর পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে নানা তথ্য সংগ্রহ করাই বিজ্ঞানসাধকের মূল কর্তব্য। তাঁর মতে, বিজ্ঞানী প্রথমে তাঁর চারদিকে যা ঘটবে তা সূক্ষ্মভাবে লক্ষ করার পর সেই ঘটনার বিশ্লেষণ করে একটি সিদ্ধান্তে আসবেন এবং তারপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ঘটনার রহস্য আবিষ্কার করবেন। এজন্য তাঁকে 'পরীক্ষামূলক দর্শনের জনক' বলা হয়। বিজ্ঞান বিষয়ক তাঁর লেখা দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ হল অ্যাডভান্সমেন্ট অব্ লার্নিং (Advancement of Learning) ও নোভাম অর্গানাম (Novum Organum)।
4. ইউরোপীয় রেনেসাঁ যুগের বিজ্ঞানী লিয়োনার্দো-দ্য- ভিঞ্চির অবদান আলোচনা করো।
উত্তর:-
> লিয়োনার্দো-দ্য-ভিঞ্চি ছিলেন ইটালির রেনেসাঁ যুগের বহুমুখী প্রতিভাধর এক মহাপুরুষ। তিনি ছিলেন গণিতবিদ, রসায়নবিদ, ভূতত্ত্ববিদ, স্থপতি ও ভাস্কর। এর বাইরে বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর যে অগাধ পান্ডিত্য ছিল তা তিনি প্রমাণ করেছিলেন, যেমন-
① ভেনিস শহরকে বহিরাগত আক্রমণের হাত থেকে রক্ষার জন্য আবিষ্কার করেছিলেন স্থানান্তরযোগ্য ব্যারিকেড।
② তিনি তাঁর পত্রিকায় বিভিন্ন যন্ত্রের নকশা এঁকে প্রকাশ করেছিলেন। যেমন-নানারকমের বাদ্যযন্ত্র, একটি যান্ত্রিক সৈন্য, হাইড্রোলিক পাম্প, ভানার মর্টার শেল।
③ তিনি 240 মিটার দীর্ঘ একটি সেতুর (গোল্ডেন হর্ন ব্রিজ) নকশা তৈরি করেছিলেন।
④ তিনি তাঁর নোটবুকে আরও অনেক যন্ত্রের নকশা এঁকে গিয়েছেন, যেমন-ঘোড়া বাহিত একটি যন্ত্র, কামান, হুইললক মাস্কেট, প্যারাস্যুট, প্যারাবোলা আঁকার কম্পাস, বায়বীয় স্ক্রু, ফায়ারিং কামান, লাইফ বেল্ট, সাঁজোয়া গাড়ি ইত্যাদি। এসব কারণে তাঁকে 'Universal Man' বা 'সর্বজনীন মানুষ' বলা হয়।
5. অপরসায়নচর্চায় জাস্টাস লিবিগের অবদান কী ছিল? অথবা, জাস্টাস লিবিগকে কেন 'সার শিল্পের জনক' বলা হয়?
উত্তর:-
▶ জাস্টাস লিবিগ ছিলেন উনিশ শতকের এক খ্যাতনামা জার্মান অপরসায়নবিদ। তাঁকে বলা হয় 'সার শিল্পের জনক'। কারণ
① তিনি উদ্ভিদের পুষ্টি কীভাবে হয় তা নিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন এবং এতে তিনি নাইট্রোজেন (N), ফসফরাস (P) এবং পটাশিয়াম (K)-এর রাসায়নিক উপাদানগুলিকে উদ্ভিদের বৃদ্ধির অপরিহার্য উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করে হইচই ফেলে দেন।
② তিনি দেখান যে, উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডল ও জল (H₂O) থেকে কার্বন (C) ও হাইড্রোজেন (H) সংগ্রহ করে। তাঁর সবচেয়ে স্বীকৃত কৃতিত্ব হল নাইট্রোজেনভিত্তিক সার তৈরি করা। তা প্রয়োগ করে সাফল্যও পেয়েছিলেন।
③ 1832 খ্রিস্টাব্দে তিনি অ্যানালেন ডার চেমি নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ক্রমে এটি অ্যানালেন ডার ফার্মাসি নামে পরিচিত হয় এবং রসায়নের একটি নেতৃত্বস্থানীয় পত্রিকায় পরিণত হয়।
6. কিমিয়াবিদ্যা বা অপরসায়নবিদ্যাচর্চার গুরুত্ব কী?
উত্তর:-
▶ কিমিয়াবিদ্যা বা অপরসায়নে জাদুবিদ্যা, রহস্য, সর্বপ্রাণবাদ, জ্যোতিষ প্রভৃতি ছিল অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিমিয়াবিদদের অনেকেই রোগ সারাতে কবচ বা মাদুলির ওপর বিশ্বাস করতেন। প্রথমদিকে বিভিন্ন ধাতু সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞানও ছিল ভাসাভাসা। ফলে অনেকেই মনে করেন যে, অপরসায়নের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। তবুও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, আধুনিক রসায়নচর্চার পথ প্রশস্ত করেছিল এই কিমিয়াবিদ্যা। যেমন-
① জাদুবিদ্যায় ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদান-সহ বিভিন্ন ধাতুকে কেন্দ্র করেই অনুসন্ধিৎসা শুরু হয়। ফলে রসায়নবিদ্যার প্রসার ঘটে।
② কিমিয়াবিদ্যাচর্চার মধ্য দিয়েই বিজ্ঞানীরা বহু পদার্থের পরিচয় পায়। সেই তালিকায় ছিল অসংখ্য পদার্থ। যেমন-পারদ, আর্সেনিক, সালফাইড, নিশাদল, সোরা, নানাধরনের খনিজ পদার্থ। শুধু তাই নয়, তারা অ্যাকুয়া রিজিয়ার মতো অ্যাসিডের ব্যবহার জানত, যা দিয়ে সোনা গলানো হত।
③ চিকিৎসাশাস্ত্রে কিমিয়াবিদদের অবদান কম ছিল না। যেমন-কেমোথেরাপি, অ্যানেস্থেসিয়া, ঔষধের সেবনবিধি ইত্যাদি। সে-যুগেই সর্বপ্রথম বারুদ আবিষ্কৃত হয়। সে-কারণে অপরসায়নকে আধুনিক রসায়নবিদ্যার পরীক্ষাগার বলা হয়।
7. কাকে, কেন 'আধুনিক পরমাণুবাদের জনক' বলা হয়?
উত্তর:-
▶ জন ডালটন ছিলেন একজন ব্রিটিশ রসায়বিদ। 1808 খ্রিস্টাব্দে তিনি পরমাণু গঠনের তত্ত্ব প্রকাশ করে খ্যাতিলাভ করেন। এবিষয়ে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থটি হল A New System of Chemical Philosophy। ডালটনের তত্ত্বের ভিত্তি ছিল রাসায়নিক সংযোগ সংক্রান্ত কিছু পরীক্ষা ও তার ফল। তাঁর পরমাণুবাদের স্বীকৃত বিষয়গুলি হল-
① প্রত্যেক পদার্থ অসংখ্য অবিভাজ্য কণিকা দ্বারা গঠিত। এগুলিকেই বলা হয় atom বা পরমাণু।
② একই পদার্থের পরমাণুগুলির আকার, আকৃতি, ভর ও রাসায়নিক ধর্ম অভিন্ন।
③ বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুর আকার, আকৃতি, ভর ও রাসায়নিক ধর্ম বিভিন্ন।
(4) রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্বারা যেমন পরমাণু সৃষ্টি করা যায় না, তেমনি তা ধ্বংসও করা যায় না।
(5) পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তনের সময় ওই পদার্থের পরমাণুগুলি অখণ্ড কণারূপে সরল অনুপাতে যুক্ত হয় এবং তৈরি হয় যৌগিক পরমাণু।
(6) কোনো যৌগিক পদার্থের বিয়োজনে পরমাণু পাওয়া যায় এবং সেগুলি পুনরায় যুক্ত হয়ে ওই একই অথবা নতুন কোনো যৌগ তৈরি করে বা করতে পারে। এসব কারণে তাঁকে 'আধুনিক পরমাণুবাদের জনক' বলা হয়।
8. ডাইনি এবং ডাইনিবিদ্যা কী?
উত্তর:-
> ডাইনিবিদ্যা (witchcraft) হল বিভিন্ন ধরনের জাদুকরি বা অতিমানবিক ক্ষমতা নিয়ে চর্চা। এই জাদুকরি ক্ষমতা নিয়ে যে বা যারা চর্চা করে বা করত তাকে বা তাদের বলা হয় ডাইনি বা ডাকিনি। ডাইনিদের মূলত মহিলা হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়। বিভিন্ন লিখিত উপাদান থেকে বিশ্বের নানান সভ্যতায় এই চরিত্রগুলির অস্তিত্বের কথা জানা যায়। এরা মূলত এক-একটি কাল্পনিক চরিত্র। সাধারণভাবে ডাইনিবিদ্যা বলতে বোঝায় জাদুবিদ্যা তথা অতিপ্রাকৃতিক শক্তিকে ব্যবহার করার ক্ষমতাকে।
9. কালো জাদু (Black magic) কী?
উত্তর:-
▶ মধ্যযুগে ইউরোপের ডাইনিরা জাদুবিদ্যায় পারদর্শী ছিল। এর দ্বারা তারা তাদের মনোবাসনা পূরণ করত। এমনই একটি জাদু ছিল কালো জাদু (Black Magic)। এর দ্বারা মানুষের ক্ষতিসাধন করা হয় বা হত। এটি হল ধ্বংসাত্মক ও প্রতিহিংসা-পরায়ণ ম্যাজিক। এই ম্যাজিকে সাধারণত ভূত, প্রেত, আত্মা ইত্যাদির আশ্রয় নেওয়া হয়। কালো জাদুতে দেখা যায় ছ-টি প্রক্রিয়া। এককথায় এগুলিকে বলা হয় ষষ্কর্ম। এগুলি হল-তন্ত্রে উচাটন, মারণ, বিদ্বেষণ, স্তন্তন, আকর্ষণ ও বশীকরণ। বহু তন্ত্রসাধক এই জাদুর আশ্রয় নেয়। এখানে তন্ত্রসাধনা চলে মূলত শ্মশানকে কেন্দ্র করে। কথিত আছে যে, ভূতবিদ্যা দ্বারা কবর থেকে মৃত ব্যক্তির শরীর তুলে তাকে পুনরায় জীবিত করা হয় এবং তাকে নানান অপকর্ম তথা ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যবহার করা হয়। আবার জানা যায় যে, এই ম্যাজিক দ্বারা ইউরোপে শয়তানরা ইচ্ছামতো তাদের নশ্বর দেহ ত্যাগ করে স্বর্গ অথবা নরকে যাত্রা করতে পারে।
10. জাদুবিদ্যার তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।
উত্তর:-
▶ মধ্যযুগের ডাকিনিরা জাদুবিদ্যায় পারদর্শী ছিল। জাদুবিদ্যার বৈশিষ্ট্যগুলি হল-
① উদ্দেশ্যগত:
জাদুবিদ্যায় পারদর্শী ডাকিনি, যোগিনী,ওঝা, গুণিনরা মানুষ তথা সমাজের যেমন ভালো কাজ করত, তেমনি খারাপ কাজও করত।
(i) ভালো কাজের তালিকায় রয়েছে-বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণ, ব্যাবসাবাণিজ্যের উন্নতি, শত্রুবিনাশ, মানুষের ভাগ্য ফিরিয়ে আনা, সুস্বাস্থ্য প্রদান করা ইত্যাদি।
(ii) অন্যদিকে তাদের হাত দিয়ে খারাপ বা ধ্বংসাত্মক কাজও হয় বা হত, যেমন- বশীকরণ, ক্ষেতের ফসল নষ্ট করা, গৃহপালিত বিভিন্ন পশু ও পাখির জীবন নষ্ট করা, গর্ভবতী নারীর অকালে গর্ভপাত করা, শিশুদের প্রাণে মেরে ফেলা ইত্যাদি।
② প্রয়োগগত:
এই কাজ করার সময় তারা বিভিন্ন মন্ত্রপূত বস্তু, যেমন-তাবিচ, মাদুলি, কবচ, জলপড়া, নুনপড়া, বিভিন্ন জাদুকরী চিহ্ন বা প্রতীক, জাদুকরী বোতল ইত্যাদি ব্যবহার করত বা করে। আবার মন্ত্র উচ্চারণ করে বা ঝাড়ফুঁক দিয়ে তারা তাদের কাজ হাসিল করে।
③ উপকরণগত:
জাদুকররা তাদের কাজ হাসিল করার জন্য যেমন মন্ত্র ও মন্ত্রপূত বস্তু ব্যবহার করে; তেমনি তারা বিভিন্ন বস্তুর ওপর জাদুবিদ্যা প্রয়োগ করে। এগুলি হল-
(i) মানুষের মাথার চুল, নখ, হাড়, মাংস, শরীরের ময়লা,
(ii) পাখির নখ, পালক, মাংস,
(iii) গাছের শিকড়, ছাল, ফল-ফুল ও লতা-পাতা,
(iv) মাটি, ঝাঁটা, কড়ি ও বিভিন্ন ধাতু,
(v) পশুর সিং ইত্যাদি।
11. অ্যারিস্টারকাসকে কেন 'হেলেনিস্টিক কোপারনিকাস' বলা হয়?
উত্তর:-
> অ্যারিস্টারকাস (310-230 খ্রিস্টপূর্বাব্দ) ছিলেন হেলেনিস্টিক যুগের (323-32 খ্রিস্টপূর্বাব্দ) গ্রিসের এক খ্যাতনামা জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তিনি বলেছিলেন যে, পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। তাঁর এই অভিমত 'Heliocentric theory of the Universe' বা 'সূর্যকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের তত্ত্ব' নামে খ্যাত; যে তত্ত্ব তাঁর সমসাময়িককালে এবং তাঁর মৃত্যুর পরও সুদীর্ঘকাল যাবৎ গৃহীত হয়নি। তিনি বলেছিলেন, পৃথিবী নয়; সূর্যই বিশ্বব্রহ্মান্ডের কেন্দ্রে। পৃথিবী তাকেই কেন্দ্র করে ঘুরছে। তিনি অ্যারিস্টটলের 'Geocentric theory'-র বিরোধিতা করেছিলেন এবং আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানী কোপারনিকাস অ্যারিস্টারকাসের তত্ত্ব দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন বলে, তাঁকে 'Hellenistic Copernicus' বলা হয়।
12. প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিদ্যাচর্চায় আর্যভট্টের অবদান কী?
উত্তর:-
▶ প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন আর্যভট্ট। জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত তাঁর লেখা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হল আর্যভট্টীয়। মাত্র 23 বছর বয়সে তিনি এই গ্রন্থটি রচনা করেন। এতে রয়েছে মোট 4টি অধ্যায় ও 118 টি স্তোত্র। এর গোলকপাদ অধ্যায়ে উল্লেখ করেন যে,
(1) পৃথিবী তার নিজ অক্ষের সাপেক্ষে ঘোরে। সৌরজগতের গ্রহগুলির এই কক্ষপথ হল উপবৃত্তাকার।
(2) পৃথিবীর পরিধি হল 39,968 কিমি।
(3) সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের কারণ ও সময়ের ব্যাখ্যা।
(4) চাঁদের আলো আসলে সূর্যের আলোর প্রতিফলনেরই ফলাফল।
(5) তিনি পৃথিবীর আহ্নিক গতি (পৃথিবীর নিজস্ব ঘূর্ণন) ও বার্ষিক গতির (সূর্যের চারপাশে আবর্তন) পরিচয় দেন। অনেকের মত যে, সূর্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থটিও তিনি রচনা করেছিলেন। তবে এ নিয়ে বিতর্ক আছে। অনেকের দাবি যে, এই গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন তাঁর সুযোগ্য শিষ্য লতাদেব।
13. কাকে, কেন 'ভারতের প্লিনি' বলা হয়?
উত্তর:-
> ভারতের খ্যাতনামা জ্যোতির্বিদ বরাহমিহিরকে 'ভারতের প্লিনি' বলা হয়। তিনি ছিলেন গুপ্তযুগের খ্যাতনামা দার্শনিক, জ্যোতির্বিদ ও গণিতবিদ। তাঁর শ্রেষ্ঠ দুটি গ্রন্থ হল পঞ্চসিদ্ধান্তিকা এবং বৃহৎসংহিতা। এই দুটি গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় জ্যোতিষ ও ফলিত জ্যোতিষ। গ্রহাদির আবর্তন ও অবস্থানের ফলে পৃথিবী, মানবজীবন ও কৃষিকাজে কতটা প্রভাব পড়ে তা তিনি দেখিয়েছিলেন। তিনি ভারতের ভৌগোলিক বিবরণ-সহ আবহাওয়ার ওপর আলোকপাত করেন। এজন্য তাঁকে রোমান প্রকৃতিবিদ প্রিনির সঙ্গে তুলনা করে 'ভারতের প্লিনি' বলা হয়।
14. জ্যোতির্বিদ হিসেবে দ্বিতীয় ভাস্করের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করো।
উত্তর:-
> দ্বাদশ শতাব্দীর ভারতের এক খ্যাতনামা জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন দ্বিতীয় ভাস্কর।
★ অবদান:
(1) ভাস্কর গ্রহের গতি পরিমাপ করেছিলেন। ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাসের মূলনীতিকে ব্যবহার করে।
② তিনি প্রথম ভারতীয় হিসেবে সময়কে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাগে ভাগ করেছিলেন। তিনি 1 সেকেন্ডকে 34000 ভাগে ভাগ করেছিলেন।
(3) ত্রিকোণমিতির প্রতি ডিগ্রি 2 সাইন, কোসাইনের মান নির্ণয় করেছিলেন এবং তা সারণি আকারে প্রকাশ করেছিলেন।
(4) এ ছাড়া তিনি তরলের পৃষ্ঠটান (Surface tension) ধর্মের ওপর আলোকপাত করেছিলেন। তাঁকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য 1981 খ্রিস্টাব্দের 20 নভেম্বর ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ISRO) মহাকাশে যে কৃত্রিম উপগ্রহটি উৎক্ষেপণ করেছিল; তার নাম দেয় দ্বিতীয় ভাস্কর।
15. জ্যোতির্বিজ্ঞানচর্চায় কোপার্নিকাসের অবদান কী ছিল?
অথবা,
কোপার্নিকাসকে কেন 'আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের জনক' বলা হয়?
উত্তর:-
▶ কোপার্নিকাস ছিলেন একজন পোলিস জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তিনি তাঁর পর্যবেক্ষণ দ্বারা বিশ্বব্রহ্মান্ডের গঠনতন্ত্র সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেন। খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতকে নিকোলাস
কোপার্নিকাস On the Revolutions of the Celestial Spheres নামক গ্রন্থটি রচনা করেন। এই গ্রন্থটি ছ-টি খন্ডে বিভক্ত। কোপার্নিকাস প্রবর্তিত সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তত্ত্বে বলা হয়েছে যে,
① মহাবিশ্বের কেন্দ্র বলে কিছু নেই, পৃথিবীর কেন্দ্র মহাবিশ্বের কেন্দ্র নয়।
(2) প্রতিটি গ্রহ ও উপগ্রহের মধ্যবিন্দু হল সূর্য। সূর্যকেই কেন্দ্র করে পৃথিবী ও তার অন্যান্য উপগ্রহগুলি (যেমন-চাঁদ) তাদের নির্দিষ্ট কক্ষপথে উপবৃত্তাকারে প্রদক্ষিণ করে।
(3) তিনি আরও বলেন যে, শুক্র (Venus) ও মঙ্গলগ্রহ (Mars)-এর কক্ষপথের মাঝখানে অবস্থান করে পৃথিবী ও তার কক্ষপথ। এসব কারণে তাঁকে 'আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের জনক' বলা হয়।
16. জ্যোতির্বিজ্ঞানচর্চায় টাইকোব্রাহের অবদান কী ছিল?
উত্তর:-
> টাইকোব্রাহে ছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর ইউরোপের এক খ্যাতনামা জ্যোতির্বিজ্ঞানী। 1573 খ্রিস্টাব্দে তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ দে স্তেলা নোভা প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে
(1) তিনি অ্যারিস্টটলের তত্ত্বকে (স্থির ও অপরিবর্তনীয় গোলকের ধারণা) অস্বীকার করেন।
(2) 1572 খ্রিস্টাব্দে তিনি খালি চোখে এক নিখুঁত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নবতারা (New Nova) নামে একটি নতুন নক্ষত্রের ধারণা দেন, যা পৃথিবী ও চাঁদের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে। সেটি ছিল সৌরজগতের অন্যান্য নক্ষত্রদের তুলনায় খুবই উজ্জ্বল, যা বর্তমানে সুপারনোভা নামে পরিচিত।
(3) এ ছাড়া তিনি ধূমকেতু বিষয়েও স্পষ্ট ধারণা দেন। এ বিষয়ে তিনি বলেন যে, ধূমকেতুর অবস্থান চাঁদের বাইরে রয়েছে।
(4) তিনি অ্যারিস্টট্ল ও টলেমির তত্ত্বকে অস্বীকার করে বিশ্বব্রহ্মান্ডের গঠন সম্পর্কে এক নতুন মতবাদ প্রচার করেন। তিনি বলেন, “পৃথিবী ছাড়া অন্যান্য গ্রহগুলি সূর্যকে কেন্দ্র করে অবিরাম প্রদক্ষিণ করে চলেছে এবং সূর্য-সহ অন্যান্য ঘূর্ণায়মান গ্রহগুলি পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে।"
17. জ্যোতির্বিদ্যাচর্চায় জোহানেস কেপলারের অবদান কী?
উত্তর:-
▶ কেপলার ছিলেন একজন জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী। জ্যোতির্বিদ্যাচর্চার জন্য তিনি একটি উন্নতমানের দূরবিন তৈরি করেন, যাকে বলা হয় 'কেপলারীয় দূরবিন'। 1596 খ্রিস্টাব্দে কেপলার জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক প্রথম মিস্তেরিয়াম কসমোগ্রাফিকাম নামক গ্রন্থটি প্রকাশ করে ইউরোপে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন। 1609 থেকে 1619 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কেপলার গ্রহের গতি নিয়ে তিনটি সূত্র প্রচার করেন।
কেপলার একটি নতুন গ্রহের সন্ধান দিয়েছিলেন। যেটি প্রায় পৃথিবীর সমান আয়তনবিশিষ্ট এবং যা পৃথিবী থেকে প্রায় 1,206 আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। এই গ্রহটিকে NASA-র বিজ্ঞানীরা 2015 খ্রিস্টাব্দে কেপলার মহাকাশযান পাঠিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানচর্চার আঙিনায় হাজির করেছেন। এর নাম দেওয়া হয়েছে কেপলার-442B |
18. সমুদ্র অভিযাত্রী বার্থেলোমিউ দিয়াজের কৃতিত্ব আলোচনা করো।
উত্তর:-
▶ বার্থেলোমিউ দিয়াজ ছিলেন একজন পোর্তুগিজ নাবিক। তিনি পোর্তুগালের রাজা দ্বিতীয় জনের নির্দেশে 1486 খ্রিস্টাব্দে লিসবন থেকে সমুদ্র অভিযান শুরু করেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষে আসার জলপথ আবিষ্কার করা। দিয়াজ তিনটি জাহাজ নিয়ে অভিযান শুরু করেন। 1486 খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে তিনি যথাক্রমে সেন্ট বারবারার ভূমি, ওয়ালভিস উপসাগর ও সেন্ট স্টিফেন উপসাগরে পৌঁছেছিলেন। এরপর তিনি 1488 খ্রিস্টাব্দে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ধরে আফ্রিকার দক্ষিণতম প্রান্তে পৌঁছান। এখানে তিনি প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির মুখে পড়ে আর এগিয়ে যেতে পারেননি। তিনি সমুদ্রের উত্তাল রূপ দেখে এই অঞ্চলের নাম দেন ঝড়ের অন্তরীপ (Cape of Storm)। আশাবাদী পোর্তুগালের রাজা দ্বিতীয় জন অনুভব করেছিলেন যে, এই পথ দিয়েই ভারতবর্ষে ও প্রাচ্যের অন্যান্য অঞ্চলে পৌঁছোনো যাবে। তাই তিনি এই অন্তরীপের নাম দেন উত্তমাশা অন্তরীপ (Cape of Good Hope) ।
19. ভাস্কো-দা-গামা কীভাবে ভারতে আসেন তা আলোচনা করো।
উত্তর:-
> ভাস্কো-দা-গামা ছিলেন একজন পোর্তুগিজ নাবিক। 1497 খ্রিস্টাব্দে তিনি Cape of Good Hope বা উত্তমাশা অন্তরীপ পেরিয়ে আফ্রিকার পূর্ব উপকূল ধরে উত্তর দিকে এগিয়ে যান এবং মালিন্দি নামক স্থানে পৌঁছোন। সেখান থেকে তিনি ইবন মাহির নামে এক আরব নাবিকের সাহায্যে 1498 খ্রিস্টাব্দের 20 মে ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের কালিকট বন্দরে গিয়ে উপস্থিত হন। কিন্তু কালিকটের রাজা জামোরিনের সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দেওয়ায় তিনি নিজ দেশে ফিরে যান। 1502 খ্রিস্টাব্দে তিনি দ্বিতীয়বারের জন্য সমুদ্রপথে কালিকটে উপস্থিত হন। তিনিই প্রথম সমুদ্রপথে ভারতবর্ষে আসার জলপথ আবিষ্কার করেন। তাঁর মাধ্যমেই ভারতবর্ষে পোর্তুগিজ বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হয় ও তারা ব্যাবসাবাণিজ্য শুরু করেন।
20. সমুদ্র অভিযাত্রী হিসেবে কেব্রালের কৃতিত্ব নিরূপণ করো।
উত্তর:-
▶ পেড্রো আলভারেজ কেব্রাল ছিলেন একজন দুঃসাহসী পোর্তুগিজ নাবিক। তিনি 1500 খ্রিস্টাব্দে 13টি পালতোলা জাহাজ নিয়ে লিসবন বন্দর থেকে নৌ-অভিযান করেন। আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে তিনি দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর-পূর্ব উপকূলে উপনীত হন এবং ওই অঞ্চলের ওপর পোর্তুগালের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই অঞ্চলের নাম দেন 'Ilha da Vera Cruz' বা 'Island of the True Cross'। পরে এই অঞ্চলের নাম হয় ব্রাজিল। এরপর তিনি ওই বছর 13 সেপ্টেম্বর ভারতের কালিকট বন্দরে উপনীত হন। এখানে তিনি পোর্তুগিজ বাণিজ্যকুঠি নির্মাণ করেন। এরপর 1501 খ্রিস্টাব্দের 23 জুন তিনি ভারত থেকে প্রচুর মশলাপাতি নিয়ে পোর্তুগালে ফিরে আসেন। প্রত্যাবর্তনকালে 13 টি জাহাজের মধ্যে 6টি জাহাজের অস্তিত্ব ছিল।
21. কলম্বাস কীভাবে আমেরিকা আবিষ্কার করেন?
উত্তর:-
▶ ইতালীয় নাবিক ক্রিস্টোফার কলম্বাস স্পেনের রাজা ফার্দিনান্দ ও রানি ইসাবেলার সাহায্যে ভারতবর্ষে পৌঁছাবার জলপথ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। 1492 খ্রিস্টাব্দে তিনি তিনটি ছোটো ছোটো জাহাজ (যথা-সান্তা মারিয়া, পিন্তা ও নিনা) নিয়ে পালোস বন্দর থেকে আটলান্টিক মহাসাগরের বুকে যাত্রা শুরু করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল প্রাচ্য দেশে পৌঁছানো। কিন্তু শেষপর্যন্ত তিনি বাহামা দ্বীপপুঞ্জের একটি দ্বীপ সান-সালভাদোর দ্বীপে পৌঁছান। তাঁর বিশ্বাস ছিল তিনি ভারতের উপকূলে পৌঁছেছেন। তাই তিনি এই অঞ্চলের নাম দেন ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ বা ইন্ডিজ এবং এখানকার মানুষের গায়ের রং তামাটে লাল দেখে তাঁদের নাম দেন রেড ইন্ডিয়ান। একারণে আমেরিকার আদি বাসিন্দারা 'রেড ইন্ডিয়ান' নামে খ্যাত। আসলে তিনি জানতেন না যে, তাঁর এই অভিযানে এক নতুন মহাদেশ আবিষ্কৃত হয়েছে। জীবনের অন্তিমকাল পর্যন্ত তাঁর বিশ্বাস ছিল তিনি ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেছেন, যে দ্বীপপুঞ্জগুলি পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ নামে পরিচিত।
22. সমুদ্র অভিযাত্রী হিসেবে আমেরিগো ভেসপুচির কৃতিত্ব নিরূপণ করো।
অথবা,
আমেরিগো ভেসপুচি কীভাবে কোন্ কোন্ দেশ আবিষ্কার করেন?
উত্তর:-
▶ আমেরিগো ভেসপুচি ছিলেন একজন ইতালীয় নাবিক। তিনি প্রথমে স্পেন ও পরে পোর্তুগালের হয়ে সমুদ্র অভিযান করেন।
① প্রথম অভিযান:
1497-1498 খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তিনি ইউকাটান (Yucatan, যা ক্যারিবিয়ান সাগর ও মেক্সিকো উপসাগরের মাঝখানে অবস্থিত) উপদ্বীপ ও হন্ডুরাসে পৌঁছান।
② দ্বিতীয় অভিযান:
1499 খ্রিস্টাব্দে তিনি স্পেনের হয়ে তাঁর দ্বিতীয় অভিযান করেন। এই অভিযান দ্বারা তিনি গায়ানা উপকূলে পৌঁছাতে সক্ষম হন।
③ তৃতীয় ও চতুর্থ অভিযান:
1501 খ্রিস্টাব্দে তিনি পোর্তুগালের হয়ে তৃতীয়বার সমুদ্র অভিযান করেন। সেই বার তিনি দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিলের উপকূলে পৌঁছোন। তিনি ঘোষণা করেন যে, এই স্থানটি একটি নতুন মহাদেশের অন্তর্গত। 1503 খ্রিস্টাব্দে চতুর্থবার তিনি পুনরায় ব্রাজিল যান। তিনি ক্রিস্টোফার কলম্বাস আবিষ্কৃত মহাদেশটির নাম দেন 'Mundus Novus' অর্থাৎ, New World বা নতুন বিশ্ব। 1507 খ্রিস্টাব্দে তাঁর নামানুসারে নতুন আবিষ্কৃত মহাদেশ দুটির (উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা) নাম হয় আমেরিকা। তাঁর লেখা Cosmographiae introductio নামে একটি ভৌগোলিক অভিযানমূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাঁর এই সাফল্যের জন্য তিনি স্পেনরাজের নিকট 'মহানাবিক'- এর মর্যাদা লাভ করেন।
23. ম্যাগেলান স্মরণীয় কেন?
উত্তর:-
> ম্যাগেলান ছিলেন একজন পোর্তুগিজ নাবিক। 1519 খ্রিস্টাব্দে তিনি 5টি জাহাজ নিয়ে ও 270 জন সহযাত্রী নিয়ে স্পেনের আন্দালুসিয়ান বন্দর থেকে মশলা দ্বীপের (ইন্দোনেশিয়া, মলুকাস) উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ক্রমাগত তিনি একই দিকে যাত্রা করে আটলান্টিক মহাসাগর পার করে 'এক নতুন' সাগরে উপনীত হন। এই সাগরের শান্ত রূপ দেখে তিনি এর নাম দেন প্রশান্ত মহাসাগর (Pacific Ocean)। এরপর তিনি প্রশান্ত মহাসাগর পেরিয়ে আরও পশ্চিমে যাত্রা করে একটি দ্বীপে এসে পৌঁছোন। স্পেনের রাজপুত্র ফিলিপের নাম অনুসারে এই দ্বীপের নাম হয় 30 ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ (1521 খ্রিস্টাব্দ)। সেখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে ম্যাকটানের যুদ্ধে তাঁর মৃত্যু হয়।
তাঁরই একটি জাহাজ ভিক্টোরিয়া 18 জন নাবিক নিয়ে ভারত মহাসাগর পেরিয়ে আফ্রিকা ঘুরে স্পেনে ফিরে আসে (1522 খ্রিস্টাব্দ)। এইভাবে ভিক্টোরিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। এর ফলে প্রমাণিত হয় পৃথিবী গোলাকার।
24. টীকা লেখো: ম্যারিনারস কম্পাস।
উত্তর:-
▶ 'কম্পাস' শব্দটি এসেছে প্রাচীন ফরাসি শব্দ Compas থেকে। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যে কম্পাস আবিষ্কৃত হয়। দিকনির্ণয় যন্ত্র হিসেবে এটি সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়। 700-1100 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে চিনে সর্বপ্রথম নাবিকদের প্রয়োজনে তৈরি হয় এই কম্পাস। ইউরোপে সামুদ্রিক অভিযানের সময় দিকনির্ণয়ের জন্য এক ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, যা নৌ-কম্পাস (Mariner's Compass) নামে পরিচিত। এই কম্পাসে থাকে একটি চুম্বক শলাকা, যেটি একটি গোলাকার পিতলের কাঠামোর ওপর লাগানো থাকে এবং ঘুরতে পারে। গোলাকৃতি কাঠামোর ব্যাসার্ধটি কম্পাস রোজ নামে পরিচিত। যখন এটি ভূপৃষ্ঠের সমান্তরালে রাখা হয়, তখন শলাকাটির তির সর্বদা উত্তর দিক নির্দেশ করে।
25. জমি ঘেরাও আন্দোলন (এনক্লোজার মুভমেন্ট) বলতে কী বোঝো?
উত্তর:-
▶ ষোড়শ-অষ্টাদশ শতকের মধ্যে ইংল্যান্ডের ধনী কৃষকরা গ্রামের সর্বসাধারণের ব্যবহৃত ছোটোবড়ো জমিগুলিকে একত্রিত করে। তাতে বেড়া দিয়ে তার সীমানা নির্দিষ্ট করার যে প্রক্রিয়া শুরু করে তাকেই বলা হয় জমি ঘেরাও আন্দোলন বা বেষ্টনী আন্দোলন। টিউডর যুগে (1485-1603 খ্রিস্টাব্দ) এই আন্দোলন চরম আকার ধারণ করেছিল। একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, 1750-1805 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইংল্যান্ডে প্রায় 60 লক্ষ একর জমি ঘেরাও হয়েছিল। এর ফলে একদিকে যেমন জমি বা কৃষিতে ব্যাপক বিনিয়োগ শুরু হয়েছিল, তেমনি ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল।
26. কোন্ সময়কে কেন ইউরোপের 'সামরিক বিপ্লবের যুগ' বলা হয়?
উত্তর:-
▶ পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের মধ্যে ইউরোপে বারুদের প্রচলন ঘটে। এই বারুদকে তারা বন্দুক, কামান ইত্যাদির ইন্ধন হিসেবে ব্যবহার করা শুরু করে। এই সমরাস্ত্রগুলি খুব দ্রুত সামরিক বাহিনীর হাতে চলে যায়, যা ব্যবহার করে ইউরোপের শক্তিশালী রাজারা দারুণ সাফল্য পায়। এই সমরাস্ত্রগুলির তালিকায় ছিল-
① বন্দুক,
② হারকুইবাস জাতীয় বন্দুক,
③ কামান,
④ মাস্কেট বা গাদা বন্দুক। এসব কারণে এই সময়কে বলা হয় ইউরোপের 'সামরিক বিপ্লবের যুগ'।
27. 'ট্রেস ইতালিয়েন' কী?
উত্তর:-
▶ 1453 খ্রিস্টাব্দে অটোমান তুর্কি সেনাবাহিনী পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্ট্যান্টিনোপল আক্রমণ করে। তুর্কি গোলন্দাজ বাহিনীর লাগাতার গোলাবর্ষণে কনস্ট্যান্টিনোপলের দুর্গের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। শেষপর্যন্ত এই দুর্গের তথা পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয়। এর থেকে শিক্ষা নিয়ে ইতালীয় স্থপতিরা মজবুত দুর্গ নির্মাণ করার চিন্তাভাবনা শুরু করে দেন। এর ফলশ্রুতি হিসেবে কামানের গোলা প্রতিরোধক এক ধরনের দুর্গ গড়ে ওঠে। এগুলিকে বলা হত ট্রেস ইতালিয়েন (Trace Italienne) । এই দুর্গ নির্মাণ রীতির প্রচলন হয় মূলত উত্তর ইটালিতে। এর মূল উপকরণ ছিল এবড়ো-খেবড়ো বা খাঁজওয়ালা পাথর খন্ড। এর উল্লেখ পাওয়া যায় ইতালীয় স্থপতি আলবার্তির লেখা On the Art of Building গ্রন্থে। পরে এই দুর্গস্থাপত্যরীতি সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। সপ্তদশ শতকে ফ্রান্সে প্রথম সুরক্ষিত দুর্গ তৈরি শুরু করেন ভবাঁ। এ ধরনের দুর্গ অবরোধের সময় শত্রুপক্ষের প্রচুর সময়, নানা উপকরণ ও লোকবলের প্রয়োজন হত।
নতুন তৈরি দুর্গগুলি ছিল আরও বেশি উন্নত ও সুরক্ষিত। দুর্গের দেয়ালে ছিল নতুন ধরনের আক্রমণের জায়গা। টাওয়ার বা চূড়া অংশের নীচে দুর্গের দেয়ালের পাশে প্রতিপক্ষের ওপর অনায়াসে আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করা হত। 1480 খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এ ধরনের দুর্গ নির্মাণ প্রথম দেখা গেলেও 1494 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইটালিতে এই ধরনের দুর্গ ব্যবহার শুরু হয়।
মান্ডুয়া এবং কাসাল শহর দুটি সবথেকে বড়ো দুর্গশহরে পরিণত হয়। তিরের ফলার মতো কোনাচে গম্বুজওয়ালা দুর্গ ক্রমশ হ্যাপসবার্গ, বুরবোঁ রাজ্যের সীমান্তে এবং নেদারল্যান্ড, দানিয়ুব উপত্যকায় ও জার্মানিতে ছড়িয়ে পড়ে।
28. ইউরোপের সামরিক বিপ্লবের ফল কী হয়েছিল?
উত্তর:-
▶ ইউরোপের সামরিক বিপ্লবের এক সুদূরপ্রসারী ফলাফল দেখা দিয়েছিল রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে। এর ফলে ইউরোপে
(1) এক নতুন সার্বভৌম ও সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল। এগুলি আবার শাসকদেরও বিশেষভাবে সহায়ক হয়ে উঠেছিল। ফলে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং সাম্রাজ্য বিস্তারের পথ সুগম হয়ে উঠেছিল।
(2) মধ্যযুগের যুদ্ধরীতি অচল হয়ে যাওয়ার ফলে নাইটদের কাহিনি উপকথায় পরিণত হয়ে গিয়েছিল। নতুন পদ্ধতিতে শিভ্যালরির কোনো স্থান ছিল না। এর বদলে রণকৌশলে প্রশিক্ষণ ও আগ্নেয়াস্ত্রই প্রাধান্য পেল।
(3) নতুন আমলাতন্ত্রের ওপর ভর করে এক স্থায়ী সেনাবাহিনীর ওপর নির্ভরশীল রাষ্ট্র গড়ে ওঠে।
ঐতিহাসিক ম্যাকনিল, কালিন জোনস, মাইকেল ডুফি এই সামরিক উন্নতির সঙ্গে আধুনিক রাষ্ট্রের উদ্ভব, আমলাতন্ত্রের সৃষ্টি ও সামরিক পেশাদারিত্ব শুরু হওয়া সম্পর্কে নানা দিক তুলে ধরেন। জেরেমি ব্ল্যাক সামরিক বিপ্লবকে একটি ফল হিসেবেই মনে করেছেন। অনেকের মত যে, সামরিক উন্নতির ফলেই অটোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় স্পেনের সাফল্য ও ভারত মহাসাগর এলাকায় পোর্তুগালের সাফল্যও এসেছিল এই কারণেই।
29. ইউরোপে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে নির্মিত জাহাজগুলির গঠনগত বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।
উত্তর:-
> 15-16 শতকে উন্নত জাহাজ নির্মাণের জন্য নৌ-শিল্পীরা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা শুরু করে। এগুলির গঠনগত বৈশিষ্ট্য ছিল
(1) জাহাজগুলি দ্রুতগামী করার জন্য রাখা হত 1-4টি মাস্কুল ও একাধিক মোটা কাপড়ের পাল।
(2) জাহাজগুলি হত মজবুত এবং দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে অনেক দীর্ঘ হত, যাতে অধিক সংখ্যক রসদ, সেনাবাহিনী, গোলাবারুদ ইত্যাদি রাখা যায়।
(3) দিক নির্ণয় ও অন্যান্য সুবিধার জন্য জাহাজগুলিতে রাখা হত কম্পাস, উচ্চতা- মাপক যন্ত্র, অ্যাস্ট্রোল্যাব, মানচিত্র, চার্ট ইত্যাদি।
30. কাকে কেন 'আধুনিক মুদ্রণযন্ত্রের জনক' বলা হয়?
উত্তর:-
> নবজাগরণের যুগে ইউরোপে জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে আধুনিক মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার ছিল এক যুগান্তকারী অধ্যায় জার্মান স্বর্ণকার জোহানেস গুটেনবার্গ 1439 খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। জার্মানির স্ট্রাসবুর্গ শহরে মুদ্রণযন্ত্র নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। এরপর 1448 খ্রিস্টাব্দে তিনি তাঁর জন্মস্থান মেইন্ঞ্জ শহরে ফিরে আসেন এবং সেখানে একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে বই ছাপার জন্য তিনি কাঠের ব্লকের হরফ ব্যবহার করেন। এরপর 1450 খ্রিস্টাব্দে তিনি চলমান ধাতব অক্ষরের মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কার করেন। এজন্য তাঁকে বলা হয় 'আধুনিক মুদ্রণযন্ত্রের জনক'। এই মুদ্রণযন্ত্র দিয়েই তিনি 1455 খ্রিস্টাব্দে লাতিন ভাষায় বাইবেল (যার প্রতি পৃষ্ঠায় 42টি করে লাইন) প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থটিকে বলা হয় গুটেনবার্গ বাইবেল।
31. আধুনিক মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কারের সঙ্গে ইউরোপের আঞ্চলিক ভাষার উন্নতির সম্পর্ক কী?
উত্তর:-
▶ মধ্যযুগীয় ইউরোপে সাহিত্যচর্চার একমাত্র মাধ্যম ছিল লাতিন ভাষা। 1500 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপে মুদ্রিত বইগুলির 77% ছিল লাতিন ভাষায় লিখিত। কিন্তু ইউরোপে কাগজশিল্প তথা মুদ্রণশিল্পের অভাবনীয় উন্নতি হলে সেই ধারার বদল হয়। ফলে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় সাহিত্যচর্চা শুরু হয়। ইটালিতে পেত্রার্ক, দান্তে, বোকাচ্চিয়ো প্রমুখ ছিলেন সেই ধারার দিশারি। এ প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ উল্লেখ্য যে, ইউরোপে মুদ্রণ বিপ্লবের পর জার্মান ভাষায় 11টি, ইটালিয়ান ভাষায় 4টি, ফরাসি ভাষায় 1টি ও স্প্যানিশ ভাষায় 1টি করে বাইবেল ছাপা হয়। 1455 খ্রিস্টাব্দে গুটেনবার্গ লাতিন ভাষায় পবিত্র বাইবেল গ্রন্থটি প্রকাশ করেছিলেন। এইভাবে মুদ্রিত বইপত্রগুলি বিভিন্ন ভাষায় লিখিত রূপ নিতে শুরু করে। ফলে আঞ্চলিক ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।
32. আধুনিক মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে ইউরোপে কীভাবে শিক্ষার প্রসার ঘটেছিল বলে মনে হয়?
উত্তর:-
▶ মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পূর্বাবধি জ্ঞানপিপাসু মানুষ ও ছাত্রদের কাছে সহায়-সম্বল বলতে ছিল হাতে লেখা পুথি বা পাণ্ডুলিপি (Manuscript)। কিন্তু এই পুথির সংখ্যা ছিল যেমন কম, তেমনি ছিল মানুষের নাগালের বাইরে। তা ছাড়া এগুলির বেশিরভাগই ছিল ধর্মকেন্দ্রিক। 1440- এর দশকে জার্মনিতে আধুনিক মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হলে, ক্রমান্বয়ে পুস্তক মুদ্রিত হতে শুরু করে। এই পুস্তকগুলি ছিল যথেষ্ট উপযোগী। কারণ এগুলি ছাপতে যেমন কম সময় লাগত, তেমনি ছিল স্বল্পমূল্যের। তা ছাড়া মুদ্রিত পুস্তকগুলি হত নির্ভুল, সুপাঠ্য, সুন্দর ও দীর্ঘস্থায়ী। এসব কারণে এগুলি খুব দ্রুত সকলের বিশেষ করে জ্ঞানপিপাসু মানুষ ও ছাত্রদের মন জয় করে নেয়। স্বাভাবিকভাবেই মুদ্রণযন্ত্রের হাত ধরে ইউরোপে শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার ঘটে। এর ব্যতিক্রম ছিল না ভারতবর্ষ ।
| একাদশ শ্রেণীর ইতিহাস এর দ্বিতীয় সেমিস্টারের সকল অধ্যায় ও প্রশ্নোত্তর |
|---|
| অধ্যায় ৪ - রাষ্ট্রের প্রকৃতি, রাষ্ট্রচিন্তা ও প্রতিষ্ঠান (Nature of the State and Its Apparatus) |
| অধ্যায় ৫ - পরিবর্তনশীল ঐতিহ্য (Changing Traditions) |
| অধ্যায় ৬ - বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিস্তৃত দিগন্ত (Expanding Horizons of Science and Technology) |
| একাদশ শ্রেণীর ইতিহাস এর দ্বিতীয় সেমিস্টারের সিলেবাস |
| Mock Test |
| Coming Soon |
| Coming Soon |