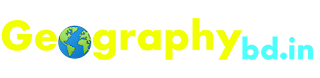ধ্বনি ও বর্ণ | বাংলা ব্যাকারণ | Dhwani o barna | ধ্বনির বৈশিষ্ট্য | বর্ণের বৈশিষ্ট্য
আজকে আমরা আলোচনা করবো ধ্বনি ও বর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে । এই ধ্বনি ও বর্ণ বিষয়ক প্রশ্নটি পরীক্ষার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ তাই ধ্বনি ও বর্ণ বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবো। আমরা এই লিখাটির মাধ্যমে তোমাদের কে খুব সহজ ভাষায় ধ্বনি ও বর্ণ বিষয়ের প্রশ্নটির গুরুত্বপূর্ণ অংশ সমুহ এখানে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছি।
ধ্বনির সংজ্ঞা | ধ্বনি কাকে বলে
ভাষার মূলগত উপাদান হল ধ্বনি। মানুষ তার মনের ভাবকে কিছু সাংকেতিক আওয়াজের সাহায্যে প্রকাশ করে। এই সাংকেতিক আওয়াজগুলি বিভিন্ন সমন্বয়ে মিলিত হয়ে অর্থবহ সমষ্টি গড়ে তোলে। ভাষায় ব্যবহৃত ঐ আওয়াজগুলি সৃষ্টি হয় মানুষের বাগ্যন্ত্রে। এই আওয়াজগুলি ব্যাকরণে ধ্বনি নামে পরিচিত। সাধারণ ব্যবহারিক জীবনে যে কোনো আওয়াজকেই ধ্বনি বলে। কিন্তু ব্যাকরণে ধ্বনি কাকে বলে? "ভাব প্রকাশের উদ্দেশ্যে মানুষের বাগযন্ত্র থেকে নিঃসৃত সাংকেতিক আওয়াজকে ধ্বনি বলে।" মনে রাখতে হবে ভাষার ধ্বনি তখনই সার্থক হয় যখন তা একক ভাবে বা ধ্বনিগুচ্ছ আকারে কোনো ভাব বা সংকেত বহন করে।
অথবা অন্যভাবে আমরা এই ভাবে বলতে পারি যে,
যেকোনো শব্দকে বা আওয়াজকে ধ্বনি বলা হয়। কিন্তু ব্যাকরণের আলোচনায়, মানুষের বাগযন্ত্র থেকে যে শব্দ বা আওয়াজ (Sound) বের হয় তাকে ধ্বনি বলা হয়। ধ্বনির লিখিত রূপকে বলা হয় বর্ণ। সুতরাং, ধ্বনি আর বর্ণের মধ্যে পার্থক্য এটুকুই যে, ধ্বনি হল উচ্চারিত আর বর্ণ লিখিত। ধ্বনির উৎপত্তি যেহেতু বাকযন্ত্রে, তাই দেখে নেওয়া যাক বাকযন্ত্র বলতে কী বোঝায়?
ধ্বনির বৈশিষ্ট্য
১: ধ্বনি উচ্চারিত হবে স্বেচ্ছায়।
২: ধ্বনি উচ্চারিত হবে ভাব প্রকাশের উদ্দেশ্যে।
৩: ধ্বনি হবে মানুষের বাগ্যন্ত্র থেকে সৃষ্ট।
বিভাজ্য ধ্বনি ও অবিভাজ্য ধ্বনি
ধ্বনিকে প্রাথমিক ভাবে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়।
১: বিভাজ্য ধ্বনি ও
২: অবিভাজ্য ধ্বনি।
ধ্বনির প্রকারভেদ
ধ্বনি প্রধানত দুই রকমের।
যথাঃ স্বরধ্বনি (Vowels) এবং
ব্যঞ্জনধ্বনি (Consonant)। এই দুই প্রকার ধ্বনির আবার উচ্চারণস্থান এবং উচ্চারণরীতি অনুসারে অনেকগুলি ভাগ রয়েছে। নীচে দুই প্রকার ধ্বনি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।
স্বরধ্বনি সংজ্ঞা । স্বরধ্বনি কাকে বলে
যে ধ্বনিগুলি উচ্চারণকালে বিশেষ বাধা পায় না এবং উচ্চারণে স্বনির্ভর, তাদেরকে স্বরধ্বনি বলা হয়। বাংলা স্বরধ্বনির সংখ্যা এগারোটি। ‘ঌ’ ধ্বনি এবং বর্ণের ব্যবহার বাংলাতে নেই। তাছাড়া, ‘ঋ’ ধ্বনির উচ্চারণ ‘রি’-এর মত। এদেরকে বাদ দিলে বাংলা স্বরধ্বনির সংখ্যা দশ।
স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ
স্বরধ্বনিকে গঠন, উচ্চারণ স্থান, উচ্চারণকাল, উচ্চারণ-প্রকৃতি প্রভৃতি দিক থেকে নানা ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথমেই দেখে নেওয়া যাক উচ্চারনের সময় অনুসারে স্বরধ্বনির বিভাজন।
হ্রস্বস্বর ও দীর্ঘস্বর– উচ্চারণের সময় অনুযায়ী স্বরধ্বনিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেসকল স্বরধ্বনি উচ্চারণ করতে কম সময় লাগে তাদেরকে বলা হয় হ্রস্বস্বর। অ, ই এবং উ হল হ্রস্বস্বর। যে স্বরধ্বনিগুলি উচ্চারণ করতে বেশি সময় লাগে তাদেরকে বলা হয় দীর্ঘস্বর। যেমন- আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ।
এবার আমরা জানবো গঠনগত দিক থেকে স্বরধ্বনিকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করি, যথা
ক) মৌলিক স্বরধ্বনি
খ) অর্ধস্বর ধ্বনি
গ) যৌগিক স্বরধ্বনি
গঠনগত দিক থেকে স্বরধ্বনিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। সেগুলি হল-
ক) মৌলিক স্বরধ্বনি– যে স্বরধ্বনিগুলি অবিভাজ্য তাদেরকে বলা হয় মৌলিক স্বরধ্বনি। বাংলায় মৌলিক স্বরধ্বনির সংখ্যা সাত। সেগুলি হল- অ, আ, ই, উ, এ, ও এবং অ্যা। এদের মধ্যে ‘অ্যা’ ধ্বনিটির নিজস্ব কোনো চিহ্ন নেই কিন্তু বাংলা ভাষায় এই ধ্বনিটির প্রচলন অনেক বেশি। যেমন- আমরা কেউ ‘এক’ বলি না, বলি- ‘অ্যাক’। তেমনি, দেখ> দ্যাখ ইত্যাদি অনেক শব্দ উচ্চারণ করার সময় ‘এ’ না বলে ‘অ্যা’ উচ্চারণ করা হয়।
খ) অর্ধস্বর– পাশাপাশি অবস্থিত দুটি শব্দ মৌলিক স্বরধ্বনির দ্বিতীয়টি যদি স্পষ্টভাবে উচ্চারিত না হয়, তবে তাকে অর্ধস্বর বলা হয়। এই অর্ধস্বরগুলি এককভাবে দল গঠন করতে পারে না। যেমন- বই শব্দটিতে রয়েছে ব, অ, ই। অ এবং ই উভয়েই মৌলিক স্বরধ্বনি কিন্তু ই-এর উচ্চারণ নির্ভর করছে ‘অ’- এর উপর- অই। অ ধ্বনিটি স্পষ্ট কিন্তু ‘ই’ ধ্বনিটি অস্ফুটরূপে উচ্চারিত হচ্ছে। এখানে ‘ই’ হল অর্ধস্বর।
গ) যৌগিক স্বরধ্বনি– যে স্বরধ্বনিগুলি বিভাজ্য তাদেরকে যৌগিক স্বরধ্বনি বলা হয়। একটি মৌলিক স্বরধ্বনি এবং একটি অর্ধস্বর একসাথে উচ্চারিত হলে তাকে যৌগিক স্বরধ্বনি বলা হয়। যেমন- ঐ (অ+ই), ঔ (অ+উ)। ঐ এবং ঔ এই দুটি যৌগিক স্বরধ্বনির নিজস্ব চিহ্ন রয়েছে কিন্তু বাংলায় মোট ২৫টি যৌগিক স্বরধ্বনির সন্ধান দিয়েছেন আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। এরকম কয়েকটি যৌগিক স্বরধ্বনি হল- ইই, ইউ, ইআ, এও, এউ, অ্যাও, উই, ওয় ইত্যাদি।
এছাড়াও স্বরধ্বনির একটি বিশেষ রূপভেদ হল প্লুতস্বর। গান গাওয়ার সময় বা কাউকে সম্বোধন করার সময় কোনো কোনো স্বরধ্বনিকে টেনে টেনে বা দীর্ঘায়িত করে উচ্চারণ করা হয়। এরূপ দীর্ঘায়িত স্বরধ্বনিকে বলা হয় প্লুতস্বর। যেমন- “আ-আ-আ-আমরা নূতন যৌবনেরই দূত”- এখানে ‘আ’ ধ্বনিটি প্লুতস্বর।
এবার দেখে নেওয়া যাক, মৌলিক স্বরধ্বনিগুলি উচ্চারণ করার সময় মুখ, জিহ্বা ও ঠোঁটের আকার বা অবস্থান কী রকম থাকে, সেই অনুযায়ী স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ।
ব্যঞ্জনধ্বনি সংজ্ঞা । ব্যঞ্জনধ্বনি কাকে বলে
যে ধ্বনিগুলি উচ্চারণকালে বাগযন্ত্রের বিভিন্ন স্থানে বাধা পায় এবং সেইজন্য কোনো স্বরধ্বনির সাহায্য নিয়ে উচ্চারিত হতে পারে তাদেরকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলা হয়। বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি হল- ক, খ্, গ্, ঘ্, ঙ্, চ্, ছ্, জ্, ঝ্, ঞ্, ট্, ঠ্, ড্, ঢ্, ণ্, ত্, থ্, দ্, ধ্, ন্, প্, ফ্, ব্, ভ্, ম্, য্, র্, ল্, শ্, ষ, স্, হ্, ড়, ঢ়, য়, ং এবং ঃ। এই ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলির মধ্যে অন্তঃস্থ-ব এর বাংলায় ব্যবহার নেই। ব্যঞ্জনধ্বনিগুলিকে উচ্চারণ স্থান এবং উচ্চারণ প্রকৃতি অনুসারে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়।
উচ্চারণ প্রকৃতি অনুসারে ব্যঞ্জনধ্বনির ভাগ
উচ্চারণ প্রকৃতি অনুসারে বাংলা ব্যঞ্জন ধ্বনিকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায়। আগে ভাগগুলি দেখে নেওয়া যাক তারপর সংজ্ঞা দেওয়া হবে।
(i) স্পর্শধ্বনি
(ii) উষ্ম ধ্বনি
(iii) অন্তঃস্থ ধ্বনি
(iv) নাসিক্য ধ্বনি
(v) অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ধ্বনি
(vi) ঘৃষ্টধ্বনি
(vii) দ্বিব্যঞ্জন ধ্বনি
(viii) ঘোষ ধ্বনি ও অঘোষ ধ্বনি
(ix) কম্পিত বর্ণ
(x) পার্শ্বিক ধ্বনি
(xi) তাড়িত ধ্বনি
(xii) অযোগবাহ ধ্বনি
(i) স্পর্শধ্বনি– ক থেকে ম পঁচিশটি ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণকালে জিহ্বা বাগযন্ত্রের কোন না কোন অংশকে স্পর্শ করে। তাই এদেরকে স্পর্শধ্বনি (Stops ) বলা হয়। এদের আবার পাঁচটি বর্গে বিভাজন করা হয় বলে এদেরকে বর্গীয় ধ্বনিও বলা হয়। প্রত্যেক বর্গের প্রথম ধ্বনি অনুযায়ী বর্গগুলির নামকরণ হয়েছে। যেমন-
ক-বর্গঃ- ক, খ, গ, ঘ, ঙ
চ-বর্গঃ- চ, ছ, জ, ঝ, ঞ
ট-বর্গঃ- ট, ঠ, ড, ঢ, ণ
ত-বর্গঃ- ত, থ, দ, ধ, ন
প-বর্গঃ- প, ফ, ব, ভ, ম।
(ii) উষ্ম ধ্বনি– শ, ষ, স, হ—এদের উচ্চারণকালে শ্বাসবায়ু শিসধ্বনির মতাে উষ্ণতা উৎপাদন করে নির্গত হয়। তাই এদেরকে উষ্মধ্বনি (Spirants) বলা হয়।
(iii) অন্তঃস্থ ধ্বনি– অন্তঃস্থ কথার অর্থ হল মধ্যবর্তী। য, র, ল, ব এই চারটি ধ্বনির অবস্থান স্পর্শধ্বনি ও উষ্মধ্বনির মাঝখানে বলে এদেরকে অন্তঃস্থ ধ্বনি বলা হয়।
(iv) নাসিক্য ধ্বনি– প্রত্যেক বর্গের পঞ্চম ধ্বনি যথাঃ ঙ, ঞ, ণ, ন, ম – এদের উচ্চারণকালে শ্বাসবায়ু কেবল মুখ দিয়ে না বেরিয়ে আংশিক নাসিকার মধ্য দিয়ে বার হয়। এজন্য এদেরকে অনুনাসিক বা নাসিক্য ধনি (Nasals) ধ্বনি বলা হয়।
(v) অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ধ্বনি– প্রাণ কথার অর্থ হল শ্বাসবায়ু। যে সকল ধ্বনি উচ্চারণ করার সময় অধিক শ্বাসবায়ু নির্গত হয় তাদেরকে বলা হয় মহাপ্রাণ (Aspirated) ধ্বনি। প্রত্যেক বর্গের দ্বিতীয় এবং চতুর্থ ধ্বনি (যথাঃ খ, ঘ, ছ, জ, ঝ, ঠ, ঢ, থ, দ, ধ, ফ, ব, ভ) হল মহাপ্রাণ ধ্বনি। যেসকল ধ্বনি উচ্চারণকালে অল্প পরিমাণ শ্বাসবায়ু নির্গত হয় তাদেরকে বলা হয় অল্পপ্রাণ (Unaspirated) ধ্বনি। প্রত্যেক বর্গের প্রথম ও তৃতীয় ধ্বনি ( যথাঃ ক, গ, চ, জ, ট, ড, ত, দ, প, ব) হল অল্পপ্রাণ ধ্বনি।
(vi) ঘৃষ্টধ্বনি– চ ও জ ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বার সঙ্গে তালুর ঘর্ষণ হয়। এজন্য এদেরকে ঘৃষ্টধ্বনি (Affricate) বলা হয়।
(vii) দ্বিব্যঞ্জন ধ্বনি– মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলিতে একটি অল্পপ্রাণ এবং ‘হ্’ ধ্বনি মিশে থাকে। যেমন- ক+হ= খ, গ+হ= ঘ ইত্যাদি। আবার, ঘৃষ্টধ্বনিগুলি উচ্চারণের শুরুতে স্পর্শধ্বনির মতো কিন্তু শেষে উষ্মধ্বনির মতো। যেমন- চ= ক্+শ্, জ্= গ্+শ্। এজন্য ঘৃষ্টধ্বনি এবং মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলিকে দ্বিব্যঞ্জন ধ্বনি বলা হয়।
(viii) ঘোষ ধ্বনি ও অঘোষ ধ্বনি– উচ্চারণকালে কয়েকটি ধ্বনিতে স্বরতন্ত্রীর কম্পনজাত সুর মিশে থাকে। একে ঘোষ বলা হয়। ঘোষ কথার অর্থ গাম্ভীর্য। বর্গের প্রথম এবং দ্বিতীয় ধ্বনি উচ্চারণকালে ঘোষ বা গাম্ভীর্য প্রকাশ পায় না। তাই এদেরকে অঘোষ (Unvoiced) ধ্বনি বলে। ক, খ ; চ, ছ; ট, ঠ; ত, থ; প, ফ অঘােষ ধনি। বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম ধ্বনিতে স্বরতন্ত্রীর কম্পনজাত সুর বা গাম্ভীর্য প্রকাশ পায়। এজন্য এদেরকে ঘোষ (Voiced) ধ্বনি বলা হয়। গ, ঘ, ঙ ; জ, ঝ, ঞ; ড, ঢ, ণ; দ, ধ, ন; ব, ভ, ম হল ঘোষ ধ্বনি।
(ix) কম্পিত বর্ণ : ‘র্’ ধ্বনিটি উচ্চারণ করার সময় জিহ্বাগ্র কম্পিত হয়। তাই ‘র্’ ধ্বনিটিকে কম্পিত বা কম্পনজাত ধ্বনি বলে।
(x) পার্শ্বিক ধ্বনি– ‘ল’ ধ্বনিটি উচ্চারণ করার সময় জিভ উল্টে গিয়ে শ্বাসবায়ু জিভের দু’পাশ দিয়ে বের হয়। এজন্য ‘ল’ ধ্বনিটিকে পার্শ্বিক ধ্বনি বলা হয়।
(xi) তাড়িত ধ্বনি: ‘ড়’ এবং ‘ঢ়’ ধ্বনিদুটি উচ্চারণের সময় জিহ্বা মূর্ধাকে তাড়িত করে। তাই এই দুটি ধ্বনিকে তাড়িত ধ্বনি বলে।
(xii) অযোগবাহ ধ্বনি: অনুস্বার ( ং ) ও বিসর্গ (ঃ)- এই দুটি ধ্বনি অন্য ধ্বনিকে আশ্রয় করে উচ্চারিত হয়, সেজন্য এদের আশ্রয়স্থানভাগী ধ্বনি বলে। অন্য ধ্বনির যোগ ছাড়া এদের ‘বাহ’ বা প্রয়োগ হয় না বলে এই দুটি ধ্বনিকে অযোগবাহ ধ্বনিও বলা হয়।
আমরা সাধারণ ধারণায় যেগুলিকে ধ্বনি বলি, অর্থাৎ অ,আ, ক, খ ইত্যাদি, এগুলি আসলে বিভাজ্য ধ্বনি। কারণ এই ধ্বনিগুলিকে যে কোনো সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত করা যায় এবং তাদের আবার আলাদা করে দেখানো যায়। যেমন: আকাশ = আ+ক্+আ+শ্+অ। অপর দিকে আমরা কথা বলার সময় যে বিশেষ বিশেষ সুর(যেমন প্রশ্ন করার একটা বিশেষ সুর আছে কিন্তু ওই একই কথা উত্তর হিসেবে বললে সুর পাল্টে যায়), তাল, কণ্ঠের ওঠাপড়া ইত্যাদি ব্যবহার করি, সেগুলি অবিভাজ্য ধ্বনি। একটা সহজ উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা অনেক স্পষ্ট হবে।
যদি বলা হয়--- "রাম যাবে।" তাহলে কথাটা যেমন শুনতে লাগবে, "রাম যাবে?" বললে তার চেয়ে অনেক আলাদা শোনায়। এই পার্থক্যটা গড়ে দিচ্ছে অবিভাজ্য ধ্বনি(এখানে সুর)। লক্ষ করলে দেখা যাবে বিভাজ্য ধ্বনিগুলো কিন্তু উভয় বাক্যে একই রকম আছে। অবিভাজ্য ধ্বনি মূলত চার প্রকার: সুরতরঙ্গ, যতি, দৈর্ঘ্য ও শ্বাসাঘাত। বিভাজ্য ধ্বনি দুই প্রকার: স্বর ও ব্যঞ্জন।
বর্ণ সংজ্ঞা । বর্ণ কাকে বলে
বর্ণ বলতে বোঝায় ধ্বনির লেখ্য রূপ। মনে রাখতে হবে, বর্ণ আসলে ধ্বনির একটি বিকল্পমাত্র। বর্ণের কাজ হল ধ্বনিকে স্হায়িত্ব দেওয়া। ধ্বনি আর বর্ণকে অনেকে অনেক সময় এক করে ফেলেন। বাস্তবে তা কিন্তু ভুল।
ধ্বনি ও বর্ণের পার্থক্য
- বর্ণ চোখে দেখার জিনিস আর ধ্বনি কানে শুনবার।
- ধ্বনি অস্থায়ী, বর্ণ স্থায়ী।
- ধ্বনিকে উচ্চারণ করতে হয়, বর্ণকে লিখতে হয়।
ব্যাকরণে ধ্বনির আলোচনাই গুরুত্বপূর্ণ, বর্ণের আলাদা আলোচনা প্রয়োজন নেই।
ভাষায় লিপি সম্পর্কে পড়াশোনা করতে হলে বর্ণ জানা প্রয়োজন। বাংলা বর্ণগুলি ধ্বনিমূলক বর্ণ। অর্থাৎ বাংলা বর্ণগুলির উচ্চারণ মোটামুটি সুনির্দিষ্ট। বাংলা ক্ ধ্বনিকে সব সময় একই ভাবেই উচ্চারণ করা হয়। অপরদিকে ইংরেজি C বর্ণ কখনও স্ আবার কখনও ক্-এর মতো উচ্চারিত হয়।
আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা
পৃথিবীর সমস্ত ভাষার সমস্ত ধ্বনিকে একটিমাত্র বর্ণমালার সাহায্যে লেখার জন্য আন্তর্জাতিক ধ্বনিতাত্ত্বিক সংস্থা একটি বর্ণমালা উদ্ভাবন করে। এই বর্ণমালা সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বনিতাত্ত্বিক। অর্থাৎ এর প্রতিটি বর্ণের উচ্চারণ সুনির্দিষ্ট। একে বলা হয় আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা বা International Phonetic Alphabet (IPA). এই বর্ণমালার উদ্ভাবন হয় ঊনিশ শতকের আটের দশকে। তারপর থেকে বহুবার এই বর্ণমালার সংস্কার ও পরিবর্ধন হয়েছে। ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে চাইলে এই বর্ণমালা জানা একান্ত প্রয়োজন।
ধ্বনি ও বর্ণের মধ্যে পার্থক্য
ধ্বনি ও বর্ণের 10 টি পার্থক্য
ধ্বনি ও বর্ণ বলতে অনেকে একই জিনিস বোঝেন। আসলে কিন্তু তা নয়। ধ্বনি ও বর্ণ পরস্পরের পরিপূরক, কিন্তু অভিন্ন নয়। নিচে আমরা ধ্বনি বর্ণের পার্থক্যগুলি দেখে নেবো।
১: ধ্বনি শুধুমাত্র আমরা শুনতে পারি কিন্তু দেখতে পাই না । অন্যদিকে বর্ণ আমরা দেখতে পাই না।
২: ধ্বনি ক্ষণস্থায়ী। বর্ণ দীর্ঘস্থায়ী।
৩: ধ্বনি কানে শোনা যায়। বর্ণকে চোখে দেখা যায়।
৪: ধ্বনির সৃষ্টি হয় বাগযন্ত্র দ্বারা কিন্তু বর্ণ শুধুমাত্র একটা চিত্র।
৫: ধ্বনি হল ভাষার প্রাথমিক উপাদান। বর্ণ হল ভাষার একটি বিকল্প উপাদান।
৬: ধ্বনি এক ধরনের আওয়াজ-সংকেত। বর্ণ এক ধরনের চিত্র-সংকেত।
৭: ধ্বনি সৃষ্টি হয় বাগ্যন্ত্রে। বর্ণকে অঙ্কন করা হয়।
৮: ধ্বনির ভাব-প্রকাশ-ক্ষমতা অনেক বেশি। বর্ণের ভাব-প্রকাশ-ক্ষমতা ধ্বনির চেয়ে কম।
৯: ধ্বনি ক্ষণস্থায়ী যা উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথেই শেষ।অপরদিকে বর্ণ দীর্ঘস্থায়ী যা লেখার সাথে সাথেই শেষ হয়ে যায় না।
Many People also search this article to use these type of keywords
- বর্ণ ও অক্ষরের মধ্যে পার্থক্য
- ধ্বনি ও বর্ণ কাকে বলে
- স্বরধ্বনি ও স্বরবর্ণের পার্থক্য
- ধ্বনি বর্ণ ও অক্ষরের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক
- ধ্বনি ও বর্ণের উদাহরণ
- শব্দ ও পদের মধ্যে পার্থক্য
- ধ্বনি ও বর্ণ প্রশ্ন উত্তর
- স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি পার্থক্য
আশাকরি তোমাদের ধ্বনি ও বর্ণ অংশটি থেকে সকল ধরনের সংশয় কমপ্লিট হয়েছে। আমরা আমাদের সর্বাঙ্গীণ প্রচেষ্টা করেছি তোমাদের এই ধ্বনি ও বর্ণ বিষয়টি থেকে সব ধরণের তথ্য দেওয়ার জন্য, এখন কাজ হল তোমাদের বাড়িতে পড়ার । পড়তে থাকো , প্র্যাকটিস করতে থাকো, প্র্যাকটিস মানুষকে উত্তম করে তোলে। যত পড়বে তত শিখবে, ততই জ্ঞানী হবে।
তোমাদের বাংলা ব্যাকারণ এর বিভিন্ন অধ্যায়ের প্রাকটিসের জন্য আমাদের কুইজে অংশগ্রহণ করতে পারো, সম্পূর্ণ ফ্রিতে, নিচে লিঙ্ক দেওয়া আছে কুইজে অংশ নিতে পারো।
বাংলা ব্যাকারণ এর অন্যান্য অধ্যায় গুলি সম্পর্কে আরও পড়তে চাইলে নিচে অধ্যায় অনুযায়ী লিঙ্ক দেওয়া আছে, লিঙ্কে ক্লিক করে বিভিন্ন ক্লাস এর অন্য অধ্যায় গুলি পড়ে নাও। আমাদের পরিসেবা তোমাদের ভালো লাগলে আমাদের এই ওয়েবসাইটটি ফলো করতে পারো।